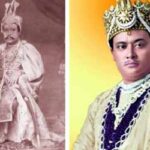মহারাজা রাধা কিশোর, বীরেন্দ্র কিশোর, বীর বিক্রম ও বীরচন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত।
ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। রাজা এবং রাজ পরিবারের লোকেরা নিজেরাও সাহিত্য চর্চা করেছেন। রাজসভার কাজে ব্যবহার করেছেন বাংলা। এমনকি আধুনিক যুগেও রাজকার্যে যাতে বাংলার ব্যবহার ব্যাহত না হয় সেজন্য রাজা সতর্ক নজর রেখেছেন। পঞ্চদশ শতকে রত্ন মাণিক্যের সময় থেকেই ত্রিপুরার রাজকার্যে পার্সি ও বাংলার প্রভাব পড়তে থাকে। পঞ্চদশ শতকে মহারাজা ধর্ম মাণিক্য ‘রাজমালা’ রচনা করান। এই রাজমালাকে বাংলা কাব্যের প্রাচীন নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
নিজ বংশের পূর্ব পুরুষদের কীর্তি কাহিনি লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহারাজ ধর্ম মাণিক্য (১৪৩১-৬২ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর আদেশে চন্তাই দুর্লভেন্দ্রের সহায়তায় পন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রচনা করেছিলেন ‘রাজমালা’। কেউ কেউ বলেছেন, বাংলা নয়, তা ছিল সংস্কৃতে। বিতর্ক আছে, আবার গবেষণাও অব্যাহত। সুদূর অতীত কালে রাজার ইচ্ছা ও নির্দেশে রচিত ‘রাজমালা’ সঠিক ইতিহাস নয়। তার বিষয়বস্তুতে মূলত প্রাধান্য পেয়েছে রাজবংশের কীর্তিগাঁথা। অবশ্য কাব্যে বর্ণিত পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ইতিহাসের সঙ্গে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ।
আরও পড়ুন:

এই দেশ এই মাটি, ত্রিপুরা: আজ কাল পরশুর গল্প, পর্ব-২১: বিরোধী দলের সরকারে যোগদান

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-৭৩: দুই মহর্ষির দ্বন্দ্বে কি ‘ইতি ও নেতি’র বিরোধেরই প্রতিফলন?
‘রাজমালা’র রচনাকাল, রচয়িতা এবং কাব্যের ভাষা নিয়ে আজও গবেষণা অব্যাহত থাকলেও প্রচলিত ধারণা হল, পঞ্চদশ শতকে মহারাজা ধর্ম মানিক্যের আমলে বাংলায় প্রথম ‘রাজমালা’ রচিত হয়। ‘রাজমালা’র সার সংকলক রেভারেন্ড লঙ বলেছেন,পঞ্চদশ শতকের লেখা এই পুঁথি বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কেউ কেউ আবার বলেছেন ‘রাজমালা’র মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত ঘটেছে।
মহারাজা বীরবিক্রমের শাসনকালে (১৯২৩-৪৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত ‘শ্রীরাজমালা’র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ বলেছেন—”রাজমালা’র দ্বারাই বঙ্গভাষার ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইয়াছে।তৎপর বৈষ্ণব মহাজনদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে ইতিহাস ও চরিতাখ্যান রচনা কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা গিয়াছে,কিন্তু রাজত্বের ইতিহাস কিংবা রাজনীতিক আলোচনা রাজমালা ব্যতীত তৎকালীন অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।” তিনি আরও বলেছেন, সমগ্র রাজমালা একসঙ্গে রচিত হয়নি। ধর্ম মানিক্যের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তী রাজাদের আদেশে রাজমালা ছয় পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে রচিত হয়েছে।
মহারাজা বীরবিক্রমের শাসনকালে (১৯২৩-৪৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত ‘শ্রীরাজমালা’র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ বলেছেন—”রাজমালা’র দ্বারাই বঙ্গভাষার ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইয়াছে।তৎপর বৈষ্ণব মহাজনদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে ইতিহাস ও চরিতাখ্যান রচনা কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা গিয়াছে,কিন্তু রাজত্বের ইতিহাস কিংবা রাজনীতিক আলোচনা রাজমালা ব্যতীত তৎকালীন অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।” তিনি আরও বলেছেন, সমগ্র রাজমালা একসঙ্গে রচিত হয়নি। ধর্ম মানিক্যের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তী রাজাদের আদেশে রাজমালা ছয় পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে রচিত হয়েছে।
আরও পড়ুন:
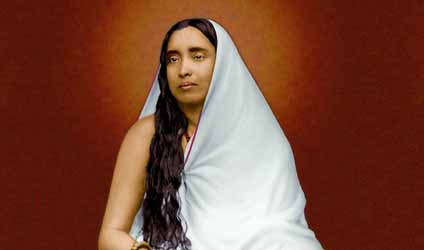
আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৫৬: নান্দনিক শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন শ্রীমা

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৫০: পুত্রস্নেহে অন্ধ হলে পিতাকেও ধৃতরাষ্ট্রের মতো দুর্দশা ভোগ করতে হয়
‘শ্রীরাজমালা’ সম্পাদক বলেছেন, রাজমালা বাংলা ভাষায় রচিত হলেও তাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম মাণিক্যের বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে ‘শ্রীরাজমালা’র সম্পাদক আরও, ‘রাজমালা’র প্রথম লহর ধর্ম মাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হয়। এছাড়াও রাজা সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়েছিলেন এমন কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর এই গ্রন্হের অস্তিত্ব নেই। সব মিলিয়ে মাণিক্য রাজাদের বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে অক্ষয় হয়ে আছে ধর্ম মাণিক্যের নাম।
আরও পড়ুন:

গীতা: সম্ভবামি যুগে যুগে, পর্ব-৩: কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
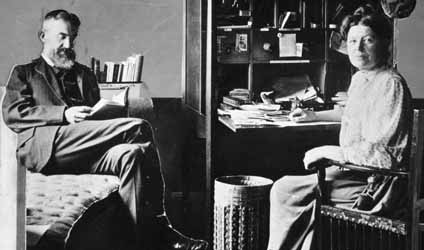
বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-৫: বার্নার্ড শ ও শার্লটি—যদি প্রেম দিলে না প্রাণে/১
পঞ্চদশ শতকের রাজা রত্ন মাণিক্যের সময় থেকেই বঙ্গের মুসলমান শাসকদের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজকার্যের ভাষাতেও তখন থেকেই পার্সি ও বাংলার প্রভাব পড়তে থাকে। লক্ষ্মণাবতীতে বসবাস কালে কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে রত্ন ফা’র ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সিংহাসনে বসার পর তিনি তাদেরকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন এবং নিষ্কর ভূমিদান সহ নানা ভাবে সাহায্য করেন। কালক্রমে তারা রাজকার্যেও নিযুক্ত হন।
আরও পড়ুন:

পর্দার আড়ালে, পর্ব-৫৮: কালীর হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মহানায়ক বলেছিলেন, ‘কাউকে বলো না’
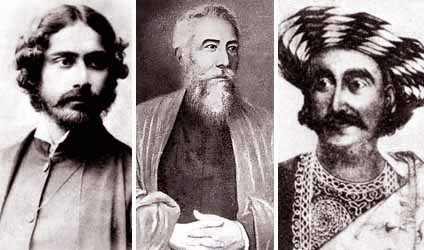
গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৯৬: স্রোতস্বিনী পদ্মায় লাফিয়ে কবির কটকি চটি-উদ্ধার
‘রাজমালা’ অনুসারে আরও জানা যায় যে,গৌড়াধিপতির অনুমতিক্রমে বঙ্গদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি প্রজাকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসে বসতি পত্তন করিয়েছিলেন রত্ন মাণিক্য। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে প্রথম রত্ন মাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রাই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর মুদ্রায় বাংলা লিপির ব্যবহার রাজার বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।—চলবে।
* ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে পান্নালাল রায় এক সুপরিচিত নাম। ১৯৫৪ সালে ত্রিপুরার কৈলাসহরে জন্ম। প্রায় চার দশক যাবত তিনি নিয়মিত লেখালেখি করছেন। আগরতলা ও কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ইতিমধ্যে তার ৪০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা-সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস ভিত্তিক তার বিভিন্ন গ্রন্থ মননশীল পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও সে-সব উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। রাজন্য ত্রিপুরার ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সম্পর্ক, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ব্যতিক্রমী রচনা আবার কখনও স্থানীয় রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ সমূহের বিষয়বস্তু। সহজ সরল গদ্যে জটিল বিষয়ের উপস্থাপনই তাঁর কলমের বৈশিষ্ট্য।