
(বাঁদিকে) হরিয়ালের বাসায় তা। (ডান দিকে) হরিয়াল দম্পতি। ছবি: সংগৃহীত।
দু’সপ্তাহ আগে এক রবিবারের কথা। সকাল ন’টা নাগাদ কাকদ্বীপ বামুনের মোড়ে যাচ্ছিলাম বাজার করতে। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে একটু দূরের ওই বাজারে যাই কারণ গ্রামের থেকে মানুষজন নানা রকম শাকসব্জি বিক্রি করতে সরাসরি আসে। দামে একটু সস্তা হওয়ার থেকেও বড় কথা গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো অনেক শাকসব্জি ওই বাজার থেকে কেনার সুযোগ থাকে। যথারীতি সাইকেলে চেপে যাচ্ছিলাম। স্টেশনের একটু আগে হঠাৎ মনে হল কোনও একটা বড় মাপের পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কাক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু স্পষ্টত আমি একটু অন্যরকম যেন ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পেলাম। আর তাই সাথে সাথে চোখ চলে গেল উপরের দিকে। দেখলাম একটা পাখি উড়ে গিয়ে সামনেই একটা নারকেল গাছের পাতার উপর বসল। সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়লাম। আমার থেকে পাখির দূরত্ব একটু বেশি হওয়ায় ভালোভাবে বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত হলাম যে কাক নয়। তবে প্রায় কাকের আকারের পাখি। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পৌঁছে গেলাম নারকেল গাছের নিচে। এ বার ভালোভাবে বুঝতে পারলাম যে পাখিটার রং সবুজ। ওর বুকের কাছে হালকা কমলা রং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে পাখিটা ডেকে উঠল ‘কক্ কক্ কঅঅ ক্রিউয়া কুইক’! একবার… দুবার…তিনবার। এ ডাক তো আমার অনেক দিনের চেনা।
রংছোটবেলায় প্রায়শই এ ডাক শুনেছি গ্রামে থাকতে। ভাবতে লাগলাম কী নাম যেন এই পাখিটার? কখনও এক জোড়া, কখনও তিন-চারটে, কখনও একটা পাখি ধীর লয়ে উড়ে এসে আমাদের পেয়ারা গাছে বা অর্জুন গাছে বা সবেদা গাছে এসে বসত। ওদের উড়ে আসার সময় বা উড়ে যাওয়ার সময় ডানার ঝাপট দেওয়ার ঢপ ঢপ শব্দ হত। হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমরা বলতাম ‘ঢপঢপে’ পাখি। ডানা সঞ্চালনের সময় ওই বিশেষ শব্দের জন্য যে স্থানীয়ভাবে আমরা সুন্দরবনের মানুষজন এই নাম বলতাম তা বলা বাহুল্য। তবে এই পাখিটার শুদ্ধ নাম যে ‘হরিয়াল’ এবং ইংরেজিতে যে বলে ‘Orange breasted green pigeon’ তা বই পত্র পড়ে পরে জেনেছিলাম। কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা ‘বেদিয়া’ কবিতাটার কয়েকটা লাইন মনে পড়ল—
“লুটায়ে রয়েছে কোথা সীমান্তে শরৎ ঊষার শ্বাস!
ঘুঘু-হরিয়াল-ডাহুক-শালিক-গাঙচিল-বুনোহাঁস।
নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিরে ফিরে,
বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে!”
রংছোটবেলায় প্রায়শই এ ডাক শুনেছি গ্রামে থাকতে। ভাবতে লাগলাম কী নাম যেন এই পাখিটার? কখনও এক জোড়া, কখনও তিন-চারটে, কখনও একটা পাখি ধীর লয়ে উড়ে এসে আমাদের পেয়ারা গাছে বা অর্জুন গাছে বা সবেদা গাছে এসে বসত। ওদের উড়ে আসার সময় বা উড়ে যাওয়ার সময় ডানার ঝাপট দেওয়ার ঢপ ঢপ শব্দ হত। হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমরা বলতাম ‘ঢপঢপে’ পাখি। ডানা সঞ্চালনের সময় ওই বিশেষ শব্দের জন্য যে স্থানীয়ভাবে আমরা সুন্দরবনের মানুষজন এই নাম বলতাম তা বলা বাহুল্য। তবে এই পাখিটার শুদ্ধ নাম যে ‘হরিয়াল’ এবং ইংরেজিতে যে বলে ‘Orange breasted green pigeon’ তা বই পত্র পড়ে পরে জেনেছিলাম। কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা ‘বেদিয়া’ কবিতাটার কয়েকটা লাইন মনে পড়ল—
ঘুঘু-হরিয়াল-ডাহুক-শালিক-গাঙচিল-বুনোহাঁস।
নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিরে ফিরে,
বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে!”
সত্যি আমার শৈশবের সেই বহু পুরাতন সঙ্গী ঢপঢপে পাখি বা হরিয়াল যে এত দশক পর আমার কাছে ফিরে আসবে আমি একবারের জন্যও ভাবিনি। কথাগুলো যখনই ভাবছি তখনই ডানায় ঢপ ঢপ শব্দ তুলে সে উড়ে গেল দক্ষিণ আকাশে। আমার ঘোর কাটল। ফের সাইকেলে বসে প্যাডেলে চাপ দিলাম।
ঢপঢপে পাখি বা হরিয়ালদের খুব প্রিয় খাবার হল পাকা পেয়ারা, পাকা সবেদা, পাকা ডুমুর, বট ইত্যাদি ফল। যেহেতু আমাদের গ্রামের বাড়িতে বড় বড় পেয়ারা গাছ, সবেদা গাছ ও ডুমুর গাছ ছিল তাই হরিয়ালদের প্রায়ই দেখা যেত আমাদের ওইসব গাছে বসে পাকা ফল খাচ্ছে।
ঢপঢপে পাখি বা হরিয়ালদের খুব প্রিয় খাবার হল পাকা পেয়ারা, পাকা সবেদা, পাকা ডুমুর, বট ইত্যাদি ফল। যেহেতু আমাদের গ্রামের বাড়িতে বড় বড় পেয়ারা গাছ, সবেদা গাছ ও ডুমুর গাছ ছিল তাই হরিয়ালদের প্রায়ই দেখা যেত আমাদের ওইসব গাছে বসে পাকা ফল খাচ্ছে।
আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৭: পাতি সরালি

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-৪৮: রান্নার জ্বালানি নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ?
পুকুরঘাটের পাশেই ছিল কয়েকটা বড় পেয়ারা গাছ ও সবেদা গাছ। যখন হরিয়ালদের ঝাঁক এসে সেই গাছে বসত তার ডানার শব্দ ঘরের মধ্যে থেকেই শোনা যেত। তখন মাকে বলতে শুনেছি, “ওই দেখ ঢপঢপে পাখিরা এসেছে।” অমনি ছুটতাম দেখার জন্য। খুঁজে পেতে কিন্তু বেশ সমস্যা হত কারণ গাছের সবুজ পাতার সঙ্গে ওদের গায়ের রং দারুণভাবে মিশে যেত। তবে যখন ফল খাওয়ার কারণে গাছের শাখাগুলো দুলত তখন দেখতে পেতাম। ওরা কিন্তু এক ডাল থেকে আর এক ডালে উড়ে গিয়ে ফল খেত না, দিব্যি হেঁটে হেঁটে এক ডাল থেকে আর এক ডালে যেত। অনেক সময় ঝুলে ঝুলে ফল খেত। তখন আমাদের ক্যামেরা ছিল না ফলে কোনও হরিয়ালের ছবি তুলে রাখতে পারিনি। কিন্তু ওদের অসাধারণ রূপের ছবি মনের মধ্যে এখনও গাঁথা আছে। কোনটা পুরুষ আর কোনটা স্ত্রী হরিয়াল তখন ছোট ছিলাম বলে চিনতে পারতাম না। কিন্তু দু’রকম হরিয়াল যে হয় তা জানতাম। পরে জেনেছি যে হরিয়ালদের বুকের কাছে কমলা রঙের অসাধারণ একটা শেড থাকে তারা হল পুরুষ।

(বাঁদিকে) উড়ন্ত হরিয়াল। (ডান দিকে) সতর্ক হরিয়াল। ছবি: সংগৃহীত।
হরিয়ালের বিজ্ঞানসম্মত নাম ‘Treron bicinctus’। কিছু ইউরোপীয় ভাষায় একে নাকি ‘বেঙ্গলি লম্বগলম্ব’ (Bengali Lombgalamb) বলা হয় যার অর্থ বাংলার পাতা-পায়রা। হরিয়ালরা আসলে এক ধরনের পায়রা। আমরা বাড়িতে যেসব পায়রা পুষি আকারে প্রায় তাদের মতোই। গড়ন একই রকম। পার্থক্য কেবল রঙে। রীতিমত গাট্টাগোট্টা চেহারা। লম্বায় প্রায় ১১-১২ ইঞ্চি। স্ত্রী ও পুরুষদের পেট, ডানা, গলা সবই সবুজ। পুরুষের ঘাড়ের রং ধূসরাভ সবুজ। মাথার সামনের দিকের রং সবুজ হলেও তাতে হলদে ভাব একটু বেশি। বুকের কাছে রয়েছে হালকা গোলাপি রঙের একটা ব্যান্ড, আর তার নিচেই রয়েছে কমলা রঙের বেশ চওড়া ছোপ।
রংএদের ডানার রং সবুজ হলেও তা পেট বা মাথার থেকে একটু গাঢ়। ডানার প্রান্ত ও কিনারায় কালো রঙের পালক থাকলেও ফিতের মতো এক সারি হলুদ রঙের পালক রয়েছে। যখন বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে তখন ডানার শেষ প্রান্তে কালো পালকগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। কোমরের কাছে রং ধূসর সবুজ আর লেজের রং ধূসর। অবশ্য লেজের নিচের দিকের রং কালচে লাল। দু’ পায়ের ঊরুতে যে পালক থাকে তার রং হলদেটে সবুজ। স্ত্রী পাখি চেনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল ওদের বুকে গোলাপি ব্যান্ড ও কমলা রঙের ছোপ নেই। পুরোটাই উজ্জ্বল সবুজ। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের চঞ্চু ফ্যাকাসে সবুজ আর পায়ের রঙ লালচে গোলাপি। চঞ্চুর সামনের দিকটা নিচের দিকে একটু বাঁকা। উপরের চঞ্চুর পেছনদিকে লম্বাটে দুটো নাসারন্ধ্র স্পষ্ট দেখা যায়। চোখে কালো রঙের কনীনিকা ঘিরে চারদিকে রয়েছে প্রথমে নীল ও তার বাইরে গোলাপি রঙের বৃত্ত।
রংএদের ডানার রং সবুজ হলেও তা পেট বা মাথার থেকে একটু গাঢ়। ডানার প্রান্ত ও কিনারায় কালো রঙের পালক থাকলেও ফিতের মতো এক সারি হলুদ রঙের পালক রয়েছে। যখন বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে তখন ডানার শেষ প্রান্তে কালো পালকগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। কোমরের কাছে রং ধূসর সবুজ আর লেজের রং ধূসর। অবশ্য লেজের নিচের দিকের রং কালচে লাল। দু’ পায়ের ঊরুতে যে পালক থাকে তার রং হলদেটে সবুজ। স্ত্রী পাখি চেনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল ওদের বুকে গোলাপি ব্যান্ড ও কমলা রঙের ছোপ নেই। পুরোটাই উজ্জ্বল সবুজ। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের চঞ্চু ফ্যাকাসে সবুজ আর পায়ের রঙ লালচে গোলাপি। চঞ্চুর সামনের দিকটা নিচের দিকে একটু বাঁকা। উপরের চঞ্চুর পেছনদিকে লম্বাটে দুটো নাসারন্ধ্র স্পষ্ট দেখা যায়। চোখে কালো রঙের কনীনিকা ঘিরে চারদিকে রয়েছে প্রথমে নীল ও তার বাইরে গোলাপি রঙের বৃত্ত।
আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১২: অপারেশন অপহরণ

বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-১৫: এ কেমন রঙ্গ জাদু, এ কেমন রঙ্গ…/৩
হরিয়াল দের খাবার সংগ্রহের সময় সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যের আগে। যখন এরা খাওয়ার সংগ্রহ করে সেই সময় যদি কোনও বিপদের আভাস পায় তাহলে খাওয়া বন্ধ করে সবাই স্থির হয়ে যায়। আর সবুজ রং হওয়ায় এমনিতেই পাতার মধ্যে মিশে থাকে ফলে ওই সময় কোনও শিকারির পক্ষে হরিয়াল খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর। আর সমস্ত হরিয়াল যখন ঝাঁক বেঁধে একসঙ্গে কোনও গাছ থেকে উড়ে যায় তখন সে দৃশ্য যেমন হয় অতি মনোরম তেমনই ওদের ডানা ঝাপটানোর অদ্ভুত ধাতব শব্দের মতো সমবেত ধ্বনিতে আশপাশ মুখরিত হয়।
হরিয়ালদের প্রজনন ঋতু হল সাধারণতঃ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। এই সময় স্ত্রী ও পুরুষ হরিয়ালের প্রেমপর্ব পুরো জমে ওঠে। পুরুষ হরিয়াল স্ত্রী হরিয়ালের সামনে তার পালক ফুলিয়ে মাথাটাকে ওপর-নিচে ক্রমাগত উঠিয়ে নামিয়ে ও একরকম শব্দ করে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। এই শব্দ কখনও কখনও খুব মিষ্টি সুরে হয় আবার কখনও কখনও খ্যাসখেসে সুরেও হয়।
হরিয়ালদের প্রজনন ঋতু হল সাধারণতঃ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। এই সময় স্ত্রী ও পুরুষ হরিয়ালের প্রেমপর্ব পুরো জমে ওঠে। পুরুষ হরিয়াল স্ত্রী হরিয়ালের সামনে তার পালক ফুলিয়ে মাথাটাকে ওপর-নিচে ক্রমাগত উঠিয়ে নামিয়ে ও একরকম শব্দ করে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। এই শব্দ কখনও কখনও খুব মিষ্টি সুরে হয় আবার কখনও কখনও খ্যাসখেসে সুরেও হয়।
আরও পড়ুন:
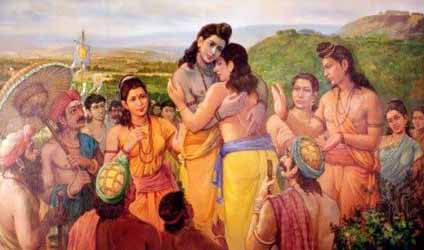
মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১১২: প্রশাসক রামচন্দ্রের সাফল্য কী আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে সফল প্রশাসকদের আলোর দিশা হতে পারে?

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫৫: সর্বত্র বরফ, কোত্থাও কেউ নেই, একেবারে গা ছমছম করা পরিবেশ
যাইহোক কখনও হেঁড়ে গলায়, কখনও সুরেলা গলায় গান গেয়ে পুরুষ হরিয়াল স্ত্রীহরিয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময় আবার কখনও কখনও স্ত্রী হরিয়ালকে ছোট ছোট পদক্ষেপে প্রায় নাচের ভঙ্গিতে ও মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সরে গিয়ে ভালোবাসা স্বীকার করতে দেখা যায়। কখনও কখনও একটা স্ত্রী হরিয়ালের জন্য দুটি পুরুষ হরিয়ালকে প্রতিযোগিতা করতে দেখা যায়। তখন তারা পরস্পর ডানা ঝাপটে এবং চঞ্চু দিয়ে পরস্পরকে খুঁচিয়ে লড়াই করে। স্ত্রী ও পুরুষ জুটি বাঁধার কাজ শেষ হলে উভয়ে মিলে যেমন-তেমন করে একটা বাসা বানায়। বাসার মূল উপাদান শুকনো কাঠি। বাসা এতটাই অগোছালো ও চ্যাটালো যে দেখে মনে হয় প্রাচীনকালের বাসা। বাসা বানানোর জন্য পুরুষ চঞ্চুতে করে কাঠি নিয়ে আসে আর স্ত্রী হরিয়াল সাধারণত বাসা তৈরি করে।

সুন্দরবনে হরিয়াল। ছবি: সংগৃহীত।
সাধারণত মাটি থেকে ২৫-৩০ ফুট উপরে কোনও বৃক্ষের উপরে বাসা বাঁধে। দু-তিন দিনের মধ্যেই বাসা বানানোর কাজ শেষ হয়। তবে ওরা দিনভর বাসা বানায় না। সকাল আর বিকেলে কয়েক ঘন্টা করে বাসা বানায়, বাকি সময়টা বিশ্রাম নেয় বা খাবার খেতে ব্যস্ত থাকে। বাসা বানানোর শেষ হলে সাধারণত একদিনের ব্যবধানে স্ত্রী হরিয়াল দুটি ডিম পাড়ে। ছোট ছোট ও ঝকঝকে সাদা ডিমগুলি প্রায় ১.১ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুরুষ হরিয়াল কিন্তু খুব দায়িত্ববান। স্ত্রী হরিয়াল যখন খাবার খেতে যায় সেই সময় পুরুষ হরিয়াল ডিমে তা দেয়। এমনকি যখন স্ত্রী ডিমে তা দেয় তখন সে খাবার এনে স্ত্রীকে খাইয়ে দেয় নতুবা স্ত্রীর সামনে নানা সুরে গান গেয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করে। ১২ থেকে ১৪ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে আসে। এদের আয়ু যথেষ্ট বেশি, প্রায় ২৬ বছর বাঁচে।
আরও পড়ুন:

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৬: মা সারদার প্রথম মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন দুর্গাপুরীদেবী

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৭৭: পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাঁর জীবনের আকাশে কখনও শত্রুতার মেঘ জমেনি
আমরা অনেক সময় একটা বাংলা প্রবাদ বলি যে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। হরিয়ালদের রূপের অহংকার রয়েছে কিনা আমার জানা নেই তবে এরা কিন্তু সত্যি সত্যি কখনও মাটিতে নামে না। এদের যা কিছু কর্মকাণ্ড সবই হয় গাছের শাখায়, নয়তো আকাশে। জল পান করার জন্য এদের মাটিতে নামার প্রয়োজন হয় না। তার কারণ পাতা বা ফলের গায়ে যে শিশির বিন্দু বা বৃষ্টির কণা জমে থাকে এবং বিভিন্ন ফলের শাঁসে যেটুকু জল থাকে তা হরিয়ালদের জন্য যথেষ্ট।
রংভারতের প্রায় সমস্ত উপকূল এলাকা জুড়ে, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব ফিলিপিনস ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে হরিয়ালদের দেখা যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে অরণ্য এলাকায় হরিয়ালদের উপস্থিতি আজও তুলনামূলকভাবে বেশি কিন্তু বসতি এলাকায় এদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। জঙ্গল এলাকায় হেতাল ও কেওড়াগাছের ফল হরিয়ালদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। আর বসতি এলাকায় সবচেয়ে প্রিয় খাবার হল ডুমুর, বট ও অশ্বত্থ গাছের ফল। কিন্তু সুন্দরবনের বসতি এলাকায় এই গাছগুলির পরিমাণ ভয়ঙ্কর ভাবে কমে গিয়েছে।
রংভারতের প্রায় সমস্ত উপকূল এলাকা জুড়ে, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব ফিলিপিনস ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে হরিয়ালদের দেখা যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে অরণ্য এলাকায় হরিয়ালদের উপস্থিতি আজও তুলনামূলকভাবে বেশি কিন্তু বসতি এলাকায় এদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। জঙ্গল এলাকায় হেতাল ও কেওড়াগাছের ফল হরিয়ালদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। আর বসতি এলাকায় সবচেয়ে প্রিয় খাবার হল ডুমুর, বট ও অশ্বত্থ গাছের ফল। কিন্তু সুন্দরবনের বসতি এলাকায় এই গাছগুলির পরিমাণ ভয়ঙ্কর ভাবে কমে গিয়েছে।

(বাঁদিকে) বটগাছে খাবার সংগ্রহে বসে হরিয়া। (ডান দিকে) স্ত্রী হরিয়ালের খাবার সংগ্রহ। ছবি: সংগৃহীত।
সম্ভবত এই কারণেই সুন্দরবন অঞ্চলের বসতি এলাকা থেকে হরিয়ালরা প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া এদের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু হওয়ায় পাখি শিকারিরা গুলি করে নিয়মিত হরিয়ালদের হত্যা করেছে। ছোটবেলায় বন্দুক হাতে পাখি শিকারীদের প্রায়শই এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখতাম। আমাদের বাড়ির বাঁশবাগানে, পুকুরপাড়ে ঘোরাঘুরি করত। অবশ্য বাবা দেখতে পেলেই বকুনি দিয়ে ভাগিয়ে দিত। সুন্দরবনের বসতি এলাকায় হরিয়ালদের সংখ্যা হ্রাসের এটাও অন্যতম কারণ।
প্রায় চার দশক পর কাকদ্বীপ এলাকায় হরিয়াল দেখলাম। অনেক এলাকায় খোঁজ নিয়েও দেখলাম যে এদের আর আগের মতো যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায় না। আজকের প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে প্রকৃতির এই অপরূপ সুন্দরী প্রায় অধরাই থেকে গেল। সুন্দরবনের বসতি এলাকায় আমার পুরাতন শৈশব সঙ্গী ‘ঢপঢপে’ পাখি হরিয়ালকে আবার কবে দেখতে পাব বা আদৌ পাব কিনা জানি না। প্রশ্নচিহ্নটা রয়েই গেল। —চলবে।
প্রায় চার দশক পর কাকদ্বীপ এলাকায় হরিয়াল দেখলাম। অনেক এলাকায় খোঁজ নিয়েও দেখলাম যে এদের আর আগের মতো যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায় না। আজকের প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে প্রকৃতির এই অপরূপ সুন্দরী প্রায় অধরাই থেকে গেল। সুন্দরবনের বসতি এলাকায় আমার পুরাতন শৈশব সঙ্গী ‘ঢপঢপে’ পাখি হরিয়ালকে আবার কবে দেখতে পাব বা আদৌ পাব কিনা জানি না। প্রশ্নচিহ্নটা রয়েই গেল। —চলবে।
* * সৌম্যকান্তি জানা। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। নিবাস কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পেশা শিক্ষকতা। নেশা লেখালেখি ও সংস্কৃতি চর্চা। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ‘দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২০১৬ সালে ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২০১৭ সালে ‘অমলেশচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি সম্মান’ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।




















