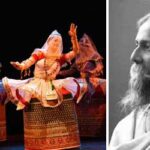(বাঁদিকে) বাসা নির্মাণরত স্ত্রী মৌটুসি। ছবি: সংগৃহীত। বটলব্রাশ গাছে পুরুষ মৌটুসি। ছবি: লেখক।
দুর্গা টুনটুনিকে নিয়ে লিখতে গিয়ে ওরই এক জ্ঞাতি ভাইয়ের কথা আমার স্মৃতিকথায় উঠে এসেছিল। মৌটুসি। অনেকে বলে মৌচুষি। মৌবনে মৌ জমলে মৌটুসিরা কি আর না এসে থাকতে পারে? যে বাগানে কিংবা যে গাছে ফোটা ফুলে মধুর সমৃদ্ধ ভান্ডার সেখানে মৌটুসিদের অবাধ আনাগোনা। দুর্গা টুনটুনিদেরও আনাগোনা সেখানে। রঙের বিন্যাসে ও বাহারে দুর্গা টুনটুনি আর মৌটুসিদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের আকার আর স্বভাবে কোনও পার্থক্য আছে বলে আমার অন্তত কোনওদিন মনে হয়নি। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়ির বাগানে নানারকম ফুল ফুটত। পুকুরপাড়ে সাদা ও হলুদ কলকে, রক্তজবা আর পঞ্চমুখী জবার বড় গাছ ছিল। সামনে ছিল টগর আর রঙ্গনের বড় বড় গাছ। আর মাঠের দিকে ছিল মাধবীলতা ফুলের ঝোপ। আম, কুল আর বেল গাছ বেয়ে মাধবীলতা উঠে গিয়েছিল। আর কিছু মাধবীলতা আমাদের টালির চালে বেয়ে উঠেছিল। মাধবীলতার ফুলের গন্ধে সন্ধে থেকে মম করত চতুর্দিক। আর এইসব ফুলের মধু খেতেই হাজির হত দুর্গা টুনটুনি ও মৌটুসির দল। সকাল থেকে দুপুর চুই চুই চুই, চিইইই উইট শব্দে মুখরিত হয়ে থাকত আমাদের বাড়ি। খুব মনে পড়ে সেই সময়টা যখন শীতকালে সজনে গাছে ফুল দেখা দিত। আমাদের পুকুর ঘাটের পাশেই ছিল বিরাট একটা সজনে গাছ। সকাল বেলা পুকুরপাড়ে সাদা হয়ে বিছিয়ে থাকত ঝরে পড়া সজনে ফুল। সেই ফুল কুড়োতে খুব ভালো লাগত। মা সেই সজনে ফুল দিয়ে চচ্চড়ি রান্না করত। যাইহোক, যখন নিচে সজনে ফুল কুড়োতাম তখন কিন্তু সজনে গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে লাফাতে লাফাতে রীতিমতো গানের জলসা বসিয়ে দিত মৌটুসি আর দুর্গা টুনটুনিরা। তবে মৌটুসিদের দখলদারি ছিল বেশি। কারণ ওদেরকেই বেশি দেখতাম।
আমাদের স্কুলের সামনে বারান্দা লাগোয়া যে একটা বিরাট বটলব্রাশ গাছ ছিল সে কথা আগেও বলেছি। প্রায় সারা বছর সেই গাছ থাকত লাল ফুলে ভরা। সেখানে দুর্গা টুনটুনিদের সঙ্গে মৌটুসিদের থাকত সমান আনাগোনা। বটলব্রাশ গাছে বেশ কয়েকবার ছবিও তুলেছি ওদের। আর রয়েছে একটা হলুদ পলাশের গাছ। ফাল্গুন মাসে পাতা ঝরিয়ে সে সেজে ওঠে হলুদরঙা পুষ্পসম্ভারে। তখন মৌটুসি আর দুর্গা টুনটুনিদের যেন মোচ্ছব শুরু হয় পলাশ গাছে। আর একটা কথা মনে পড়ল মৌটুসিদের নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে। আমাদের গ্রামের বাড়ির সামনে ছিল জোয়ার-ভাটা খেলা নোনা জলের খাল। তার পাড়ে ছিল প্রচুর গেঁওয়া গাছ। গেঁওয়া গাছে এক ধরনের পরজীবী জন্মাতে দেখতাম। তার ফুলগুলো ভারি সুন্দর। পরে জেনেছি এই পরজীবীর নাম বড়মন্দা (Dendrophthoe falcata)। এই পরজীবীর ফুলের মধু খেতে মৌটুসি আর দুর্গা টুনটুনিদের প্রায়শই দেখতাম। পরে আমার স্কুলের লাগোয়া ঝিলের পাড়ে থাকা গেঁওয়া গেছে একই দৃশ্য এখনও দেখতে পাই। পরে জেনেছি বড়মন্দা ফুলের পরাগমিলনের প্রধান উদ্যোক্তা এই দুই জ্ঞাতিভাই। আর মাঝে মাঝে এখন বিকেল বেলায় যখন ছাদে গিয়ে বসি তখন কখনও কখনও কোথা থেকে একটা বা একজোড়া মৌটুসি উড়ে এসে চুই চুই চুই করে ডাকতে ডাকতে ছাদে জামা কাপড় মেলার জন্য টাঙানো দড়িতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বসতে দেখি। বড়ো চঞ্চল পাখি। ক্যামেরা তাক করা তো দূরের ব্যাপার, ভালো করে দেখার আগেই ফুরুৎ।
আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৩: সাত-সহেলি

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯o: মা সারদার কথায় ‘ঈশ্বর হলেন বালকস্বভাব’
মৌটুসি পাখিরা মধু খেতে ভালোবাসে বলে হিন্দিতে এদের বলে সক্করখোরা। তবে ইংরেজিতে এদের নাম পার্পল রামপ্ড সান বার্ড (Purple Rumped Sun Bird)। বিজ্ঞানসম্মত নাম ‘Nectarinia zeylonica’। লম্বায় এরা হয় দুর্গা টুনটুনিদের মতোই প্রায় চার ইঞ্চি। আর দুর্গা টুনটুনির মতো মৌটুসি পুরুষদের রূপলাবণ্য অতুলনীয়। মাথার চাঁদির রং ঝকঝকে বটলগ্রীন। সূর্যের আলো পড়ে যেন প্রতিফলিত হচ্ছে মনে হয়। চাঁদির পেছন থেকে ঘাড় হয়ে পিঠের অর্ধেক পর্যন্ত রঙ মেরুন। থুতনি আর গালের রঙও মেরুন তবে অপেক্ষাকৃত গাঢ়। চারিদিকে মেরুন রঙের মাঝে গলার কাছে অদ্ভুত সুন্দর লালচে বেগুনি বা গোলাপি রঙের ছোপ। ডানার মাঝামাঝি থেকে পেছনদিকের রং কালচে বাদামি। ডানার সামনে দু’পাশে ছোট্ট জায়গায় মাথার চাঁদির মতো বটলগ্রিন রঙের একটা ছোপ ওর সৌন্দর্যকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পিঠের পেছনে কোমরের কাছে বেগুনি রঙের ছোপ থাকে। অবশ্য বিশ্রামরত অবস্থায় এই ছোপ দেখা যায় না, কেবল ওড়ার সময় দৃষ্টিগোচর হয়। বুকের কাছ থেকে পেটের দিকের রং কাঁচা হলুদের মতো। পেছনদিকে এই রঙ ক্রমশঃ ফিকে হতে হতে পায়ুর কাছাকাছি আর ডানার নিচে হয়ে গেছে সাদা। দু’পায়ের ঊরুর পালকের রঙও সাদা। নাতিদীর্ঘ লেজের রং কালো। পুরুষ দুর্গা টুনটুনির সাথে পুরুষ মৌটুসীর অন্যতম পার্থক্য হল যখন প্রজনন ঋতু নয় তখন পুরুষ দুর্গা টুনটুনির রঙের পরিবর্তন হয় কিন্তু পুরুষ মৌটুসির ক্ষেত্রে সারা বছর থাকে একই রং।
আরও পড়ুন:

উপন্যাস: আকাশ এখনও মেঘলা, পর্ব-৯: আকাশ এখনও মেঘলা

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫১: রোজই দেখি আলাস্কা পর্বতশৃঙ্গের বাঁ দিকের চূড়া থেকে সূর্য উঠতে
স্ত্রী দুর্গা টুনটুনিদের মতো স্ত্রী মৌটুসির রূপলাবণ্যও পুরুষদের থেকে কিছুটা কম। এদের মাথা, ঘাড় ও পিঠের অর্ধেক অংশের রং কালচে ধূসর। দুই ডানার অর্ধেক থেকে পেছন দিকের রং তামাটে ধূসর। চিবুক, দুই গাল আর গলার রং ফ্যাকাসে ধূসর। কিন্তু বুকের কাছ থেকে পেটের দিকে রং পুরুষ পাখির মতো অত উজ্জ্বল না হলেও হলুদ। আর যথারীতি এই হলুদ রঙ ক্রমশ পেছনদিকে ফ্যাকাসে হতে হতে হয়ে গিয়েছে সাদা। ডানার নিচে ও ঊরুর পালকের রঙও পুরুষদের মতো সাদা। আর এদের চঞ্চুর পেছন থেকে চোখের পেছন পর্যন্ত একটা লম্বা কালো রেখা থাকে। দেখে মনে হবে যেন কেউ কাজল পরিয়ে দিয়েছে। লেজ যথারীতি কালো। মৌটুসিদের চোখের মণি ঘিরে লাল রঙের বৃত্তাকার বর্ডার কোকিলের চোখকে মনে করিয়ে দেয়। দুর্গা টুনটুনিদের মতো এদের চঞ্চুও সরু লম্বা এবং আগার দিকে সামান্য বাঁকা যাতে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। তবে চঞ্চুর আগায় করাতের মতো সামান্য খাঁজ কাটা থাকে।

(বাঁদিকে) স্ত্রী মৌটুসির মধুপান। (ডান দিকে) স্ত্রী মৌটুসির শিশির-স্নান। ছবি: সংগৃহীত।
মৌটুসীদের প্রধান খাবার যে ফুলের মধু সে তো তার নামেই বোঝা যায়। মধু খেতে গিয়ে এরা বহু গাছের ফুলের পরাগমিলন ঘটায়। মধু খাওয়ার দৃশ্যও নয়নমনোহর। পাকা জিমন্যাস্টের মতো গাছে সরু শাখা থেকে ঝুলে হেঁটমুন্ড উর্ধ্বপদ হয়ে মধু খেতে পারে। যদি ফুলের আকার এমন হয় যে ফুলের ভেতর দিয়ে মধুভাণ্ড পর্যন্ত চঞ্চু পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না তখন এরা মধু সংগ্রহের জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। চঞ্চুর আগায় করাতের মতো অংশ দিয়ে ফুলের গোড়া কিছুটা কেটে দেয়। তারপর সেখান দিয়ে চঞ্চু প্রবেশ করিয়ে মধু টেনে নেয়। ঠিক এই কারণে এদের ‘মধুচোর’ পাখি বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে পোকামাকড় খেতেও এরা ওস্তাদ। বিশেষ করে আমার শিউলি ও জামরুল গাছে এদের শুয়োপোকা খেতে প্রায়শই দেখি। অসম্ভব ছটফটে পাখি মৌটুসি। সারাক্ষণ ‘চুই চুই চুই চুই’ করতে করতে এ ডাল থেকে ও ডালে, এ ফুল থেকে ও ফুলে লাফিয়ে চলে। এদের ডাক বেশ তীক্ষ্ণ। সবসময়ই যে একইভাবে এরা ডাকে তা নয়। আমি তো মনোযোগ দিয়ে চার-পাঁচ রকমের ডাক শুনেছি, যেমন চুই চুই, চুই চুই চু, চুই চুই চু চু, চুই চুই চু চু চিক, চুই চুই চু চু চিকিচু … ইত্যাদি।
আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১০৭: লুকাবো বলি, লুকাবো কোথায়?

গল্পবৃক্ষ, পর্ব-২২: নন্দিবিলাস-জাতক: রূঢ়ভাষে কষ্ট কারও করিও না মন
মৌটুসি পাখিরা মাটি থেকে ৪-৫ ফুট উপরে বাসা বানায়। বাসার আকৃতি ও উপাদান হুবহু দুর্গা টুনটুনিদের মতো। জ্ঞাতিভাই বলে কথা! শুকনো ঘাস, শেকড়, শুকনো বাকল, শুকনো মস, শ্যাওলা, সুতো, উল, ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরো, ছেঁড়া প্লাস্টিকের টুকরো বাসার উপকরণ হিসেবে কিছুই বাদ দেয় না এরা। এইসব হাবিজাবি উপকরণের জন্য বাসা দৃষ্টিনন্দন হয় না। তবে অনেক পক্ষী বিশেষজ্ঞের মতে, শত্রু পাখির খপ্পর থেকে ডিম ও ছানা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের ভয় দেখাতে এমন বিচিত্র বাসা তৈরি করে। মাকড়সার জাল দিয়ে বাসাকে এরা শক্তপোক্ত করে গাছের শাখা থেকে ঝুলিয়ে দেয়। মাকড়সার এই জাল সংগ্রহ করার জন্য ওদেরকে মাঝে মাঝেই জানালার উপরে বসতে দেখি।
আরও পড়ুন:
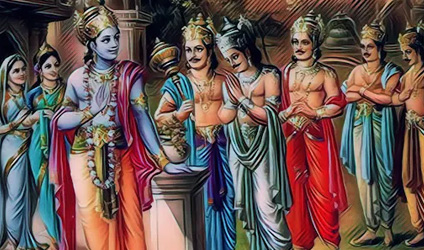
মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০৭: সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কে বা কারা রইলেন পাদপ্রদীপের আলোয়?

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৭০: বিচারক
বাসার ভিতরে থাকে নরম তন্তুর আস্তরণ। এজন্য এরা তুলো ও আকন্দ বীজের রোম ব্যবহার করে। বাসার আকার ঠিক যেন লম্বাটে আকারের কুঁজোর মত। বাসা লম্বায় হয় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি। বাসার উপরের দিকে থাকে গোলাকার একটা ছিদ্র। আর এই ছিদ্রের ওপরে থাকে রোদ-বৃষ্টি আটকানোর জন্য সানসেড। যতবার মৌটুসি ও দুর্গা টুনটুনিদের বাসা আমার নজরে আসে প্রত্যেকবারই এদের এই অনবদ্য প্রকৌশলী বুদ্ধির জন্য মনে মনে সেলাম জানাই। স্ত্রী মৌটুসি একাই এই বাসা বানায়। তবে সেই সময় কাছাকাছি শাখায় বসে পুরুষ মৌটুসি ‘চুই চুই চুই চুই’ করে গান গেয়ে স্ত্রী মৌটুসিকে মানসিক শক্তি ও উৎসাহ জোগায় বলে মনে হয়!
বাসা তৈরি শেষ হলে স্ত্রী পাখি ডিম পাড়ার আগে বাসার ভেতরে ঢুকে দু’চার রাত কাটায়। তারপর সে এক জোড়া ডিম পাড়ে। তবে তা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় মৌটুসির ভূমিকা রয়েছে। ১৪ থেকে ১৬ দিন তা দেওয়ার পর ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে আসে। আর বাচ্চাদের প্রতিপালন করার দায়িত্ব নেয় বাবা ও মা দুজনেই। সাধারণত ১৭ দিন বয়স হলে বাচ্চারা উড়তে শিখে যায়।
বাসা তৈরি শেষ হলে স্ত্রী পাখি ডিম পাড়ার আগে বাসার ভেতরে ঢুকে দু’চার রাত কাটায়। তারপর সে এক জোড়া ডিম পাড়ে। তবে তা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় মৌটুসির ভূমিকা রয়েছে। ১৪ থেকে ১৬ দিন তা দেওয়ার পর ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে আসে। আর বাচ্চাদের প্রতিপালন করার দায়িত্ব নেয় বাবা ও মা দুজনেই। সাধারণত ১৭ দিন বয়স হলে বাচ্চারা উড়তে শিখে যায়।

(বাঁদিকে) পুরুষ মৌটুসি। (ডান দিকে) কলা ফুলে মধুর সন্ধানে পুরুষ মৌটুসি। ছবি: সংগৃহীত।
মৌটুসিদের স্নানের দৃশ্য দেখা আর এক আকর্ষণীয় ব্যাপার। এমন দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আমার অনেকবার হয়েছে। শরতে যখন খুব শিশির পড়ে তখন মানকচুর পাতায় জমে থাকা শিশিরে স্নান করতে দেখেছি। বৃষ্টিতে জমা জলেও দেখেছি স্ত্রী ও পুরুষকে স্নান করতে। মানকচু ছাড়াও কচু পাতা, কলাপাতা আর জামরুলের পাতায় জমা জলেও ওরা স্নান করে। আমগাছে মুকুল এলে আমি মাঝে মাঝে জল স্প্রে করি। দু’বছর আগে একদিন জল স্প্রে করার পর আমগাছে ‘চুই চুই চুই’ শব্দ শুনে দেখি পাতা থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা জলে একটা স্ত্রী মৌটুসি কী সুন্দর বৈকালিক স্নান সারছে! অবশ্য টুনটুনি পাখিদের ক্ষেত্রে এ দৃশ্যের অভিজ্ঞতা আমার সবসময় হয়।
সুন্দরবন অঞ্চলের বসতি এলাকায় মৌটুসিদের অন্তত কোনও বিপদ এই মুহূর্তে রয়েছে বলে মনে হয় না। গ্রাম হোক কিংবা শহর — সর্বত্রই এদের যথেষ্ট উপস্থিতি রয়েছে। গেরস্থের বাগান ওদের বেশি পছন্দ। মৌটুসিদের সান্নিধ্য বেশি বেশি করে পেতে হলে বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করে আমাদের আরও বেশি বেশি মধু উৎপাদক গুল্ম ও বৃক্ষজাতীয় গাছ রোপন করতে হবে। মৌবন না থাকলে মৌটুসিরাও থাকবে না। —চলবে।
সুন্দরবন অঞ্চলের বসতি এলাকায় মৌটুসিদের অন্তত কোনও বিপদ এই মুহূর্তে রয়েছে বলে মনে হয় না। গ্রাম হোক কিংবা শহর — সর্বত্রই এদের যথেষ্ট উপস্থিতি রয়েছে। গেরস্থের বাগান ওদের বেশি পছন্দ। মৌটুসিদের সান্নিধ্য বেশি বেশি করে পেতে হলে বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করে আমাদের আরও বেশি বেশি মধু উৎপাদক গুল্ম ও বৃক্ষজাতীয় গাছ রোপন করতে হবে। মৌবন না থাকলে মৌটুসিরাও থাকবে না। —চলবে।
* সৌম্যকান্তি জানা। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। নিবাস কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পেশা শিক্ষকতা। নেশা লেখালেখি ও সংস্কৃতি চর্চা। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ‘দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২০১৬ সালে ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২০১৭ সালে ‘অমলেশচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি সম্মান’ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।