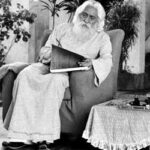“ঘড়িটি বলছে শুনো টিক টিক / সময় যায় যে উড়ে ঠিক ঠিক।” ছোটবেলায় পড়া একটি ছড়ার এই লাইনটি যে কতটা সত্যি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সূর্যচন্দ্র যেমন রোজ আমাদের সঙ্গে থাকে তেমনি সময়ের হাত ধরে পরিবর্তনও আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী হয়ে উঠে। তবে এই পরিবর্তনের চেহারা বড় শান্ত, বড় ধীর লয়ে চলে।
কাছাড়ের শেষ রাজা মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ হরিটিকরে দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হন। সালটা ছিল ১৮৩০। তারপর রাজকর্য ইংরেজ সরকারের হাতে চলে গেল। তখন লেফটেন্যান্ট টমাস ফিশার ছিলেন কাছাড়ের প্রথম শাসক। তখন গভর্নর জেনারেলের হেড কোয়াটার ছিল বর্তমান মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে। কিন্তু এত দূর থেকে শাসনকার্য চালানো সুবিধাজনক মোটেও ছিল না। সুতরাং, ১৮৩৩ সালের শুরুর দিকে হেড কোয়াটার অফ এজেন্ট অফ গভর্নর জেনারেল স্থাপিত হল দুধ পাতিলে। আজ দুধ পাতিলে সেই অফিসের কোনও চিহ্ন নেই। কারণ, ১৮৪৩ সালে এক বীভৎস অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেই অফিসটি পুড়ে যায়। অফিসে থাকা নথিপত্রও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অফিস গড়ে ওঠে শিলচরে।
কাছাড়ের শেষ রাজা মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ হরিটিকরে দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হন। সালটা ছিল ১৮৩০। তারপর রাজকর্য ইংরেজ সরকারের হাতে চলে গেল। তখন লেফটেন্যান্ট টমাস ফিশার ছিলেন কাছাড়ের প্রথম শাসক। তখন গভর্নর জেনারেলের হেড কোয়াটার ছিল বর্তমান মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে। কিন্তু এত দূর থেকে শাসনকার্য চালানো সুবিধাজনক মোটেও ছিল না। সুতরাং, ১৮৩৩ সালের শুরুর দিকে হেড কোয়াটার অফ এজেন্ট অফ গভর্নর জেনারেল স্থাপিত হল দুধ পাতিলে। আজ দুধ পাতিলে সেই অফিসের কোনও চিহ্ন নেই। কারণ, ১৮৪৩ সালে এক বীভৎস অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেই অফিসটি পুড়ে যায়। অফিসে থাকা নথিপত্রও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অফিস গড়ে ওঠে শিলচরে।
কোনও আলাদিনের জিন এসে ধুম করে একটি গ্রামকে শহরে কিংবা একটি শহরকে মহানগরীতে রূপান্তরিত করে দেয় না। এক সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কোনও খবর পৌঁছনো ছিল এক বিশাল ব্যাপার কিন্তু আজ ইন্টারনেটের সাহায্যে নিমিষে খবরের আদান প্রদান হয়ে যায়। মলে ঘেরা শহরগুলির আজকের চেহারা আর আজ থেকে একশো বছর আগের চেহারাও এক ছিল না। আজ আমাদের অসমের শহরগুলিতে সব রকম উন্নত সুযোগ সুবিধে রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গুয়াহাটি, তেজপুর, ডিব্রুগড়-সহ আরও কয়েকটি ছোট-বড় শহর রয়েছে।
আরও পড়ুন:

অসমের আলো অন্ধকার, পর্ব-৪৯: পান-সুপারি ছাড়া অসম্পূর্ণ অসমীয়া খাবারের থালি
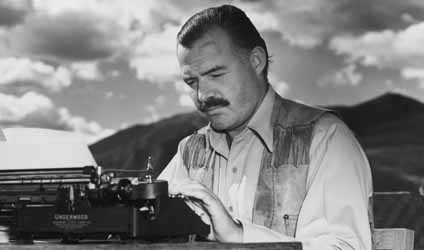
বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-১৭: একাকিত্বের অন্ধকূপ/২: অন্ধকারের উৎস হতে
বরাক উপত্যকার তিনটি বড় শহর শিলচর, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ-সহ আরও কয়েকটি ছোট ছোট শহর। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চিকিৎসার জন্য এবং যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য অন্যান্য শহর গুলিকে শিলচর শহরের উপর নির্ভর করতেই হয়। ১৮৮২ সালে মাত্র বারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত হলো শিলচর স্টেশন কমিটি। এই কমিটির সদস্যদের নিয়েই শুরু হল মিউনিসিপ্যাল্টি কমিটি।
চল্লিশের দশকেও এই শিলচরে বাস বা অন্য ধরনের গাড়ি খুব বেশি দেখা যেত না। আর আজ শহরে গাড়ির ভিড়। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকতায় অনেক কিছু হারিয়ে যায়। গল্পের পাতায় স্থান করে নেই। এই যেমন শিলচরের প্রেমতলায় ছিল গোলদিঘি। আসলে দীঘি ঠিক নয়, ছিল একটা বড় গোল পুকুর। শোনা যায়, চল্লিশের দশকে এই গোলদিঘি এবং তার আশেপাশের জায়গাটিকে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অনেক সভা সমিতিও করেছেন এই গোলদিঘির পাড়ে। এমন কী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষও এই গোলদীঘিতে নেমে সাঁতারের কলা কৌশল শহরবাসিকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।
চল্লিশের দশকেও এই শিলচরে বাস বা অন্য ধরনের গাড়ি খুব বেশি দেখা যেত না। আর আজ শহরে গাড়ির ভিড়। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকতায় অনেক কিছু হারিয়ে যায়। গল্পের পাতায় স্থান করে নেই। এই যেমন শিলচরের প্রেমতলায় ছিল গোলদিঘি। আসলে দীঘি ঠিক নয়, ছিল একটা বড় গোল পুকুর। শোনা যায়, চল্লিশের দশকে এই গোলদিঘি এবং তার আশেপাশের জায়গাটিকে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অনেক সভা সমিতিও করেছেন এই গোলদিঘির পাড়ে। এমন কী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষও এই গোলদীঘিতে নেমে সাঁতারের কলা কৌশল শহরবাসিকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।
আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১৪: বন্দি, জেগে আছো?

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-৪৮: রান্নার জ্বালানি নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ?
শহরে বাসের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস ড্রাইভাররা এখানেই নিজেদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। ফলে দিঘীর সৌন্দর্যহানি হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বাস চালকদের সঙ্গে জুড়ে গেল অটো চালকরাও আর এই গোলদিঘি হয়ে গেল ইতিহাস। আজ সেখানে গোলদিঘি মল রয়েছে। সেই মলে রয়েছে বহু ধরনের দোকান। মল আজ এক ব্যবসায়িক কেন্দ্র স্থল, কিন্তু তাতে চাপা পরে গেল এক সুন্দর ইতিহাস। এই গোলদীঘিকে রক্ষা করলে পারলে শহরের সৌন্দর্যও যে বর্ধিত হত তাতে সন্দেহ নেই।
আরও পড়ুন:

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৭: শ্রীমার কথায় ‘ঠাকুরের দয়া পেয়েচ বলেই এখানে এসেচ’

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫৫: সর্বত্র বরফ, কোত্থাও কেউ নেই, একেবারে গা ছমছম করা পরিবেশ
সময়ের ইঁদুর দৌড়ে দৌড়াতে গিয়ে অনেক সময় আমরা এগিয়ে যাই ,কিন্তু পিছনে পড়ে যায় অনেক কিছুই। আমরা ভুলে যাই সমান্তরাল পথে যে আমাদের পরম বন্ধু প্রকৃতিও আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। আমরা এমন দৌড় দৌড়াই যে, প্রকৃতি রানি আর পেরে উঠে না। এই যেমন বরাক নদীতে এক সময় গাঙ্গেয় নদীর ডলফিন পাওয়া যেত। তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এক সময় এই বরাক নদী এই গাঙ্গেয় ডলফিনদের আবাসস্থল হলেও এখন ডলফিনদের দেখা মেলা ভার। শোনা যায়, ষাঠের দশক পর্যন্ত এই নদীতে প্রচুর ডলফিনদের ঘন বসতি ছিল। অসম মণিপুর সীমান্তে নারায়ণদহ নামে জায়গায় নদীর উজানে ডলফিনদের সংখ্যা বেশি ছিল।
আরও পড়ুন:

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৭৮: রক্তে ভেজা মাটিতে গড়ে ওঠে সত্যিকার প্রাপ্তি

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১১৩: একটি হিংসা অনেক প্রতিহিংসা, জিঘাংসা, হত্যা এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে সর্বত্র
১৯৮৫ সালের আসে পাশে এক দল লোক বহিঃপ্রান্ত থেকে এসে ডলফিন হত্যা শুরু করে। এই ডলফিনের মাংসের চাহিদা খুব একটা ছিল না। কিন্তু ডলফিনের তেল নিষ্কাশন করা হত এবং তা এক ধরনের ওষধ তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হতো। স্থানীয় অনেকে এও মনে করেন যে, এই ষধ এবং তেলের চাহিদা খুব বেশি ছিল। চোরা পথে এই তেল এবং ওষধ নাকী দেশের বাইরেও রপ্তানি হত বলে শোনা যায়। প্রায় দশ বছরের মধ্যে নারায়ণদহের নদীর ডলফিনরা নির্বংশ হয়ে যায়। সরকার এই ডলফিনদের সংরক্ষণ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও, তা কার্যকরী হতে হতে ডলফিনদের সংখ্যা ভয়ঙ্কর ভাবে কমে গেল।
এখন ডলফিন বরাকের জলে দেখা দুষ্কর। ডলফিনদের রক্ষা করার জন্য স্থানীয় মানুষও এগিয়ে আসেনি। ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপালের কয়েকটি নদীতেই এই ডলফিনদের প্রজাতি পাওয়া যায়। এই দুষ্প্রাপ্য প্রজাতিকে রক্ষা করা গেল না, তার দায় ভার কিন্তু সরকার এবং এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ কেউ এড়াতে পারবেন না।—চলবে।
এখন ডলফিন বরাকের জলে দেখা দুষ্কর। ডলফিনদের রক্ষা করার জন্য স্থানীয় মানুষও এগিয়ে আসেনি। ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপালের কয়েকটি নদীতেই এই ডলফিনদের প্রজাতি পাওয়া যায়। এই দুষ্প্রাপ্য প্রজাতিকে রক্ষা করা গেল না, তার দায় ভার কিন্তু সরকার এবং এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ কেউ এড়াতে পারবেন না।—চলবে।
* ড. শ্রাবণী দেবরায় গঙ্গোপাধ্যায় লেখক ও গবেষক, অসম।