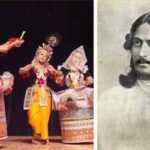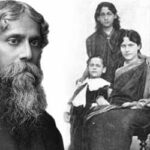ছবি: প্রতীকী। সংগৃহীত।
প্রতিদিন সকাল হলেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যুদ্ধ শুরু হয় চা পান করার মধ্যে দিয়ে। আমরা বাঙালিরা আবার চা খাই! দামি চা, সবুজ চা (গ্রিন টি), ভাঁড়ের চা এরকম কতরকমের চা আমরা আমাদের সারাদিনের জীবনে জুড়ে দিয়েছি। এই জুড়ে দেওয়া আমাদের মনের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে আমাদের মন চা চেয়ে বসল, রোম্যান্টিক হওয়ার উপাদান হিসেবে। কাজের জায়গায় নিজেদের মধ্যে জরুরি আলোচলা করতে হবে চা সেখানে আলোচনায় সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অতিথিকে চা দিয়ে আপ্যায়ন আর সেই সঙ্গে নিজেদের ‘ক্লাস’ বুঝিয়ে দেওয়া চলে। আবার চা বাগানের মধ্যে টিনের ড্রামের মধ্যে ইটের উনুনে চা ফুটছে চা শ্রমিকদের জন্য। সেই কালো চা তে ঔপনিবেশিক সময় থেকে আজ অবধি সময় থমকে আছে। বন্দেভারতের উপস্থিতিও সেই সময়ের মেঘে বিশেষ কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। আমি সেই নরম কোমল হাতের নারী শ্রমিকদের কথা বলছি, যাঁরা চাপাতা তোলেন।
চা পাতা তোলা চা তৈরির প্রাথমিক কাজ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যদি সঠিক পাতা না তোলা হয় তাহলে চায়ের গুণমাণ ব্যাহত হয়। এই গুরুত্বপুর্ন কাজটি যে মেয়েরা করেন তারা মুখ্যত আদিবাসী সম্প্রদায়— ওঁরাও, মুণ্ডা, কুরুখ, মাহালি প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত।
সকালে খুব ভোরেই চা বাগানে পৌঁছে গিয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজ শুরু করেন তবে সন্ধ্যে নাবার আগে বাড়ি ফিরে আসেন কারণ বাড়ি ফেরার পথে চিতা বাঘ বা হাতির আক্রমণের মুখে পড়তে পারেন। এই ধরনের জন্তু আক্রমণ শীতের শেষে শুরু হয় তারপর ক্রমেই বাড়তে থাকে আবার শীত না পড়া অবধি। ফলে জন্তু আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসতে হয়। তারপর মোলাকাত হয় স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে। এদের স্বামীরা সবসময় যে সমাজ স্বীকৃত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী হন তা নয়। এখানে একটি প্রথা এখনও আছে যা এদের পূর্বপুরুষরা বিহার, ছোটনাগপুর, থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন। প্রথাটি হল সঙ্গিনী নির্বাচন করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা।
এই প্রথা ঘটুল প্রথার একটি রূপ বলা যায়। মূল ঘোটুল ব্যবস্থায় গ্রামের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করা হয় যেখানে অবিবাহিত নারী পুরুষ এক সঙ্গে থাকে এবং পরস্পরকে চিনতে শেখে। যৌন সর্ম্পক কি তাও তারা শেখে। কিন্তু উত্তর বঙ্গের চা বাগানের কুলি বস্তিতে এই আলাদা বাড়ি তৈরি সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রথা অন্য ধারায় নিজেকে গড়ে নিয়েছে। নিজেরা নিজেদের বস্তির ঘরেই ঘটুল বানিয়ে নিয়েছে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল কারও পছন্দ না হলে বেরিয়ে যেতে পারে সম্পর্ক থেকে। আবার সারাজীবন এক সঙ্গে থাকতে পারে নিজেদেরকে বিয়ে না করেও। এই অব্ধি পড়ে অনেকের মনে হতে পারে কত আধুনিক এই জীবন। তবে এই আধুনিকতা এই পর্যন্ত।
সকালে খুব ভোরেই চা বাগানে পৌঁছে গিয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজ শুরু করেন তবে সন্ধ্যে নাবার আগে বাড়ি ফিরে আসেন কারণ বাড়ি ফেরার পথে চিতা বাঘ বা হাতির আক্রমণের মুখে পড়তে পারেন। এই ধরনের জন্তু আক্রমণ শীতের শেষে শুরু হয় তারপর ক্রমেই বাড়তে থাকে আবার শীত না পড়া অবধি। ফলে জন্তু আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসতে হয়। তারপর মোলাকাত হয় স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে। এদের স্বামীরা সবসময় যে সমাজ স্বীকৃত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী হন তা নয়। এখানে একটি প্রথা এখনও আছে যা এদের পূর্বপুরুষরা বিহার, ছোটনাগপুর, থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন। প্রথাটি হল সঙ্গিনী নির্বাচন করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা।
এই প্রথা ঘটুল প্রথার একটি রূপ বলা যায়। মূল ঘোটুল ব্যবস্থায় গ্রামের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করা হয় যেখানে অবিবাহিত নারী পুরুষ এক সঙ্গে থাকে এবং পরস্পরকে চিনতে শেখে। যৌন সর্ম্পক কি তাও তারা শেখে। কিন্তু উত্তর বঙ্গের চা বাগানের কুলি বস্তিতে এই আলাদা বাড়ি তৈরি সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রথা অন্য ধারায় নিজেকে গড়ে নিয়েছে। নিজেরা নিজেদের বস্তির ঘরেই ঘটুল বানিয়ে নিয়েছে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল কারও পছন্দ না হলে বেরিয়ে যেতে পারে সম্পর্ক থেকে। আবার সারাজীবন এক সঙ্গে থাকতে পারে নিজেদেরকে বিয়ে না করেও। এই অব্ধি পড়ে অনেকের মনে হতে পারে কত আধুনিক এই জীবন। তবে এই আধুনিকতা এই পর্যন্ত।
আরও পড়ুন:

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-৪৬: নারী কি জলবায়ুর পরিবর্তনের ভোগান্তি রুখতে পরেছে?

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯২: শ্রীমার সঙ্গে এক মেমসাহেবের কথোপকথন
বিনি-মিনির দল এখনও খুব একটা লেখা পড়া করতে চায় না। বাড়ির বড়রা বলেন তারা পড়তে বলেন কিন্তু এরা পড়ে না। আমি বিনি-মিনি দের লেখা পড়া না করার কারণ জিজ্ঞেস করাতে আমাকে জানাল যে তার লেখাপড়া করতে পারেনি কারণ বাড়িতে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, মা এবং বড় দাদারা কাজে বেরিয়েছে। বড় পরিবার, মিনি-বিনিরা বুঝে নিয়েছিল ছোট বয়সে যে তাদের এত বড় পরিবারের বোঝা হয়ে থাকাটা মানাচ্ছে না! তাই তারা বিয়ে করে নিয়েছিল। আমার সংযোজন হল এদের কাছে পড়াশুনা করার পরিবেশ ছিল না। এদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সেরকম ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এদের নিজেদের মধ্যে বলার ভাষা আলাদা। বাড়ির বাইরে হিন্দি বা নেপালি ভাষা রপ্ত করতে হবে। লেখা পড়ার জন্য বাংলা ভাষা। এত জটিলতার মধ্যে পেটের খিদে। ফলে ছোট থেকেই এরা বুঝে যায় নিজেদের জন্য কোনও পথ নির্মাণ করতে হবে।
আরও পড়ুন:

গল্পবৃক্ষ, পর্ব-২৩: তিত্তিরজাতক: পাপ ও আত্মজিজ্ঞাসা

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৪: মৌটুসি
বিনি-মিনির দল এটাও জানে যদি স্বামী বা সঙ্গী বেশি মদ্যপ হয় তাহলে তাদের কে বাগানে কাজ করেই সংসার চালাতে হবে। এরা এটাও জানে এদের কাছে গার্হস্থ্য হিংসা খুব সাধারণ ঘটনা। আমার ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে কেঁপে যাচ্ছে কীভাবে একজন মিনি-বিনিকে সরু লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে দেখে। আর এই মিনি-বিনি মার খেয়েও পরের দিন ভোর বেলায় অ্যাপ্রন পরে ঝোলায় খাবার ভোরে পায়ে মোজা পরে চলে যাচ্ছে চা বাগানে পাতা তুলতে। মিনি বিনির দল পাতা তোলার কাজটাই পায়। চা যেখানে তৈরি হয় অর্থাৎ কারখানাতে এদের কাজ খুবই সীমিত। কারণ জিজ্ঞেস করলেই জানবেন ফ্যাক্টরি তে মেশিন চলে তাই সেটা ‘হাই রিস্ক জোন’। আর ‘হাই রিস্ক জোন’গুলিতে মহিলাদের রাখা যায় না, এটি চা বাগানের নিয়ম।
আমি জিজ্ঞেস করলাম অন্য যারা করেন কাজ, ধরে নিন পুরুষেরা তাদের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে না? উত্তর এল হ্যাঁ হয়। তাহলে? আমি দেখলাম খুব কম সংখ্যক মেয়েকে এই দুর্ঘটনাপ্রবণ জায়গায় রাখা হয়েছে শুধু ঝাট দেওয়ার জন্য। চা তৈরির পর বা বলা ভালো শুকনো হয়ে যাওয়ার পর সাইজ অনুযায়ী আলাদা হয়ে মেশিন থেকে বেরোয়। বেরোনোর সময় পড়ে যায় মেঝেতে কিছুটা। সেই পড়ে যাওয়া চা গুলোকেই গুছিয়ে তুলে রাখার কাজ পায় মেয়েরা।
আমি জিজ্ঞেস করলাম অন্য যারা করেন কাজ, ধরে নিন পুরুষেরা তাদের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে না? উত্তর এল হ্যাঁ হয়। তাহলে? আমি দেখলাম খুব কম সংখ্যক মেয়েকে এই দুর্ঘটনাপ্রবণ জায়গায় রাখা হয়েছে শুধু ঝাট দেওয়ার জন্য। চা তৈরির পর বা বলা ভালো শুকনো হয়ে যাওয়ার পর সাইজ অনুযায়ী আলাদা হয়ে মেশিন থেকে বেরোয়। বেরোনোর সময় পড়ে যায় মেঝেতে কিছুটা। সেই পড়ে যাওয়া চা গুলোকেই গুছিয়ে তুলে রাখার কাজ পায় মেয়েরা।
আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১০: অন্ধকারে, চুপিসারে

ত্রিপুরা: আজ কাল পরশুর গল্প, পর্ব-৫৪: রবীন্দ্রনাথের ‘মুকুট’ ত্রিপুরার ইতিহাসাশ্রিত গল্প
বিনি মিনির দল কে জিজ্ঞেস করলাম এই বড় মেশিন দেখলে ভয় করে কিনা? বললো করে এবং তাদের ইচ্ছে করে না এগুলো ব্যবহার করতে। কত কত শতাব্দী পলি-পাঁক জমেছে এদের শিরায় শিরায় যেখানে বলা আছে মেশিন মেয়েদের জন্য নয়। কে সেগুলো আজকে তুলে সরাবে? তবে মিনি বিনির দল খুব প্রিয় চা বাগানের ম্যানেজার দের। প্রথম এবং প্রধান কারণ মেয়েরা কাজ গুছিয়ে পরিষ্কার করে করেন। কাজের ধরন খুব ভালো বুঝতে পারেন। কাজ শেষ করে তবে বাড়ির পথে এগোন। অর্থাৎ দায়িত্বশীল হয়ে থাকেন মেয়েরা। তবুও এদের একটু শিখিয়ে ফিটারের কাজে নেওয়া হয় না বা ম্যানেজার করা হয় না। বিনি মিনির দল বংশ পরম্পরাতে চা বাগানের পাতা তোলার শ্রমিক অর্থাৎ সবচেয়ে নীচু তলার শ্রমিক হিসেবে থেকে যাচ্ছেন। অথচ পাতা তোলার কাজ সারাবছরের নয়। কিছু মাসের জন্য হয়ে থাকে। চায়ের গুনগত মান পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভীষণ রকম ভাবে নির্ভরশীল।
আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০৮: গার্হস্থ্যজীবনে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের ভাবমূর্তি, তাঁর দেববিগ্রহে উত্তরণের একটি অন্যতম কারণ?

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৯: সে এক স্বপ্নের ‘চাওয়া পাওয়া’
এই বিষয়টি নিয়ে গভীরে ভাবার মধ্যেই এসে যাচ্ছে দারুন রকম ভাবে গজিয়ে ওঠা ইকো ট্যুরিজম-এর রিসোর্ট গুলিতে বিনি মিনির দলের প্রবেশ। এই সব আধুনিক সুবিধা যুক্ত স্থানে গাড়ি হাঁকিয়ে, প্লেনে ট্রেনে চেপে আসা মানুষ প্রকৃতিতে কার্বন মনোক্সাইড যুক্ত করে প্রকৃতি দেখতে আসে। এরা শুধু প্রকৃতির রূপ দেখে সন্তুষ্ট নয়। এদের চাই মনোরঞ্জন। সেই জন্য এই সব রিসর্টে বার্বিকিউ এর সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নৃত্য দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিনি বিনি পয়সা পায়। দিনে রান্নার কাজ, বাসন মাজার কাজ আর রাতে নৃত্য। খুব স্বাভাবিক বা নিজেদের মনের স্ফূর্তির প্রকাশ, এখানে আদিবাসী নাচকে কবে থেকে যেন আমরা পণ্য করে নিয়েছি। কিন্তু বেহুলার দেবতাদের সভায় নৃত্য পরিবেশন করে পরিবার বাঁচানোর গল্পের নোটে শাক এখনও মুড়োলো না।

ছবি: প্রতীকী। সংগৃহীত।
এখন আদিবাসী নারীদের সেই ভূমিকায় নাবিয়ে আনছি। কোনও নৃত্য উৎসব চালু করেছি? আদিবাসী নৃত্য উৎসব, যেখানে সবাই টিকিট কেটে বসে দেখবে। এতদিন এদের সরু আঙুল গুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। এবার এদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নাচ কেও ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। বিনি মিনির দল কাজ শেষ করে লাল টিপ কপালে দিয়ে সারি বেঁধে বেরিয়ে আসে চা বাগান থেকে তখন “একটি কুড়ি দুটি পাতা রতনপুর বাগিচায় অমল কোমল হাত বাড়িয়ে লছমি আজো তোলে” এই অবস্থানের পরিবর্তন প্রার্থনা করি।
—চলবে।
—চলবে।
* বৈষম্যের বিরোধ-জবানি (Gender Discourse): নিবেদিতা বায়েন (Nibedita Bayen), অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ।