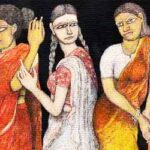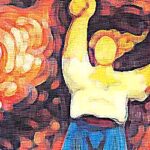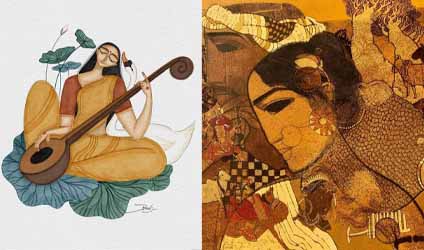
ছবি: প্রতীকী।
ভোর রাতে ওঠা অথবা ভোর রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সন্ধিক্ষণে কিছু শব্দ পাওয়া যায়। কেউ বলবে পাখি গান গাইছে, আবার কেউ বলবে পাখি ডাকছে। এই ডাকের মধ্যে সুর আছে, আবার সমন্বয় আছে, বার্তাও আছে। দিনের আলো ফুটে উঠছে। উঠে পড়তে হবে খাবারের সন্ধান করার তাগিদে।
আমার সেই সুরেলা ডাক শুনে মানুষের গান গাওয়ার প্রচেষ্টার কথা মনে হল। যাত্রাপথে মানুষকে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে দেখেছি। যাত্রা পথের ক্লান্তি বা বিরক্তি কাটানোর একটা সহজ উপায়। কোন ধরনের গান শোনেন জানতে চাইলে একটা লম্বা লিস্ট পেয়ে যাবেন। কেউ শোনেন ধ্রুপদী সঙ্গীত, আবার কেউ ইংরেজি। কেউ রবীদ্রসঙ্গীত তো, কেউ আবার সুমন, নচিকেতা। আবার কেউ নিজের দেশের লোকসঙ্গীত। আবার বিশেষ দিনে দেশাত্মবোধক গান অথবা ভজন গান। আর বাঙালির জীবনে মহালয়ার সকালে রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ-সহ পুরো মহালয়ার অনুষ্ঠানটি শোনা একটি প্রথা এবং অবশ্যই মধ্যবিত্তের প্রথাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কোনও দিন মনে হয়েছে বীরেন্দ্র কৃষ্ণের জায়গায় কোনও মহিলা শিল্পী এই অংশটি বলতেন তাহলে কেমন লাগত শুনতে?
আমার সেই সুরেলা ডাক শুনে মানুষের গান গাওয়ার প্রচেষ্টার কথা মনে হল। যাত্রাপথে মানুষকে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে দেখেছি। যাত্রা পথের ক্লান্তি বা বিরক্তি কাটানোর একটা সহজ উপায়। কোন ধরনের গান শোনেন জানতে চাইলে একটা লম্বা লিস্ট পেয়ে যাবেন। কেউ শোনেন ধ্রুপদী সঙ্গীত, আবার কেউ ইংরেজি। কেউ রবীদ্রসঙ্গীত তো, কেউ আবার সুমন, নচিকেতা। আবার কেউ নিজের দেশের লোকসঙ্গীত। আবার বিশেষ দিনে দেশাত্মবোধক গান অথবা ভজন গান। আর বাঙালির জীবনে মহালয়ার সকালে রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ-সহ পুরো মহালয়ার অনুষ্ঠানটি শোনা একটি প্রথা এবং অবশ্যই মধ্যবিত্তের প্রথাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কোনও দিন মনে হয়েছে বীরেন্দ্র কৃষ্ণের জায়গায় কোনও মহিলা শিল্পী এই অংশটি বলতেন তাহলে কেমন লাগত শুনতে?
আসলে উত্তর হাতড়ানোর দরকার নেই। দরকার হল কীভাবে আমরা সঙ্গীত/গায়কী/ নৃত্য প্রভৃতির সঙ্গে লিঙ্গকে জুড়ে দিয়ে থাকি, সেই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা। সঙ্গীত/গায়কী/ নৃত্য প্রভৃতির সঙ্গে আর একটি বিষয় থাকে সেটি হল গানের বিষয় বস্তু কী এবং কী ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করছে।
বিষয়ের জটিলতায় পৌঁছনোর আগে একটি বিষয় নিয়ে বলে রাখি। বিষয়টি হল গান/ নৃত্য আমরা একা নিজেরা নিজেদের মতো করে করি বেশি, নাকি আমরা সমবেত হয়ে সমবেত জনতার জন্য করি। এই ধরনের প্রক্রিয়া গত বিষয় আমাদের লিঙ্গ ভাবনার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।
বিষয়ের জটিলতায় পৌঁছনোর আগে একটি বিষয় নিয়ে বলে রাখি। বিষয়টি হল গান/ নৃত্য আমরা একা নিজেরা নিজেদের মতো করে করি বেশি, নাকি আমরা সমবেত হয়ে সমবেত জনতার জন্য করি। এই ধরনের প্রক্রিয়া গত বিষয় আমাদের লিঙ্গ ভাবনার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।
আরও পড়ুন:

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-৪৮: রান্নার জ্বালানি নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ?
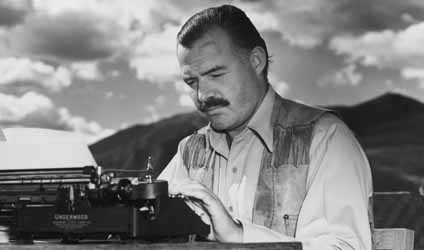
বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-১৭: একাকিত্বের অন্ধকূপ/২: অন্ধকারের উৎস হতে
আমরা যখন জটিল সমাজ গঠন করিনি, তখন বেশি করে সমবেত ভাবে গান গাইতে চাইতাম। সেই চাওয়ার মধ্যে কঠিন পরিস্থিতিতে সবাই একত্রিত ভাবে কীভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে সেই বিষয়টি গুরুত্বপুর্ন ছিল। একা মন খারাপ তাই গাইছি বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে না। এখন আমাদের কাছে এই সঙ্গীত/নৃত্যের রূপটি ধরা দেয় বেশি করে যখন আমরা আদিবাসী নৃত্য উপভোগ করি। আদিবাসী নারীদের দেখেছি নিজেদের মধ্যে একটি বাঁধন তৈরি করে কীভাবে একসঙ্গে একটি তাল তৈরি করে, গানের কথা থাকে সমুচ্চারে। সঙ্গে ধামসা, মাদোল বাজতে থাকে। দূর থেকে শোনা যায়। বার্তা রোটে যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনন্দের, সমবেত থাকার বার্তা। রসদের সন্ধান পাওয়ার বার্তা। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিষয়টি হচ্ছে মেয়েরা নাচ এবং গান করছে আর তাদের সঙ্গত করছে পুরুষেরা ধামসা মাদল বাজিয়ে। এই বাদ্য যন্ত্রগুলি ভারী এবং কায়দা করে বাজাতে হয়। লিঙ্গ বিভাজন হল কীভাবে? তবে কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের দলকে নাচতে এবং বাজাতে দেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মেয়েরাই কি প্রথম থেকে নেচে আসছেন নাকি পরবর্তীতে এই ভাবে গড়ে উঠেছে পুর বিষয়টি?
আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১৪: বন্দি, জেগে আছো?

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৭০: বিচারক
অন্য দিকে শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য মেয়েদের একটি নির্দিষ্ট সুরে গান গাইতে শোনা যায়। খুব জোরে নয় সেই গান। সুরেলা সেই গান কিন্তু একান্তই শিশুর সঙ্গে মায়ের সংযোগ স্থাপনের ভাষা। এই ভাষার মধ্যে মাতৃ স্নেহ, আবেগ আছে। যেখান থেকে মায়ের প্রকৃত ভূমিকা কী তার একটি স্পষ্ট, প্রকট ধারণা তৈরি হয়।
এই নিজের মতে করে সুর করে বার্তা দেওয়া, সন্তানকে হোক বা ঈশ্বর কে বা ভালোবাসার মানুষকে অনেক বেশি আধুনিক ধারণা। এই ধারণা অনেক বেশি মেয়েলি ধারণা। আমরা সিনেমার গান সে বলিউড হোক বা বাংলা সিনেমার হোক রোম্যান্টিক গান মূলত মেয়েদের গাইতে দেখি। পুরুষেরা গায় কিন্তু গানের মধ্যে দিয়ে প্রেমিকার রাগ ভাঙ্গানো বা নিজে প্রেমিক হিসেবে কতটা গ্রহণীয় সেই বিষয়ের প্রকাশ বেশি থাকে। নারীকে লাজুক প্রেমিকা হিসেবে দেখানো হয়। প্রেমিকা কখনই নিজের ইচ্ছে বা সেক্সুয়ালিটি নিয়ে পরিষ্কার করে বলে না। তিনি এখানে প্রেমিকা, প্রেম ভক্তির সংযুক্ত প্রকার যা আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে দেখি সেটাই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেতে দেখি। অর্থাৎ প্রেমিকা নারী হিসেবে রাধাকে ধরে নেবেন আদর্শ প্রেমিকা। রাধার মুখে বসানো প্রেমের কথাই হবে আপামর বাঙালি নারির ভাষা। সেখানে বিচ্যুতি দেখলেই জুটে যাবে তকমা যে সে আইটেম সং গাইছেন। তিনি আর যাইহোক সংস্কারী নারী নন। অর্থাৎ আমাদের সমাজে সবসময় বিষম লিঙ্গ বিভাজন রাখা হয়। সেই সঙ্গে কোন ধরনের নারীকে পিতৃতন্ত্র গ্রহণ করবে আর কাকে গ্রহণ করবে না সেই বিষয়টি ভীষণ রকম ভাবে পরিষ্কার।
এই নিজের মতে করে সুর করে বার্তা দেওয়া, সন্তানকে হোক বা ঈশ্বর কে বা ভালোবাসার মানুষকে অনেক বেশি আধুনিক ধারণা। এই ধারণা অনেক বেশি মেয়েলি ধারণা। আমরা সিনেমার গান সে বলিউড হোক বা বাংলা সিনেমার হোক রোম্যান্টিক গান মূলত মেয়েদের গাইতে দেখি। পুরুষেরা গায় কিন্তু গানের মধ্যে দিয়ে প্রেমিকার রাগ ভাঙ্গানো বা নিজে প্রেমিক হিসেবে কতটা গ্রহণীয় সেই বিষয়ের প্রকাশ বেশি থাকে। নারীকে লাজুক প্রেমিকা হিসেবে দেখানো হয়। প্রেমিকা কখনই নিজের ইচ্ছে বা সেক্সুয়ালিটি নিয়ে পরিষ্কার করে বলে না। তিনি এখানে প্রেমিকা, প্রেম ভক্তির সংযুক্ত প্রকার যা আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে দেখি সেটাই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেতে দেখি। অর্থাৎ প্রেমিকা নারী হিসেবে রাধাকে ধরে নেবেন আদর্শ প্রেমিকা। রাধার মুখে বসানো প্রেমের কথাই হবে আপামর বাঙালি নারির ভাষা। সেখানে বিচ্যুতি দেখলেই জুটে যাবে তকমা যে সে আইটেম সং গাইছেন। তিনি আর যাইহোক সংস্কারী নারী নন। অর্থাৎ আমাদের সমাজে সবসময় বিষম লিঙ্গ বিভাজন রাখা হয়। সেই সঙ্গে কোন ধরনের নারীকে পিতৃতন্ত্র গ্রহণ করবে আর কাকে গ্রহণ করবে না সেই বিষয়টি ভীষণ রকম ভাবে পরিষ্কার।
আরও পড়ুন:

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৭: শ্রীমার কথায় ‘ঠাকুরের দয়া পেয়েচ বলেই এখানে এসেচ’

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫৫: সর্বত্র বরফ, কোত্থাও কেউ নেই, একেবারে গা ছমছম করা পরিবেশ
এই সব কিছুর সঙ্গে আবার এটাও দেখা যায় ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে নারীদের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। তাঁরা তাঁদের নিজেদের যৌণ অনুভূতি বা ইচ্ছে প্রকাশ করছে। তাঁরা নিজেরা জানাচ্ছেন তাদের বিয়ে করার ইচ্ছে। লোকসঙ্গীতের এই ধারার মধ্যে বদল এসেছে। মূল স্রোতে টিকে থাকার তাগিদে এই বদল আনতে হয়েছে।
উনিশ শতকে আমাদের লোকসঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশিত সব ধরনের লিঙ্গের ভাব প্রকাশকে গ্রহণ না করা শুরু হয়েছিল। মূল সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে। মূল কাঠামোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে নতুন নারী নির্মাণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আদর্শ তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ সমাজের মূল্যবোধের ধারণার সূত্র ধরে।
সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। সেই প্রক্রিয়াতে নারীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে না দেখে বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা বেশি। বস্তুর কোনও যৌণ ইচ্ছে থাকে না। তাই পুর বাংলা জুড়ে একটি নিয়মের ধারণায় বাঁধা থেকে, প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে যেখানে নারী ভক্তি, কৃতজ্ঞ এবং নুয়ে পড়া চরিত্রকে কায়েম করে গান গাইবে। কিন্তু নিজের ইচ্ছেকে বক্ত করবে না।
উনিশ শতকে আমাদের লোকসঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশিত সব ধরনের লিঙ্গের ভাব প্রকাশকে গ্রহণ না করা শুরু হয়েছিল। মূল সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে। মূল কাঠামোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে নতুন নারী নির্মাণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আদর্শ তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ সমাজের মূল্যবোধের ধারণার সূত্র ধরে।
সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। সেই প্রক্রিয়াতে নারীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে না দেখে বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা বেশি। বস্তুর কোনও যৌণ ইচ্ছে থাকে না। তাই পুর বাংলা জুড়ে একটি নিয়মের ধারণায় বাঁধা থেকে, প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে যেখানে নারী ভক্তি, কৃতজ্ঞ এবং নুয়ে পড়া চরিত্রকে কায়েম করে গান গাইবে। কিন্তু নিজের ইচ্ছেকে বক্ত করবে না।
আরও পড়ুন:

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৭৮: রক্তে ভেজা মাটিতে গড়ে ওঠে সত্যিকার প্রাপ্তি

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১১৩: একটি হিংসা অনেক প্রতিহিংসা, জিঘাংসা, হত্যা এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে সর্বত্র
ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের শাস্ত্রীয়, ধ্রুপদী সঙ্গীত ঘরণায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অন্য দিকে দক্ষিণ ভারতে মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দেবদাসী প্রথায় আমূল পরিবর্তন আসে। উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে আগে মহিলারা যারা গান গাইতেন তারা ঠুমরি এবং খেয়াল জাতীয় গান গাইতেন। এই সমস্ত গাইয়ে মহিলাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল না। এরা উচ্চবিত্ত, রাজা জমিদার দের সামনে অর্থাৎ নির্বাচিত পুরুষ দর্শকদের সামনে গাইতেন। এই সমস্ত দর্শকদের তারা নানা ভাবে মনোরঞ্জন করতেন। সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ২০১৫ সালের এথনোমিউজিকোলজি গবেষণা জানাচ্ছে এখনও উত্তর ভারতের দ্রুপদ এবং খেয়াল সঙ্গীতকে মনে করা হয় ধ্রুপদী, সঙ্গীত দ্বারা আধিপত্য তৈরি করা, পৌরুষ নির্ভর বিষয়। এর উল্টো দিকের ধারণা হল ঠুমরি, হরি, প্রভৃতি সঙ্গীত অতটাও ধ্রুপদী নয়, কথা এবং অনুভূতি নির্ভর এবং তাই নারী কেন্দ্রিক। পুরুষ নির্ভর সঙ্গীত কখনই আবেগকে পাত্তা দেবে না। আর নারীরা আবেগপ্রবণ, তাই বেশি করে প্রাধান্য দেবে। এই ধরনের সঙ্গীতের লিঙ্গ নির্ধারণ করা শুরু হয়েছিল কারণ পুরুষরা প্রধানত ধ্রুপদ সঙ্গীত পরিবেশন বেশি করতেন। ধরেই নেওয়া হয় পুরুষরা অনেক ভালো পরিবেশন করেন নারীদের থেকে। এখন যখন কোনও নারী শিল্পী পরিবেশন করেন ধ্রুপদী সঙ্গীত তখন সমালোচনায় লেখা হয় যে, নারীদের গলায় মানায় না ধ্রুপদ সঙ্গীত তবুও তারা চেষ্টা করেছেন। ধ্রুপদী সঙ্গীতকে পুরুষালি করে তোলার জন্য গানের কথা বলা হয় একজন বক্তা হিসেবে। সেখানে ঠুমরি গানের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি একজন থাকবে আর গায়িকা আর একজন নায়ক। তিনি একা নন গানের মধ্যেও।
অন্যদিকে, দেবদাসী প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কারণ দেবদাসীরা সারাজীবন দেবতার সেবা করার অঙ্গীকার নেওয়ার মধ্যে দিয়ে মাসোহারা, গয়না, জমি পেতেন। তাদের সেই সম্পদ বাড়ির লোকেরা ব্যবহার করতেন। ঔপনিবেশিককালে এই টাকার যোগান বন্ধ হয়ে গেলে এই দেবদাসী দের জীবনে দুর্দশা নেবে আসে।
নারীদের ব্যবহার করার প্রবণতা সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে। শোষিত হতে হতে কখনও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে বা আন্দোলন একটু বেপথে হাঁটতে শুরু করলে গেল গেল, ভুল পথে হাঁটছে প্রভৃতি বলা বেড়ে যায়। আমাদের প্রশ্ন করার প্রবণতা বাড়াতে হবে। গান গেয়ে হোক বা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেই হোক।—চলবে।
ঋণ স্বীকার https://doi.org/10.1080/17411912.2015.1082925
অন্যদিকে, দেবদাসী প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কারণ দেবদাসীরা সারাজীবন দেবতার সেবা করার অঙ্গীকার নেওয়ার মধ্যে দিয়ে মাসোহারা, গয়না, জমি পেতেন। তাদের সেই সম্পদ বাড়ির লোকেরা ব্যবহার করতেন। ঔপনিবেশিককালে এই টাকার যোগান বন্ধ হয়ে গেলে এই দেবদাসী দের জীবনে দুর্দশা নেবে আসে।
নারীদের ব্যবহার করার প্রবণতা সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে। শোষিত হতে হতে কখনও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে বা আন্দোলন একটু বেপথে হাঁটতে শুরু করলে গেল গেল, ভুল পথে হাঁটছে প্রভৃতি বলা বেড়ে যায়। আমাদের প্রশ্ন করার প্রবণতা বাড়াতে হবে। গান গেয়ে হোক বা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেই হোক।—চলবে।
ঋণ স্বীকার https://doi.org/10.1080/17411912.2015.1082925
* উত্তম কথাচিত্র (Uttam Kumar–Mahanayak–Actor) : ড. সুশান্তকুমার বাগ (Sushanta Kumar Bag), অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, মহারানি কাশীশ্বরী কলেজ, কলকাতা।