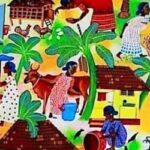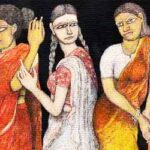ছবি: প্রতীকী। সংগৃহীত।
জলবায়ুর পরিবর্তন বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি আর সেখানে মেয়েদের কথা কীভাবেই বা আমি বলতে চাইছি? সহজ কথায় বললে, পৃথিবীর আবহাওয়া এবং তাপমাত্রার দীর্ঘ মেয়াদী পরিবর্তনকেই বোঝায়। সূর্যের কার্যকলাপের পরিবর্তন কিংবা আগ্নেয়গিরির থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। সেই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক পরিবর্তন বলে ধরে নেওয়া হবে। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপ যখন আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন আমরা সেই ঘটনাকে কীভাবে দেখব?
মূলত কয়লা, গ্যাস, তেল প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানর কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর মতো বেশ কিছু বিষাক্ত গ্যাস যাকে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলি, তা নির্গমন হয়। এই গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে একটি গ্যাসের আবরণ তৈরি করে, যা কম্বলের মতো কাজ করে। ভিতরের তাপ বেরোতে দেয় না। এখানে সূর্যের তাপকে আটকে রাখে। এর ফলে পৃথিবী উষ্ণ হতে থাকে। তাই আবহাওয়া পরিবর্তন হতে থাকে। এতটা পড়ার পর আপনারা বলবেন এই ঘটনার জন্য কারা দায়ী? শুধু মেয়েরা, শুধু ছেলেরা নাকি সব লিঙ্গের মানুষেরাই দায়ী! আবার গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে শুধু বিশ্বব্যাপী নয়, দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকাতে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য।
মূলত কয়লা, গ্যাস, তেল প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানর কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর মতো বেশ কিছু বিষাক্ত গ্যাস যাকে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলি, তা নির্গমন হয়। এই গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে একটি গ্যাসের আবরণ তৈরি করে, যা কম্বলের মতো কাজ করে। ভিতরের তাপ বেরোতে দেয় না। এখানে সূর্যের তাপকে আটকে রাখে। এর ফলে পৃথিবী উষ্ণ হতে থাকে। তাই আবহাওয়া পরিবর্তন হতে থাকে। এতটা পড়ার পর আপনারা বলবেন এই ঘটনার জন্য কারা দায়ী? শুধু মেয়েরা, শুধু ছেলেরা নাকি সব লিঙ্গের মানুষেরাই দায়ী! আবার গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে শুধু বিশ্বব্যাপী নয়, দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকাতে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য।
নারীদের উপরেই যেহেতু পরিবারের সবার খাদ্য এবং পানীয় জল সংগ্রহের দায়িত্ব থাকে, তাই তাদের দেখা গিয়েছে, জল সংগ্রহ করার জন্য মহিলাদের মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়। ভারতের রাজস্থানে এরকম চিত্র আমরা এখনও দেখতে পাই। এখনও অনেক গ্রাম মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে চব্বিশ কিলোমিটার হেঁটে খাবার এবং রান্নার জন্য কাঠ জোগাড় করতে দেখা যায়। সেই সঙ্গে কোন জঙ্গল থেকে উচ্চ জাতির মানুষ আর কোন জঙ্গল থেকে নীচু জাতের মানুষ রসদ সংগ্রহ করবে তাই নিয়ে আজও লড়াই চলছে।
খরা কিংবা বন্যার কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তন এই দুটি বিপর্যয়ের অন্যতম কারণে এখনও মেয়েদেরকেই সমস্যায় পড়তে হয় বেশি। খরা বা বন্যার জন্য তাদের সঞ্চিত শস্য নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। হয় তাদের এই সঞ্চিত শস্য খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়, নয়তো বন্যার জলে নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময়ে বন্যার জন্য বাড়ি জলের তলায় ডুবে গেলে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়। এর ফলে নারীদের মধ্যে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।
এই রকম জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের দারিদ্রতা বৃদ্ধি আর তার জন্য সরকারি স্তরে কী ধরনের নীতি নেওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে বহু আলোচনা, লেখা আমরা দেখছি।
কিন্তু যে বিষয়টি সচরাচর আমরা দেখতে পাই না, তা হল নারীদের নিজস্ব কি ধরনের ভাবনা রয়েছে এই ধরনের পরিস্থিতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্ষেত্রে। নারীদের যেখানে সম্পত্তিতে অধিকার নেই। তাদের নারী হওয়ার জন্য জাতিগত এবং শ্রেণিগত বাধা পেতে হয় প্রতিনিয়ত। যেখানে তাদের সামান্য খোরপোষের জন্য লড়াই করতে হয়, টিটকিরি শুনতে হয়, চাইল্ড কেয়ার লিভ নিলে সেখানে তারা কীভাবে মোকাবিলা করেন? নারীরা প্রথম মাটি খোঁড়ার যন্ত্র বানিয়েছিল (Cat Bohannon 2023) এবং মেয়েরা যন্ত্র বানিয়েছিল খাবার সংগ্রহ করার জন্য। মেয়েরা ঝুড়ি বুনতে শুরু করেছিল শস্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য। তারা যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র বানায়নি।
মেয়েদের এই প্রয়াস আমাদের এই সময়ে ভাবতে বাধ্য করে যে, কীভাবে মেয়েরা বাঁচার এবং বাঁচানোর কৌশল এখনও তৈরি করে যাচ্ছে, যেগুলো পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে কিংবা নারীবাদী আন্দোলনে গুরুত্বহীন থেকে যাচ্ছে।
খরা কিংবা বন্যার কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তন এই দুটি বিপর্যয়ের অন্যতম কারণে এখনও মেয়েদেরকেই সমস্যায় পড়তে হয় বেশি। খরা বা বন্যার জন্য তাদের সঞ্চিত শস্য নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। হয় তাদের এই সঞ্চিত শস্য খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়, নয়তো বন্যার জলে নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময়ে বন্যার জন্য বাড়ি জলের তলায় ডুবে গেলে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়। এর ফলে নারীদের মধ্যে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।
এই রকম জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের দারিদ্রতা বৃদ্ধি আর তার জন্য সরকারি স্তরে কী ধরনের নীতি নেওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে বহু আলোচনা, লেখা আমরা দেখছি।
কিন্তু যে বিষয়টি সচরাচর আমরা দেখতে পাই না, তা হল নারীদের নিজস্ব কি ধরনের ভাবনা রয়েছে এই ধরনের পরিস্থিতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্ষেত্রে। নারীদের যেখানে সম্পত্তিতে অধিকার নেই। তাদের নারী হওয়ার জন্য জাতিগত এবং শ্রেণিগত বাধা পেতে হয় প্রতিনিয়ত। যেখানে তাদের সামান্য খোরপোষের জন্য লড়াই করতে হয়, টিটকিরি শুনতে হয়, চাইল্ড কেয়ার লিভ নিলে সেখানে তারা কীভাবে মোকাবিলা করেন? নারীরা প্রথম মাটি খোঁড়ার যন্ত্র বানিয়েছিল (Cat Bohannon 2023) এবং মেয়েরা যন্ত্র বানিয়েছিল খাবার সংগ্রহ করার জন্য। মেয়েরা ঝুড়ি বুনতে শুরু করেছিল শস্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য। তারা যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র বানায়নি।
মেয়েদের এই প্রয়াস আমাদের এই সময়ে ভাবতে বাধ্য করে যে, কীভাবে মেয়েরা বাঁচার এবং বাঁচানোর কৌশল এখনও তৈরি করে যাচ্ছে, যেগুলো পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে কিংবা নারীবাদী আন্দোলনে গুরুত্বহীন থেকে যাচ্ছে।
আরও পড়ুন:

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-৪৫: গাড়ি ও রাস্তা—বলো তো তুমি কার?

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯o: মা সারদার কথায় ‘ঈশ্বর হলেন বালকস্বভাব’
জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আগেই বলেছি মানুষের ভূমিকা সব থেকে বেশি। এই ভুমিকার মধ্যে একটি বড় কারণ হল গাছ কেটে বানিজ্যিক কাজে লাগানো। বানিজ্যিক কাজে যখন গাছ কাঠ হয়ে যাচ্ছে, তখন তার সামাজিক আর অর্থনৈতিক মূল্য অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সেই মূল্য আরও বাড়ানোর কাজে মনোনিবেশ করেছে আর নারীদের মূল্য ক্রমশ কমিয়ে গিয়েছে।
ভারতের উত্তর প্রান্তে গাড়োয়াল অঞ্চলে এই ভাবে কাঠের মূল্যকে দুর্মূল্য করার খেলায় নেবে এক সময় দেখা গেল পাহাড়ে ধস নামতে শুরু করেছে। এর জেরে স্থানীয় মানুষ এবং অবশ্যই মেয়েরা নানা রকমের সমস্যায় পড়েছেন। পাহাড়ে গুঞ্জন শুরু হল এই সমস্যার কারণ বোঝার জন্য। সমাজের কিছু মানুষ আর মেয়েরা পুরটাই বুঝতে পারলেন খুব সহজে। এই মেয়েরা পাহাড়ি অঞ্চলের গ্রামে থাকা মেয়ে যারা উচ্চ কেন, কোনও রকম শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়নি। তারা দ্রুত পরিস্থিতি বুঝতে পারলেন তথাকথিত মেয়েদের থেকে এগিয়ে থাকা বাকি লিঙ্গের মানুষরা বুঝতে চাইলেন না বা বলব পারলেন না।
পাহাড়ি মেয়েরা এই এপ্রিল মাসে ১৯৭৩ সালে গাছকে জড়িয়ে ধরলেন পরম মমতায়। যেমন করে মেয়েরা তাদের কোমল হৃদয় দিয়ে আগলে রাখে পরিবারের সবাইকে। সেবা দিয়ে সারিয়ে তোলেন, সেই ভাবেই বা বলা ভালো সেই আগলে রাখার দায়িত্ব বোধ দিয়ে তারা গাছকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। এই মেয়েদের কাছে আন্দলনের ভাষা আহিংস এবং একান্তই নিজস্ব। এতদিন যে গুণাবলি মেয়েদের কাছে দাবি করা হত সেই মমতাময়ী হওয়ার গুণ দিয়েই তারা গাছ কাটা আটকে দিতে পেরেছিলেন। সেই সঙ্গে নিজেদের এবং যে মানুষেরা গাছ নিধন যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকেও রক্ষা করলেন। এই রকম সর্ব রক্ষাকারী মনোভাব নারীদের অনেক সময় বিপদে ফেলে। যখন নারীরা সম্পদের আধিকারি হতে পারে না বা বঞ্ছিত হয়, অত্যাচারিত হয় তখনও সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় থেকেও লড়াই করে নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছেন তারা।
আমফান ঝড়ে ইলেকট্রিক তারের খুঁটি উপড়ে গিয়েছিল। এতটাই ঝড়ের দাপট ছিল যে বিদ্যুত দফতরের খুঁটি এই গ্রামে আসার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক সপ্তাহ অন্ধকারে ছিলেন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার এই সব গ্রামের মানুষ। সেই সময় কিছু মেয়ে একত্রিত হয়ে নিজেদের ছোট ফোনের সাহায্যে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে খুঁটি জোগাড় করে গ্রামে বিদ্যুৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন।
ভারতের উত্তর প্রান্তে গাড়োয়াল অঞ্চলে এই ভাবে কাঠের মূল্যকে দুর্মূল্য করার খেলায় নেবে এক সময় দেখা গেল পাহাড়ে ধস নামতে শুরু করেছে। এর জেরে স্থানীয় মানুষ এবং অবশ্যই মেয়েরা নানা রকমের সমস্যায় পড়েছেন। পাহাড়ে গুঞ্জন শুরু হল এই সমস্যার কারণ বোঝার জন্য। সমাজের কিছু মানুষ আর মেয়েরা পুরটাই বুঝতে পারলেন খুব সহজে। এই মেয়েরা পাহাড়ি অঞ্চলের গ্রামে থাকা মেয়ে যারা উচ্চ কেন, কোনও রকম শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়নি। তারা দ্রুত পরিস্থিতি বুঝতে পারলেন তথাকথিত মেয়েদের থেকে এগিয়ে থাকা বাকি লিঙ্গের মানুষরা বুঝতে চাইলেন না বা বলব পারলেন না।
পাহাড়ি মেয়েরা এই এপ্রিল মাসে ১৯৭৩ সালে গাছকে জড়িয়ে ধরলেন পরম মমতায়। যেমন করে মেয়েরা তাদের কোমল হৃদয় দিয়ে আগলে রাখে পরিবারের সবাইকে। সেবা দিয়ে সারিয়ে তোলেন, সেই ভাবেই বা বলা ভালো সেই আগলে রাখার দায়িত্ব বোধ দিয়ে তারা গাছকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। এই মেয়েদের কাছে আন্দলনের ভাষা আহিংস এবং একান্তই নিজস্ব। এতদিন যে গুণাবলি মেয়েদের কাছে দাবি করা হত সেই মমতাময়ী হওয়ার গুণ দিয়েই তারা গাছ কাটা আটকে দিতে পেরেছিলেন। সেই সঙ্গে নিজেদের এবং যে মানুষেরা গাছ নিধন যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকেও রক্ষা করলেন। এই রকম সর্ব রক্ষাকারী মনোভাব নারীদের অনেক সময় বিপদে ফেলে। যখন নারীরা সম্পদের আধিকারি হতে পারে না বা বঞ্ছিত হয়, অত্যাচারিত হয় তখনও সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় থেকেও লড়াই করে নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছেন তারা।
আমফান ঝড়ে ইলেকট্রিক তারের খুঁটি উপড়ে গিয়েছিল। এতটাই ঝড়ের দাপট ছিল যে বিদ্যুত দফতরের খুঁটি এই গ্রামে আসার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক সপ্তাহ অন্ধকারে ছিলেন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার এই সব গ্রামের মানুষ। সেই সময় কিছু মেয়ে একত্রিত হয়ে নিজেদের ছোট ফোনের সাহায্যে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে খুঁটি জোগাড় করে গ্রামে বিদ্যুৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন।
আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৩: সাত-সহেলি

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫১: রোজই দেখি আলাস্কা পর্বতশৃঙ্গের বাঁ দিকের চূড়া থেকে সূর্য উঠতে
ভারতে চিপকো আন্দোলনের আগেই গোটা বিশ্বকে পরিবেশ দূষণের প্রভাব মেয়েদের এবং সমগ্র প্রাণী জগতের মধ্যে কীভাবে পড়ে, সেই বিষয়টি জানিয়ে গিয়েছিলেন রাচেল কারসন। তিনি নিজে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় তার লেখা বই ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ (১৯৬২) প্রথম বিশ্বকে জানায় যে, মানুষের অবিবেচকের মতো কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, পোকা মারার ওষধ, কলকারখানায় রাসায়নিকের ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাকি প্রাণিকুলের অবস্থাও সঙ্গিন হচ্ছে। পৃথিবীর ইকো সিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বাস্তু হারা হচ্ছে। এখনও মনে করা হয় এই অকুতভয় সাংবাদিকের সাহস এবং সহানুভূতিশীল মন গোটা বিশ্বে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ে মানুষকে ভাবাতে সক্ষম করেছেন এবং বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা কী হতে পারে সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।
মেয়েরা বারে বারে চেষ্টা করেছেন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও পরিবেশ নিয়ে সচেতন করে যেতে সবার স্বার্থে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন ভাবে কিছু মানুষের জন্য কিছু উন্নয়নের ব্যাবস্থা করতে হবে তখন বৃহত্তর স্বার্থ আসলে ক্ষুদ্র স্বার্থে পরিণত হয়। এরকম একটি ঘটনা হল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (১৯৮৫)। ভারতের অন্যতম প্রাচীন নদী নর্মদা। এই নদীর উপরে একটি বড় বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সরকার এবং মুখ্য উদ্দ্যেশ ছিল নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের শিল্পাঞ্চালের জলের চাহিদা মেটানো। এই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাণ্ডারি বলে প্রচার করা হলেও পরিকল্পনা ছিল কিছু অঞ্চলের প্রায় লক্ষাধিক মানুষের জীবনকে গুরুত্ব হীন করে দেওয়া। তারা প্রাচীন জনজাতি গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। তাদের সম্পূর্ণ রূপে অঞ্চলচ্যুত করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় কারণ তারা আন্দোলন করতে পারছিলেন না।
এই আন্দলনেও আমরা মেধা পাটেকরকে দেখতে পাই অগ্রণী ভূমিকা নিতে। তার ডাকে বহু মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন এবং বিশ্বে উন্নয়নের ধারনাতে বদল আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহু গবেষণার জন্ম তিনি দিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক পরিবেশে আমরা উন্নয়নের নামে একদল মানুষকে বঞ্চিত করে দিতে পারি না সেই বিষয়টি আবারও গণতান্ত্রিক ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন মেধা পাটেকর।
মেয়েরা বারে বারে চেষ্টা করেছেন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও পরিবেশ নিয়ে সচেতন করে যেতে সবার স্বার্থে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন ভাবে কিছু মানুষের জন্য কিছু উন্নয়নের ব্যাবস্থা করতে হবে তখন বৃহত্তর স্বার্থ আসলে ক্ষুদ্র স্বার্থে পরিণত হয়। এরকম একটি ঘটনা হল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (১৯৮৫)। ভারতের অন্যতম প্রাচীন নদী নর্মদা। এই নদীর উপরে একটি বড় বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সরকার এবং মুখ্য উদ্দ্যেশ ছিল নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের শিল্পাঞ্চালের জলের চাহিদা মেটানো। এই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাণ্ডারি বলে প্রচার করা হলেও পরিকল্পনা ছিল কিছু অঞ্চলের প্রায় লক্ষাধিক মানুষের জীবনকে গুরুত্ব হীন করে দেওয়া। তারা প্রাচীন জনজাতি গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। তাদের সম্পূর্ণ রূপে অঞ্চলচ্যুত করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় কারণ তারা আন্দোলন করতে পারছিলেন না।
এই আন্দলনেও আমরা মেধা পাটেকরকে দেখতে পাই অগ্রণী ভূমিকা নিতে। তার ডাকে বহু মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন এবং বিশ্বে উন্নয়নের ধারনাতে বদল আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহু গবেষণার জন্ম তিনি দিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক পরিবেশে আমরা উন্নয়নের নামে একদল মানুষকে বঞ্চিত করে দিতে পারি না সেই বিষয়টি আবারও গণতান্ত্রিক ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন মেধা পাটেকর।
আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১০৭: লুকাবো বলি, লুকাবো কোথায়?

গল্পবৃক্ষ, পর্ব-২২: নন্দিবিলাস-জাতক: রূঢ়ভাষে কষ্ট কারও করিও না মন
আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম পরিবেশ যে ভাবে আমাদের রসদ দিয়ে যেতে থাকে সেই ভাবে নারীরাও ভরিয়ে দিতে থাকে মানুষের সমাজের বিভিন্ন দিককে। মেয়েদের সঙ্গে পরিবেশের একটি যোগসূত্র দেখানো শুরু হল। নারীদের মূল্য আর পরিবেশের মূল্য একাসনে বসানোর কথা বলা হল। পরিবেশে যে ভাবে আগ্রাসন ফলানো হয় আর তার ফলে পরিবেশ যে ভাবে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, নারীদের উপরে অত্যাচার হলে সেই ভাবেই নারীরা ক্ষতি গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই ক্ষতির ধারণা থেকে নারী এবং পরিবেশ দুজনকেই উদ্ধার করতে হবে এই মনোভাব গড়ে উঠল । কিন্তু পিতৃতন্ত্র ধারণা পরিষ্কার করতে পারল না যে মেয়েদের এবং পরিবেশ উভয়কেই সময় দিলেই নিজেরাই আবার নিরময় করে নিতে পারে নিজেদের।
পিতৃতান্ত্রিক সত্ত্বা অভিভাবকের দায়িত্ব ছাড়তে নারাজ। সেই কারনে মেয়েদের সন্তান ধারণে সমস্যা হলে আইভিএফ, যা একধরনের সাহায্য কারি প্রযুক্তি দিয়ে শরীর সারিয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়ার উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। অন্য দিকে ‘জেনেটিক্যালি মডিফায়েড’ বীজ দিয়ে চাষ করে অধিক উৎপাদন করানোর চেষ্টা চলছে। ফল দিলে রাখা হচ্ছে গাছ আর না দিলে কেটে ফেলা হচ্ছে। পরিবেশ এবং মেয়েদের মূল্য এখন নির্ধারিত হচ্ছে তাদের ফল দেওয়ার ক্ষমতার অর্থাৎ সে সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম কিনা। তাই এখনও সমাজে বিসমকামিতা অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। বহু লিঙ্গের ধারনাকে এখনও অসুখ বলে মনে করা হচ্ছে।
পিতৃতান্ত্রিক সত্ত্বা অভিভাবকের দায়িত্ব ছাড়তে নারাজ। সেই কারনে মেয়েদের সন্তান ধারণে সমস্যা হলে আইভিএফ, যা একধরনের সাহায্য কারি প্রযুক্তি দিয়ে শরীর সারিয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়ার উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। অন্য দিকে ‘জেনেটিক্যালি মডিফায়েড’ বীজ দিয়ে চাষ করে অধিক উৎপাদন করানোর চেষ্টা চলছে। ফল দিলে রাখা হচ্ছে গাছ আর না দিলে কেটে ফেলা হচ্ছে। পরিবেশ এবং মেয়েদের মূল্য এখন নির্ধারিত হচ্ছে তাদের ফল দেওয়ার ক্ষমতার অর্থাৎ সে সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম কিনা। তাই এখনও সমাজে বিসমকামিতা অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। বহু লিঙ্গের ধারনাকে এখনও অসুখ বলে মনে করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন:
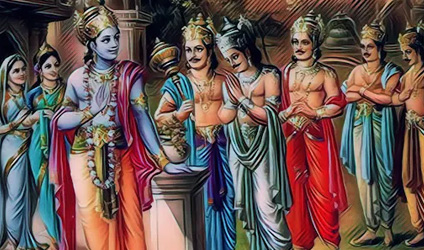
মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০৭: সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কে বা কারা রইলেন পাদপ্রদীপের আলোয়?

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৭০: বিচারক
পরিবেশ বা নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণ মূলক ধারণার আদল বদলালেও নারীদের আন্দোলন কিন্তু থেমে যায়নি। ২০১৮ সালের ষোল বছরের ছাত্রী গ্রেটা থানবারগ এর আন্দোলনের কথা ভুলে গেলে হবে না। ভারতের লিসি প্রিয়া কাঙ্গুজামের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। সেও গ্রেটা থুনবার্গ-এর আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ ভাষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।
এছাড়াও বহু নারি আছেন যারা বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত করছেন মানুষকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করার জন্য। এরকম একটি প্রয়াস হল বাড়ির রান্না ঘরে উৎপন্ন হওয়া বা বাড়ির মধ্যে যে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে দিয়ে কতরকম ভাবে পুনঃব্যবহার করা যেতে পারে। যেখানে পৌরসভা বর্জ্যের গুরুত্ব বুঝতে নারাজ সেখানে মেয়েরা সার তৈরি করা থেকে গাছ লাগানোর পাত্র থেকে শুরু করে নতুন রান্নার রেসিপি তৈরি করছেন।
এছাড়াও বহু নারি আছেন যারা বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত করছেন মানুষকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করার জন্য। এরকম একটি প্রয়াস হল বাড়ির রান্না ঘরে উৎপন্ন হওয়া বা বাড়ির মধ্যে যে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে দিয়ে কতরকম ভাবে পুনঃব্যবহার করা যেতে পারে। যেখানে পৌরসভা বর্জ্যের গুরুত্ব বুঝতে নারাজ সেখানে মেয়েরা সার তৈরি করা থেকে গাছ লাগানোর পাত্র থেকে শুরু করে নতুন রান্নার রেসিপি তৈরি করছেন।
* বৈষম্যের বিরোধ-জবানি (Gender Discourse): নিবেদিতা বায়েন (Nibedita Bayen), অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ।