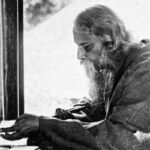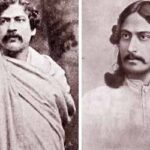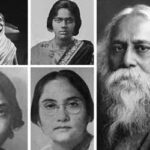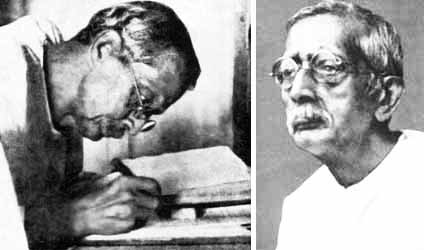
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত।
‘দিনে তো সেরেস্তার কাজে ব্যস্ত থাকো, রাতে কি করো?’ বাবু মশাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে পতিসরের জমিদারের আমিনের সেরেস্তায় কর্মরত ব্রাহ্মণ খুবই নম্রভাবে জানালেন—’সন্ধ্যার পর সংস্কৃতের চর্চা করি আর কিছুটা সময় একটি বইয়ের পান্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি পান্ডুলিপি প্রস্তুত করি।’
শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বাবু মশাই। দেখতে চাইলেন পান্ডুলিপি। তবে শুধু দেখলেনই, কিন্তু কোন কথা না বলেই ফিরে চলে গেলেন। ভাবছেন তো কার কথা বলছি? এই আমিনের ঋজুদেহি ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বাবুমশাই হলেন স্বয়ং রবি ঠাকুর।
হরিচরণের জন্ম ১৮৬৭ সালের ২৩ জুন। বাবা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মা জগদমোহিনী দেবী। ছোটবেলা থেকে তাঁর বড় হওয়া মামার বাড়িতেই। তারপর চলে যান ২৪ পরগনার যশাইকাটিতে। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন ওখানে। তারপর কলকাতায় এসে পড়াশোনা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে। বর্তমানে যা বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। কিন্তু বিএ পড়তে পড়তে স্টুডেন্ট ফান্ডের টাকা বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর আর পড়াশোনা করা হয়নি।
শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বাবু মশাই। দেখতে চাইলেন পান্ডুলিপি। তবে শুধু দেখলেনই, কিন্তু কোন কথা না বলেই ফিরে চলে গেলেন। ভাবছেন তো কার কথা বলছি? এই আমিনের ঋজুদেহি ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বাবুমশাই হলেন স্বয়ং রবি ঠাকুর।
হরিচরণের জন্ম ১৮৬৭ সালের ২৩ জুন। বাবা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মা জগদমোহিনী দেবী। ছোটবেলা থেকে তাঁর বড় হওয়া মামার বাড়িতেই। তারপর চলে যান ২৪ পরগনার যশাইকাটিতে। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন ওখানে। তারপর কলকাতায় এসে পড়াশোনা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে। বর্তমানে যা বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। কিন্তু বিএ পড়তে পড়তে স্টুডেন্ট ফান্ডের টাকা বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর আর পড়াশোনা করা হয়নি।
অগত্যা গ্রামে ফিরে কিছুকাল সেখানকার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে মেদিনীপুরের নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানকে গৃহশিক্ষক হিসেবে পড়াতে যান। কিন্তু সেই সময়ের তুলনায় টাকা খুব কম পাওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে সেই গৃহ শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। ততদিনে তাঁর কাছে এক অগ্রজের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত পতিসর কাছারিতে শৈলেশচন্দ্রের অধীনে একটি কাজের সুযোগ পান।
ঘটনার সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। পান্ডুলিপি দেখে নিরব রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিন পরই পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্রের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন—’শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।’
হরিচরণ শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে রবি ঠাকুর বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখের সঙ্গে একই সারিতে তাঁকে ঠাঁই দিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হিসেবে। এ ভাবেই শিক্ষকতা করলেন তিনি প্রায় তিন বছর।
ঘটনার সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। পান্ডুলিপি দেখে নিরব রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিন পরই পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্রের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন—’শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।’
হরিচরণ শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে রবি ঠাকুর বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখের সঙ্গে একই সারিতে তাঁকে ঠাঁই দিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হিসেবে। এ ভাবেই শিক্ষকতা করলেন তিনি প্রায় তিন বছর।
আরও পড়ুন:

অজানার সন্ধানে: পাচার হয়েছিল টন টন সোনা ও দামি ধাতু! ৮৫ বছরের সেই ভূতুড়ে রেলস্টেশন এখন অভিজাত হোটেল

ক্যাবলাদের ছোটবেলা, পর্ব-৪: এ শুধু অলস মায়া?
তারপর হঠাৎ একদিন রবিবাবু হরিচরণের কাছে একটা আবদার করে বসলেন। বললেন—’আমাদের বাংলা ভাষায় কোনও অভিধান নেই। তোমাকে একখানি অভিধান লিখতে হবে।’ শুনে প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন হরিচরণ। কিন্তু বাবুমশাই তো যে সে লোক নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর কথাকে অমান্য করার কোনও জো নেই। অতএব অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে লেখার কাজে মনোযোগী হলেন হরিচরণ।
দিন রাত এক করে চলল তার অভিধান লেখার কাজ। তাঁর পরিশ্রম দেখে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিপাঠীকে লিখেছিলেন—’এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহান ভাব দূর হইবে।’ মাঝে হরিচরণ খুব আর্থিক অনটনে পড়লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য পরে চার বছর তিনি পেয়েছিলেন ৬০ টাকা করে। এই টাকা পেয়ে আপ্লুত হয়ে কৃতজ্ঞতার অভিভূত ও আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে থাকেন হরিচরণ। এই টাকা পাওয়ার পর তিনি কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান বরাবরের জন্য।
দিন রাত এক করে চলল তার অভিধান লেখার কাজ। তাঁর পরিশ্রম দেখে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিপাঠীকে লিখেছিলেন—’এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহান ভাব দূর হইবে।’ মাঝে হরিচরণ খুব আর্থিক অনটনে পড়লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য পরে চার বছর তিনি পেয়েছিলেন ৬০ টাকা করে। এই টাকা পেয়ে আপ্লুত হয়ে কৃতজ্ঞতার অভিভূত ও আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে থাকেন হরিচরণ। এই টাকা পাওয়ার পর তিনি কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান বরাবরের জন্য।
আরও পড়ুন:
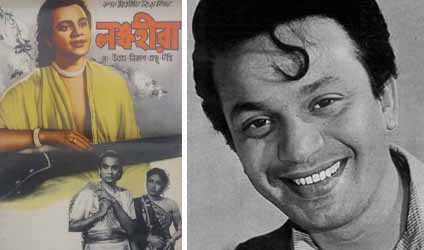
উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৩৯: পথের প্রান্তে রয়ে গিয়েছে সে হাজার তারার ‘লক্ষহীরা’

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-২: চলমান সুন্দরবন
প্রায় দু’ দশকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে তিনি খানিকটা পান্ডুলিপি প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর কোষাগার তখন প্রায় শূন্য। কোষাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন, এই বই ছাপার জন্য লাগবে অন্তত ৫০ হাজার টাকা। ভারী দুশ্চিন্তায় পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। তাহলে কি এতদিনের নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে? বার বারই রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার মিটিংয়ে বসতে লাগলেন এই বিষয় নিয়ে। কিন্তু এর কোনও সমাধান সূত্রই তো মিলল না।
অবশেষে বিশ্বকোষের নগেন্দ্রনাথ বসু রাজি হলেন বইটি প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু তার একটি শর্ত ছিল। শর্তটি হল কাগজের দাম তখনই দিয়ে দিতে হবে। ছাপার খরচ পরে দিলেও চলবে। তখন হরিচরণ তাঁর জীবনের সবটুকু সঞ্চয় দিয়ে বইটি প্রকাশ করলেন। প্রায় ১৩ বছর ধরে বইটি মোট ১০৫টি খণ্ডে প্রকাশিত হল।
এই বইটি বিক্রি করতে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন রথীন ঠাকুর, আশ্রমিক সংঘ বিশ্বভারতী সংসদ কর্তৃপক্ষ প্রমুখ।
বইটি প্রকাশ পাওয়ার পর তখনকার পত্রপত্রিকাগুলোতে হরিচরণকে ধন্য ধন্য করা হল। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও তাঁর হরিজন পত্রিকায় তাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলবার্ট মারের সঙ্গে তুলনাও করেছিলেন।
অবশেষে বিশ্বকোষের নগেন্দ্রনাথ বসু রাজি হলেন বইটি প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু তার একটি শর্ত ছিল। শর্তটি হল কাগজের দাম তখনই দিয়ে দিতে হবে। ছাপার খরচ পরে দিলেও চলবে। তখন হরিচরণ তাঁর জীবনের সবটুকু সঞ্চয় দিয়ে বইটি প্রকাশ করলেন। প্রায় ১৩ বছর ধরে বইটি মোট ১০৫টি খণ্ডে প্রকাশিত হল।
এই বইটি বিক্রি করতে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন রথীন ঠাকুর, আশ্রমিক সংঘ বিশ্বভারতী সংসদ কর্তৃপক্ষ প্রমুখ।
বইটি প্রকাশ পাওয়ার পর তখনকার পত্রপত্রিকাগুলোতে হরিচরণকে ধন্য ধন্য করা হল। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও তাঁর হরিজন পত্রিকায় তাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলবার্ট মারের সঙ্গে তুলনাও করেছিলেন।
আরও পড়ুন:

পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-১৬: ‘ও হানসিনি, মেরি হানসিনি কাঁহা উড় চলি’—কিশোর-পঞ্চম ম্যাজিক চলছেই

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-২৫: আমাদের নাকি রোজই চুল পড়ে!
হরিচরণের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে দুই খণ্ডে সমগ্র অভিধানটি সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়, যা এখনও সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত।
নিয়মনিষ্ঠ এই হরিচরণ গুরুদক্ষিণা হিসাবে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বঙ্গীয় শব্দকোষকে নিবেদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অর্পণ করেছিলেন তাঁর দুটি মহা মূল্যবান চোখকে। কারণ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে পাড়ি দেন। অতুলপ্রসাদের গানের মাধ্যমে তাঁর প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি—
রয়েছিস যদি সাথে, দারুণ এই আধার রাতে।
এখন ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নিয়ে যা হাতে হাতে।
নিয়মনিষ্ঠ এই হরিচরণ গুরুদক্ষিণা হিসাবে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বঙ্গীয় শব্দকোষকে নিবেদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অর্পণ করেছিলেন তাঁর দুটি মহা মূল্যবান চোখকে। কারণ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে পাড়ি দেন। অতুলপ্রসাদের গানের মাধ্যমে তাঁর প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি—
রয়েছিস যদি সাথে, দারুণ এই আধার রাতে।
এখন ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নিয়ে যা হাতে হাতে।
* অজানার সন্ধানে (Unknown story): ড. সঞ্চিতা কুণ্ডু (Sanchita Kundu) সংস্কৃতের অধ্যাপিকা, হুগলি মহসিন কলেজ।