
ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই।
ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতেন। চাঁদের ওঠার ওপর নির্ভর করে হিজরি সন গণনা করা হতো। আর চাষবাস নির্ভর করত সৌরবছরের উপর। এতে অসময়ে কৃষকদের খাজনা দিতে অসুবিধা হতো। ফলে তাঁরা বেশ সমস্যায় পড়তেন। সেই জন্যে সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ‘ফসলি সন’। পরে একে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ বলা হয়ে থাকে। আবার অনেকের মতে, এই বঙ্গাব্দের সূচনা করেন রাজা শশাঙ্ক।
তবে আমরা বলতে পারি, আকবরের আমল থেকেই পয়লা বৈশাখ উদ্যাপিত হতে শুরু করে। জানা যায়, এই দিনেই হজরত মহম্মদ কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় যান। এই ঘটনা আরবিতে ‘হিজরত নামে পরিচিত। এর ৯৬৩ বছর পর যখন আকবর সিংহাসনে বসেন (৯৬৩ হিজরি, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ), তখন থেকেই এই হজরত মহম্মদের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্য দিনটি পালন করতে শুরু করেন।
এ ভাবে, একটি চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে যে হিজরি সালটি প্রচলিত ছিল তা সকলের পক্ষে অসুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তখন বাদশাহ (সম্রাট) তার দরবারের অনেক পণ্ডিতদের মধ্যে একজন, ফতেল্লুআহ শিবাজীকে দায়িত্ব দেন ছয়টি ঋতুর প্রকৃতি, সময়কাল এবং কৃষিতে অবদানের কথা মাথায় রেখে নতুন বর্ষের পরিকল্পনা করতে।
পয়লা বৈশাখ বাংলার নববর্ষ। এককথায় বলা যায়, বাংলা বছরের প্রথম দিন। প্রকৃতপক্ষে এ হল নতুন বছরকে বরণ করে নেবার এক উৎসব। অতীতে পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল হালখাতার দিন। সংস্কৃত ও ফারসি—দু’টি ভাষাতেই ‘হাল’ শব্দটিকে আমরা পেয়ে থাকি। সংস্কৃত ‘হল’ শব্দের অর্থ লাঙল। তার থেকে বাংলায় এসেছে হাল শব্দটি। আর ফারসি ‘হাল’ শব্দের অর্থ নতুন। তখনকার দিনে এই সময় রাজা, মহারাজ, সম্রাটরা প্রজাদের কাছ থেকে কৃষিজমির যা খাজনা বাকি থাকতো তা আদায় করতেন।
তবে আমরা বলতে পারি, আকবরের আমল থেকেই পয়লা বৈশাখ উদ্যাপিত হতে শুরু করে। জানা যায়, এই দিনেই হজরত মহম্মদ কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় যান। এই ঘটনা আরবিতে ‘হিজরত নামে পরিচিত। এর ৯৬৩ বছর পর যখন আকবর সিংহাসনে বসেন (৯৬৩ হিজরি, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ), তখন থেকেই এই হজরত মহম্মদের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্য দিনটি পালন করতে শুরু করেন।
এ ভাবে, একটি চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে যে হিজরি সালটি প্রচলিত ছিল তা সকলের পক্ষে অসুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তখন বাদশাহ (সম্রাট) তার দরবারের অনেক পণ্ডিতদের মধ্যে একজন, ফতেল্লুআহ শিবাজীকে দায়িত্ব দেন ছয়টি ঋতুর প্রকৃতি, সময়কাল এবং কৃষিতে অবদানের কথা মাথায় রেখে নতুন বর্ষের পরিকল্পনা করতে।
পয়লা বৈশাখ বাংলার নববর্ষ। এককথায় বলা যায়, বাংলা বছরের প্রথম দিন। প্রকৃতপক্ষে এ হল নতুন বছরকে বরণ করে নেবার এক উৎসব। অতীতে পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল হালখাতার দিন। সংস্কৃত ও ফারসি—দু’টি ভাষাতেই ‘হাল’ শব্দটিকে আমরা পেয়ে থাকি। সংস্কৃত ‘হল’ শব্দের অর্থ লাঙল। তার থেকে বাংলায় এসেছে হাল শব্দটি। আর ফারসি ‘হাল’ শব্দের অর্থ নতুন। তখনকার দিনে এই সময় রাজা, মহারাজ, সম্রাটরা প্রজাদের কাছ থেকে কৃষিজমির যা খাজনা বাকি থাকতো তা আদায় করতেন।
তবুও পয়লা বৈশাখ ছিল উদযাপনের দিন। কোনও বিদ্রোহ এড়াতে, বাদশা আকবর নতুন করে বছর উদযাপনের এই প্রথা চালু করেছিলেন, যা কর-প্রদানের দিনের ঠিক পরের দিন সংঘটিত হতো। এই দিনটিতে যে সব বিনোদন এবং ভোজের আয়োজন করা হতো যা কর প্রদানের কঠোরতাকে মসৃণ করতো। সর্বোপরি, জনসাধারণের মধ্যে আগামী নতুন বছরে ভালো থাকার আশা জাগাতো।
বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খান জমিদারদের উপর নবাবি কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে বৈশাখে ‘পুণ্যাহ’ প্রথা চালু করেন। সেই সময়ে জমিদাররা নৌকো, পালকিতে করে মুর্শিদাবাদে এসে নবাবের দরবারে খাজনা জমা দিতেন। তারপর তাঁকে সোনার মোহর নজরানা হিসাবে দেওয়া হতো। নবাবও তাঁদের পদমর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন উপকরণ যেমন পাগড়ি, পোশাক, কোমরবন্ধ ইত্যাদি দান করতেন। জানা যায়, এই রকম একটি অনুষ্ঠানে বাংলার নানা অঞ্চল থেকে প্রায় চারশো জমিদার আর রাজকর্মচারী এসে খাজনা জমা দিয়েছিলেন।
যাই হোক, মুর্শিদকুলি খান ‘পুণ্যাহ’ নাম দিলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল হালখাতারই উতসব। সম্রাট প্রচলিত এই পয়লা বৈশাখ নবাবের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের থেকে ক্রমশ পশ্চিমবাংলায়ও নববর্ষ পালন শুরু হতে থাকে।
আবার প্রাচীনকালের মানুষ যারা চন্দ্র-সূর্যের গতি লক্ষ্য করে বছর গণনা করতে জানতেন না, তারা অগ্রহায়ণ (অগ্র অর্থাৎ প্রথম, হায়ন অর্থ বৎসর) মাসকেই প্রথম মাস হিসেবে ধরে নিতেন। এবং এই মাস থেকে নতুন বৎসর গণনা করতেন। এর পিছনে যুক্তি ছিল কৃষিপ্রধান এই দেশে সেই সময়ে কৃষকের ঘর নতুন ফসলে ভরে উঠত। তাই তাদের কাছে হেমন্ত ঋতুর অগ্রহায়ণই ছিল শ্রেষ্ঠ মাস বা প্রথম মাস। নববর্ষের এই উৎসব তখনকার দিনে গ্রামীণ কৃষিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
এই উৎসব ছিল একান্ত ভাবেই নতুন ফসলের আগমনের অনুষ্ঠান। বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে এর ছোঁয়া তখনও পড়েনি। আসলে সে যুগে বাংলায় নববর্ষের ধারণা ছিল অন্য রকম। অতীতে হিম (শীত) ঋতু থেকে বর্ষ গণনা আরম্ভ হতো। মানুষরা আশা করতেন, আমরা যেন শত শরৎ জীবিত থাকি। এই ‘শরৎ’ শব্দের দ্বারা তৎকালীন সময়ে বছরকেই বোঝানো হতো। আর তিথি-নক্ষত্র দেখে বর্ষা আর শরৎকালের সন্ধিক্ষণকেই বলা হতো নববর্ষ প্রবেশের উৎসব। অষ্টমী পুজো শেষে নবমী শুরুর সন্ধিক্ষণ ছিল পুরনো বছর শেষ, নতুন বছরের শুরু। তখন ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে নতুন বছরকে বরণ করা হতো।
বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খান জমিদারদের উপর নবাবি কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে বৈশাখে ‘পুণ্যাহ’ প্রথা চালু করেন। সেই সময়ে জমিদাররা নৌকো, পালকিতে করে মুর্শিদাবাদে এসে নবাবের দরবারে খাজনা জমা দিতেন। তারপর তাঁকে সোনার মোহর নজরানা হিসাবে দেওয়া হতো। নবাবও তাঁদের পদমর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন উপকরণ যেমন পাগড়ি, পোশাক, কোমরবন্ধ ইত্যাদি দান করতেন। জানা যায়, এই রকম একটি অনুষ্ঠানে বাংলার নানা অঞ্চল থেকে প্রায় চারশো জমিদার আর রাজকর্মচারী এসে খাজনা জমা দিয়েছিলেন।
যাই হোক, মুর্শিদকুলি খান ‘পুণ্যাহ’ নাম দিলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল হালখাতারই উতসব। সম্রাট প্রচলিত এই পয়লা বৈশাখ নবাবের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের থেকে ক্রমশ পশ্চিমবাংলায়ও নববর্ষ পালন শুরু হতে থাকে।
আবার প্রাচীনকালের মানুষ যারা চন্দ্র-সূর্যের গতি লক্ষ্য করে বছর গণনা করতে জানতেন না, তারা অগ্রহায়ণ (অগ্র অর্থাৎ প্রথম, হায়ন অর্থ বৎসর) মাসকেই প্রথম মাস হিসেবে ধরে নিতেন। এবং এই মাস থেকে নতুন বৎসর গণনা করতেন। এর পিছনে যুক্তি ছিল কৃষিপ্রধান এই দেশে সেই সময়ে কৃষকের ঘর নতুন ফসলে ভরে উঠত। তাই তাদের কাছে হেমন্ত ঋতুর অগ্রহায়ণই ছিল শ্রেষ্ঠ মাস বা প্রথম মাস। নববর্ষের এই উৎসব তখনকার দিনে গ্রামীণ কৃষিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
এই উৎসব ছিল একান্ত ভাবেই নতুন ফসলের আগমনের অনুষ্ঠান। বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে এর ছোঁয়া তখনও পড়েনি। আসলে সে যুগে বাংলায় নববর্ষের ধারণা ছিল অন্য রকম। অতীতে হিম (শীত) ঋতু থেকে বর্ষ গণনা আরম্ভ হতো। মানুষরা আশা করতেন, আমরা যেন শত শরৎ জীবিত থাকি। এই ‘শরৎ’ শব্দের দ্বারা তৎকালীন সময়ে বছরকেই বোঝানো হতো। আর তিথি-নক্ষত্র দেখে বর্ষা আর শরৎকালের সন্ধিক্ষণকেই বলা হতো নববর্ষ প্রবেশের উৎসব। অষ্টমী পুজো শেষে নবমী শুরুর সন্ধিক্ষণ ছিল পুরনো বছর শেষ, নতুন বছরের শুরু। তখন ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে নতুন বছরকে বরণ করা হতো।
আরও পড়ুন:

রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে…

বিশ্বসেরাদের প্রথম গোল, পর্ব-১২: স্ট্যানলি ম্যাথুজ— একজন কিংবদন্তি, লড়াই আবেগ আর মেহনতী জনতার বন্ধু

চেনা দেশ অচেনা পথ, পর্ব-১৫: সারদা দাদার থেকে চিল্পিঘাটি
তখন চৈত্র মাসের শেষে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে হত গাজন, চড়ক প্রভৃতি অনুষ্ঠান। এটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা প্রধানত নিম্নবর্গের মানুষরা পালন করতেন। অন্য দিকে, ফসল তোলা শেষ হওয়ার পর যে উৎসব পালন করা হতো, তার সঙ্গে জড়িত ছিল মানুষের অর্থনৈতিক জীবন। এক দিকে যেমন রাজাদের কাছে রাজস্ব জমা দেওয়া হতো, সেই সঙ্গে বাকি রাজস্বেও ছাড় মিলত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনও কারণে রাজস্ব দিতে না পারলে তাও মকুব করা হত। জমিদাররা এই সময় প্রজাদের ঋণ দিতেন। জমিদারের কাছারিতে রায়তদেরকে জমিদার বা নায়েবরা পান বা পানপাতা উপহার দিতেন। এই দিনটি ছিল সামাজিক আদানপ্রদানের দিন। স্বাভাবিক ভাবেই ধীরে ধীরে সেই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে ওঠে। ক্রমে তা গোটা সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে যা ছিল শুধু কৃষি উৎসব বা রাজস্ব আদায়ের বিষয়, এক সময় তা হয়ে উঠল নতুন সংস্কার, নতুন সংস্কৃতি, নতুন চিন্তাধারা, তার সঙ্গে নব জীবনের আহ্বান। যা কিছু অসুন্দর, জীর্ণ, পুরাতন, তা শেষ হয়ে যাক এই দিনটিতে। পয়লা বৈশাখ যেন সেই শুভ সূচনার দিন।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম থেকেই নববর্ষের উৎসব কোনও ধর্মের বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এই উৎসবে বাংলার মানুষ— সে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ – খ্রিস্টান সবাই মহানন্দে যোগ দিতেন। একে অন্যের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা, বিনিময়, খাওয়াদাওয়া, আনন্দ উৎসব মিলে সারা বছরের অন্য দিনগুলির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে উঠত এই দিনটি।
প্রতিটি উৎসবই স্বতন্ত্র। তাই তা পালনের একটা নিজস্ব প্রথাও আছে। হয়তো দিনকালের নিরিখে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। চৈত্র সংক্রান্তি ও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে পালন করা হয় ‘আর্তব উৎসব’। বাংলা-ইংরাজি মিলিয়ে এ ভাবে এক একটা বছর আসে, আবার কালের নিয়মে চলেও যায়। আমরা আবার মনে মনে প্রার্থনা করি মনের গোপনে গূঢ় চাওয়া পাওয়াগুলিকে যেন এই নতুন বছরে পেতে পারি। নববর্ষের প্রাক্কালে আমরা সবাই তাই ঐকান্তিক ভাবে লুকিয়ে রাখতে চাই আমাদের অপ্রিয় দুঃখগুলিকে।
এই সময় তাপপ্রবাহের পারদ ঊর্ধ্বমুখী। রাস্তায় জ্বালা ধরানো রোদ। তবু যেন এই নিরন্তর চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা, আশা-নিরাশার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা খুঁজে নিই আমাদের সুখ- স্বপ্নগুলিকে। একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনের থেকে ভালো থাকতে চাই এই দিনটিতে। বৈশাখ এলেই তাই রবীন্দ্রনাথের গান আনমনে আমরা গাইতে থাকি—‘মুছে যাক গ্লানি মুছে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম থেকেই নববর্ষের উৎসব কোনও ধর্মের বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এই উৎসবে বাংলার মানুষ— সে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ – খ্রিস্টান সবাই মহানন্দে যোগ দিতেন। একে অন্যের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা, বিনিময়, খাওয়াদাওয়া, আনন্দ উৎসব মিলে সারা বছরের অন্য দিনগুলির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে উঠত এই দিনটি।
প্রতিটি উৎসবই স্বতন্ত্র। তাই তা পালনের একটা নিজস্ব প্রথাও আছে। হয়তো দিনকালের নিরিখে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। চৈত্র সংক্রান্তি ও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে পালন করা হয় ‘আর্তব উৎসব’। বাংলা-ইংরাজি মিলিয়ে এ ভাবে এক একটা বছর আসে, আবার কালের নিয়মে চলেও যায়। আমরা আবার মনে মনে প্রার্থনা করি মনের গোপনে গূঢ় চাওয়া পাওয়াগুলিকে যেন এই নতুন বছরে পেতে পারি। নববর্ষের প্রাক্কালে আমরা সবাই তাই ঐকান্তিক ভাবে লুকিয়ে রাখতে চাই আমাদের অপ্রিয় দুঃখগুলিকে।
এই সময় তাপপ্রবাহের পারদ ঊর্ধ্বমুখী। রাস্তায় জ্বালা ধরানো রোদ। তবু যেন এই নিরন্তর চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা, আশা-নিরাশার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা খুঁজে নিই আমাদের সুখ- স্বপ্নগুলিকে। একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনের থেকে ভালো থাকতে চাই এই দিনটিতে। বৈশাখ এলেই তাই রবীন্দ্রনাথের গান আনমনে আমরা গাইতে থাকি—‘মুছে যাক গ্লানি মুছে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’
আরও পড়ুন:

দশভুজা: ‘পুরুষ মানুষের কাজে হাত দিলে এমনই হবে, মহিলাদের এসব সাজে না’

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৫৮: রবীন্দ্রনাথ সাঁতার কাটতেন, সাঁতার শেখাতেন
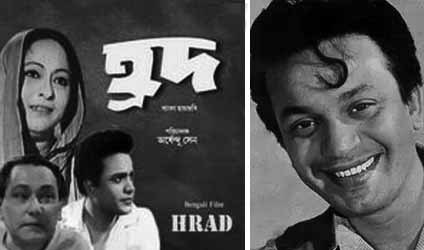
উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৩১: মরুভূমির উপল পারে বনতলের ‘হ্রদ’
সেই যে কবি বৈশাখের আবাহনে উচ্চারণ করেছিলেন— ‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো’ গ্রীষ্মের দাবদাহ নিয়ে বৈশাখের আগমন মানেই ‘জীর্ণ পুরাতন’ গোটা পুরনো সুখদুঃখে মোড়া একটা বছর শেষ করে আর একটি বছরে প্রবেশ করতে চলেছি আমরা। বাঙালির কাছে বৈশাখের অর্থই নতুনকে বরণ করে নেওয়ার এক মাস।
ব্যবসায়ী ও দোকানিরা ব্যস্ত থাকেন নতুন খাতা খুলতে। ভোর হতেই স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে শুদ্ধ চিত্তে লক্ষ্মী ও গণেশের পূজার্চনা করেন তাঁরা। তাছাড়া অন্য আরাধ্যা দেবদেবীদেরও পূজার্চনা চলে সেই সঙ্গে। অনেকে কাছে-দূরের কোনও জাগ্রত মন্দিরে যান পুজোর ডালা নিয়ে। সঙ্গে করে তাঁরা নিয়ে যান লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি, হলুদ ও সিঁদুর মাখা মুদ্রা বা ষোলো আনা। সেটিকে দেবীর অঙ্গে স্পর্শ ও পুজো করিয়ে লাল শালুতে বাঁধানো হিসাবের খাতায় দেবীর স্পর্শমাখা সিঁদুর লেপা মুদ্রার প্রণামী ছাপ দেওয়া হয় নতুন হালখাতার প্রথম পৃষ্ঠায়। ‘ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ’ কিংবা ‘শুভলাভ’ ও স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা এই হিসেবের খাতাটাই নতুন বছরের আয় ও সমৃদ্ধির প্রতিনিধি। ফুল, আলো, কলাগাছ, আম্রপল্লব দেওয়া মঙ্গলঘট দিয়ে সাজানো দোকানগুলোয় পরিচিত ও বাঁধা খদ্দেরদের জন্য করা হয় মিষ্টিমুখের আয়োজন। সঙ্গে ঠান্ডা পানীয় ও ছোটখাটো উপহার। অনেক ব্যবসায়ী আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিনও এই অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকেন। আসলে এই রেওয়াজটি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এক সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেয়। উৎসব মানেই কোনও একটা বিষয় উপলক্ষ করে সবার সঙ্গে প্রাণের মিলন। ঘটা করে নববর্ষের দিন হালখাতা পালনও একটা উৎসব বিশেষ। দীনেন্দ্রকুমার রায়-এর ‘পল্লীচিত্র’ গ্রন্থে ধরা পড়েছে বৈশাখী মেলার বিচিত্র এক রূপ— ‘দোকান পশারীও কম আসে নাই…।’
তবে এখন উৎসবের ধরনেও এসেছে বিপুল পরিবর্তন। তবু নববর্ষ তথা নতুন বছরের সূচনায় হালখাতা আর গোলাপি নতুন বাংলা পঞ্জিকার গন্ধ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় বইকী! পুজোপার্বণের অন্যতম পয়লা বৈশাখ বাঙালির কাছে অন্য তাৎপর্য বহন করে আনে।
আগে সাবেক বাঙালি ঘরে নববর্ষের দিন দুধ উথলাবার একটি প্রাচীন প্রথা ছিল। গ্রামবাংলায় সাধারণত গোয়ালঘরেই এই পুজো করার রীতি ছিল। গোয়ালঘর পরিষ্কার করে সেখানে ছোট উনুন বানিয়ে মাটির মালসায় দুধ, মুঠোখানেক আতপ চাল ও গুড়-বাতাসা দিয়ে, পাটকাঠির জ্বালানি দিয়ে দুধ ফুটিয়ে পায়েস বানানো হতো। সেই পায়েসের কিছুটা উনুনের মাটিতে রেখে, বাকি পায়েস পরিবারের সবাইকে দিয়ে দেওয়া হতো। একেই বলা হতো নববর্ষের দিন ‘দুধ উথলানো ব্রত’। আবার এই সময় গ্রামবাংলায় কোনও প্রাচীন বটগাছের নীচে জলসত্র খোলা হতো তৃষ্ণার্ত পথযাত্রীর জন্য। কোথাও কোথাও সন্ধেবেলায় সেখানে রামায়ণ পাঠও হতে দেখা যেত।
ব্যবসায়ী ও দোকানিরা ব্যস্ত থাকেন নতুন খাতা খুলতে। ভোর হতেই স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে শুদ্ধ চিত্তে লক্ষ্মী ও গণেশের পূজার্চনা করেন তাঁরা। তাছাড়া অন্য আরাধ্যা দেবদেবীদেরও পূজার্চনা চলে সেই সঙ্গে। অনেকে কাছে-দূরের কোনও জাগ্রত মন্দিরে যান পুজোর ডালা নিয়ে। সঙ্গে করে তাঁরা নিয়ে যান লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি, হলুদ ও সিঁদুর মাখা মুদ্রা বা ষোলো আনা। সেটিকে দেবীর অঙ্গে স্পর্শ ও পুজো করিয়ে লাল শালুতে বাঁধানো হিসাবের খাতায় দেবীর স্পর্শমাখা সিঁদুর লেপা মুদ্রার প্রণামী ছাপ দেওয়া হয় নতুন হালখাতার প্রথম পৃষ্ঠায়। ‘ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ’ কিংবা ‘শুভলাভ’ ও স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা এই হিসেবের খাতাটাই নতুন বছরের আয় ও সমৃদ্ধির প্রতিনিধি। ফুল, আলো, কলাগাছ, আম্রপল্লব দেওয়া মঙ্গলঘট দিয়ে সাজানো দোকানগুলোয় পরিচিত ও বাঁধা খদ্দেরদের জন্য করা হয় মিষ্টিমুখের আয়োজন। সঙ্গে ঠান্ডা পানীয় ও ছোটখাটো উপহার। অনেক ব্যবসায়ী আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিনও এই অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকেন। আসলে এই রেওয়াজটি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এক সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেয়। উৎসব মানেই কোনও একটা বিষয় উপলক্ষ করে সবার সঙ্গে প্রাণের মিলন। ঘটা করে নববর্ষের দিন হালখাতা পালনও একটা উৎসব বিশেষ। দীনেন্দ্রকুমার রায়-এর ‘পল্লীচিত্র’ গ্রন্থে ধরা পড়েছে বৈশাখী মেলার বিচিত্র এক রূপ— ‘দোকান পশারীও কম আসে নাই…।’
তবে এখন উৎসবের ধরনেও এসেছে বিপুল পরিবর্তন। তবু নববর্ষ তথা নতুন বছরের সূচনায় হালখাতা আর গোলাপি নতুন বাংলা পঞ্জিকার গন্ধ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় বইকী! পুজোপার্বণের অন্যতম পয়লা বৈশাখ বাঙালির কাছে অন্য তাৎপর্য বহন করে আনে।
আগে সাবেক বাঙালি ঘরে নববর্ষের দিন দুধ উথলাবার একটি প্রাচীন প্রথা ছিল। গ্রামবাংলায় সাধারণত গোয়ালঘরেই এই পুজো করার রীতি ছিল। গোয়ালঘর পরিষ্কার করে সেখানে ছোট উনুন বানিয়ে মাটির মালসায় দুধ, মুঠোখানেক আতপ চাল ও গুড়-বাতাসা দিয়ে, পাটকাঠির জ্বালানি দিয়ে দুধ ফুটিয়ে পায়েস বানানো হতো। সেই পায়েসের কিছুটা উনুনের মাটিতে রেখে, বাকি পায়েস পরিবারের সবাইকে দিয়ে দেওয়া হতো। একেই বলা হতো নববর্ষের দিন ‘দুধ উথলানো ব্রত’। আবার এই সময় গ্রামবাংলায় কোনও প্রাচীন বটগাছের নীচে জলসত্র খোলা হতো তৃষ্ণার্ত পথযাত্রীর জন্য। কোথাও কোথাও সন্ধেবেলায় সেখানে রামায়ণ পাঠও হতে দেখা যেত।
আরও পড়ুন:
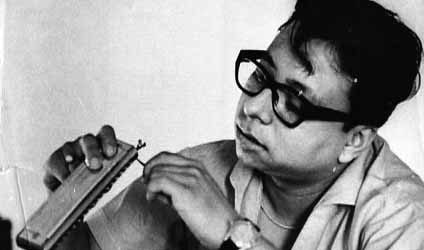
পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-৬: পঞ্চম-সভার তিন রত্ন বাসু-মনোহারী-মারুতি

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-১৫: শরীর ফিট রাখতে রোজ ভিটামিন টনিক খাচ্ছেন?
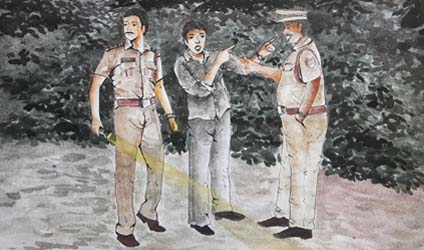
রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১০: তত্ত্বতালাশ
এখনও শহরের রাস্তায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরার সময়ে জলসত্র দেখা যায়। অনেক মন্দিরেও দেখা যায় মাটির কলসির নীচে ফুটো করে বিগ্রহের শরীরে টুপটাপ করে জল ছিটোনোর প্রথা।
বাঙালির নববর্ষ পালনের সূচনা হয় যশস্বী কবি ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাত ধরে। তিনি এমনই এক নববর্ষের দিন অতিথি আপ্যায়ন করে বিশাল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেন। শহর কলকাতার তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন সেই মজলিশি বৈঠকে। শোনা যায়, ঋষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তারপর থেকেই বিশ শতকের গোড়ায় নিয়ম করে নববর্ষের দিন নাচগানের মজলিশ বসত বলে শোনা যায়। নকশাদার জাজিমে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাবুদের সে আসরে থাকত আতর-সুরা-সারেঙ্গি-তবলা-হারমোনিয়াম-বাঈজির নাচগান। এমনকি, বেতার ও টিভির নামী শিল্পীদের বায়না করে নিয়ে আসা হতো।
পয়লা বৈশাখকে যিনি বাঙালির অন্তরের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। যা ছিল বাণিজ্যিক, তা চিরকালের জন্যে নতুন বার্তা নিয়ে এল আমাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটকে বার বার এসেছে নতুন বছরের স্বাগতবাণী। এ যেন পুরনো জীর্ণ জীবনের অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশের আনন্দ অনুভূতি।
সব ধর্মের মানুষ বিভেদ ভুলে এই উৎসবের দিনে একই সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, শামসুর রহমানরা এই দিনটিকে কেন্দ্র করে মিলনের গান গেয়েছেন, অশুভকে দূর করে নিয়ে এসেছেন শুভর বার্তা। রাত্রিশেষে প্রভাত সূর্যের দিকে চেয়ে যেন আমরা সমস্বরে বলতে চাই, “রাত্রির অন্ধকার কেটে যাক/ জয় হোক সর্বমানবের।”
বছরের এই প্রথম দিনটিতে প্রতিটি বাঙালির বাড়িতে অন্য রকম রান্না-বান্না, খাওয়াদাওয়া আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেমন শুক্তো, কুচো চিংড়ি দিয়ে মোচার ঘণ্ট, নারকেল দিয়ে সোনামুগ ডাল, ধোঁকার ডালনা, দই-মাছ, পাঁঠার মাংস, কাঁচা আমের চাটনি, মিষ্টি দই, পান ইত্যাদি।
পয়লা বৈশাখ বাংলা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বসবাসকারী বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষও উদযাপন করে থাকেন।
বাঙালির নববর্ষ পালনের সূচনা হয় যশস্বী কবি ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাত ধরে। তিনি এমনই এক নববর্ষের দিন অতিথি আপ্যায়ন করে বিশাল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেন। শহর কলকাতার তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন সেই মজলিশি বৈঠকে। শোনা যায়, ঋষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তারপর থেকেই বিশ শতকের গোড়ায় নিয়ম করে নববর্ষের দিন নাচগানের মজলিশ বসত বলে শোনা যায়। নকশাদার জাজিমে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাবুদের সে আসরে থাকত আতর-সুরা-সারেঙ্গি-তবলা-হারমোনিয়াম-বাঈজির নাচগান। এমনকি, বেতার ও টিভির নামী শিল্পীদের বায়না করে নিয়ে আসা হতো।
পয়লা বৈশাখকে যিনি বাঙালির অন্তরের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। যা ছিল বাণিজ্যিক, তা চিরকালের জন্যে নতুন বার্তা নিয়ে এল আমাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটকে বার বার এসেছে নতুন বছরের স্বাগতবাণী। এ যেন পুরনো জীর্ণ জীবনের অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশের আনন্দ অনুভূতি।
সব ধর্মের মানুষ বিভেদ ভুলে এই উৎসবের দিনে একই সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, শামসুর রহমানরা এই দিনটিকে কেন্দ্র করে মিলনের গান গেয়েছেন, অশুভকে দূর করে নিয়ে এসেছেন শুভর বার্তা। রাত্রিশেষে প্রভাত সূর্যের দিকে চেয়ে যেন আমরা সমস্বরে বলতে চাই, “রাত্রির অন্ধকার কেটে যাক/ জয় হোক সর্বমানবের।”
বছরের এই প্রথম দিনটিতে প্রতিটি বাঙালির বাড়িতে অন্য রকম রান্না-বান্না, খাওয়াদাওয়া আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেমন শুক্তো, কুচো চিংড়ি দিয়ে মোচার ঘণ্ট, নারকেল দিয়ে সোনামুগ ডাল, ধোঁকার ডালনা, দই-মাছ, পাঁঠার মাংস, কাঁচা আমের চাটনি, মিষ্টি দই, পান ইত্যাদি।
পয়লা বৈশাখ বাংলা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বসবাসকারী বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষও উদযাপন করে থাকেন।
* অজানার সন্ধানে (Unknown story): সঞ্চিতা কুণ্ডু (Sanchita Kundu) সংস্কৃতের অধ্যাপিকা, হুগলি মহসিন কলেজ।


















