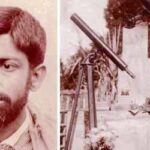বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী সাধন বসু।
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী সাধন বসু ছিলেন কোয়ান্টাম রসায়ন ও আলোক রসায়নের এক দিকপাল পণ্ডিত। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে পিতা জ্যোতিষচন্দ্র বসু ও মাতা সরযূবালা দেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এই বিশিষ্ট মানুষটি। ব্রিটিশ আমলে কলকাতার এক বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বসু পরিবার তাঁর জন্ম হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে তিনি পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচারাল রেজিনস অ্যান্ড গামস’ থেকে শেলাকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেন।
তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার বসু, যিনি ছিলেন তখনকার দিনে এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এরপর উচ্চতর গবেষণার জন্য তিনি বিদেশ যান এবং নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রবার্ট এস মুলিকেনের কাছে গবেষণা করেন। তিনি ড. মুলিকেনের কাছে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেলের উপর কাজ করেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধ ‘ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন অ্যান্ড চেন ট্রানস্ফার ইন মিথাইল মেথাক্রাইলেট’ হল পলিমার রসায়নের প্রথম ভারতীয় নিবন্ধ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে এবং এতে তাঁর সহকারী লেখকরা ছিলেন জ্যো তিন্দ্রনাথ সেন এবং আরএস পালিত।
তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার বসু, যিনি ছিলেন তখনকার দিনে এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এরপর উচ্চতর গবেষণার জন্য তিনি বিদেশ যান এবং নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রবার্ট এস মুলিকেনের কাছে গবেষণা করেন। তিনি ড. মুলিকেনের কাছে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেলের উপর কাজ করেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধ ‘ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন অ্যান্ড চেন ট্রানস্ফার ইন মিথাইল মেথাক্রাইলেট’ হল পলিমার রসায়নের প্রথম ভারতীয় নিবন্ধ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে এবং এতে তাঁর সহকারী লেখকরা ছিলেন জ্যো তিন্দ্রনাথ সেন এবং আরএস পালিত।
ড. বসু চার্জ স্থানান্তর মিথস্ক্রিয়া, লিগ্যান্ড ফিল্ড স্পেকট্রা, হাইড্রোজেন বন্ধন, কোয়ান্টাম রসায়ন এবং আলোক রসায়নের ন্যা য় বিস্তৃত ক্ষেত্রে বহুধা কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি পলিমার রসায়ন এবং ফ্রি রেডিক্যাল পলিমারাইজেশনে স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন। নাইলনে-এনএইচ২ গ্রুপ নির্ধারণের জন্য তিনি তখনকার দিনে যে পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেছেন, তা এখনও পর্যন্ত আদর্শ পদ্ধতি হিসাবেই গণ্য করা হয়। তিনি চার্জ স্থানান্তর ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারণের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে আণবিক অরবিটালের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সমাধানগুলিতে চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ডগুলিতে কম্পনমূলক কাঠামোর অস্তিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এক্সাইমার ও এক্সিপ্লেক্স নির্গমন নিয়ে বসুর কাজ দারুণ সাড়া ফেলেছিল। সুগন্ধি পলিহাইড্রোকার্বনের রূপান্তরশক্তি এবং অসিলেটর শক্তি গণনা করার জন্য শিনিচিরো টোমোনাগা গ্যাস মডেলের ব্যবহারে তাঁর গবেষণার বৈচিত্র প্রতিফলিত হয়।
আরও পড়ুন:

বিপন্ন বাংলার রাজ্যপশু বাঘরোল

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬১: ‘বন্ধু’ তোমার পথের সাথী
১৯৪৮ সালে ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স’ এর ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে রেডিক্যাল পলিমারাইজেশন চেন ট্রান্সফারের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় লিপ্ত হন এবং পলিমারের আণবিক ওজন অনুমান করার জন্য একটি আদর্শ পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৫১-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, ব্লুমিংটনে রসায়নের ‘পোষ্ট ডক্টরাল ফুলব্রাইট’ ফেলো ছিলেন। এখানেই তিনি কোয়ান্টাম রসায়নের উপর আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং দীর্ঘ তিন দশক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ভারতে পলিমার রসায়ন গবেষণার পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি ইলেকট্রন আণবিক কক্ষপথ গণনার উপর অনেক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।
পরবর্তীকালে, ১৯৬১-১৯৬২ সাল পর্যন্ত ওই ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। পরে ১৯৬২-৬২ সালে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি গ্রুপের ভিজিটিং প্রফেসর নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন শেষে, ১৯৬৪ সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ বা ‘ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি’তে রসায়নের পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর অবসরকাল পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন এবং এই পদের সুনাম বৃদ্ধি করেছিলেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন।
পরবর্তীকালে, ১৯৬১-১৯৬২ সাল পর্যন্ত ওই ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। পরে ১৯৬২-৬২ সালে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি গ্রুপের ভিজিটিং প্রফেসর নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন শেষে, ১৯৬৪ সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ বা ‘ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি’তে রসায়নের পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর অবসরকাল পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন এবং এই পদের সুনাম বৃদ্ধি করেছিলেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন।
আরও পড়ুন:

দশভুজা, সরস্বতীর লীলাকমল, পর্ব-১১: স্বর্ণকুমারী দেবী— ঠাকুরবাড়ির সরস্বতী

এই দেশ এই মাটি, পর্ব-৩৫: সুন্দরবনের নদীবাঁধের অতীত
১৯৮১ সালে ড. বসু ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স’-এর পরিচালক নিযুক্ত হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরের বছরই ওই পদ ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ‘জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমি কাউন্সিল’-এর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। স্বল্প রোগভোগের পর ১৯৯২ সালে মাত্র ৭০ বছর বয়সে এই নবতিপর মানুষটি পরলোক গমন করেন। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সন্তান সন্ততির মধ্যে দিয়ে। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানগুলি চিরকাল মানুষের শিক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে।
ড. বসু সারা জীবন কাজের জন্য অসংখ্য সম্মান এবং পুরস্কার পেয়েছেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাক্যাডেমি বা ইনশা, ১৯৬২ সালে বসুকে ফেলো হিসাবে নির্বাচিত করেন। ১৯৬২ সালে ‘বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল‘ বা ‘সিএসআইআর’ তাঁর সারা জীবন কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার প্রদান করে, যা ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বোচ্চ পুরস্কার বলে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইউজিসির জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন।
ড. বসু সারা জীবন কাজের জন্য অসংখ্য সম্মান এবং পুরস্কার পেয়েছেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাক্যাডেমি বা ইনশা, ১৯৬২ সালে বসুকে ফেলো হিসাবে নির্বাচিত করেন। ১৯৬২ সালে ‘বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল‘ বা ‘সিএসআইআর’ তাঁর সারা জীবন কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার প্রদান করে, যা ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বোচ্চ পুরস্কার বলে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইউজিসির জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন।
আরও পড়ুন:

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৭৯: কবির ভালোবাসার পশুপাখি

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৩৩: সারদা মায়ের দার্শনিক দৃষ্টি
১৯৭৫ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স তাঁকে পুনরায় ফেলো নির্বাচিত করেন এবং ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে আচার্য জেসি ঘোষ স্বর্ণপদক প্রদান করে। ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে তাঁকে সিভি রমন জন্মশতবার্ষিকী স্মৃতি পদক প্রদান করা হয়। তিনি রয়্যাাল ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ‘ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি’ ও ফ্রান্সের ‘সোসাইটি অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি’র নির্বাচিত ফেলোও হয়েছিলেন।
‘ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স’ ১৯৮৬ সালে তাঁর ৬৫তম জন্মবার্ষিকীতে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি ‘ফেস্টস্কিফ্ট’ তৈরি করেছিল। ‘ইনশা’ অধ্যাপক সাধন বসু স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর গবেষণার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি বার্ষিক পুরস্কার ‘অধ্যাপক সাধন বসু মেমোরিয়াল আওয়ার্ড’ দিয়ে থাকে। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ২০১৩ সালে ভারতের প্রথম শ্রেণির বৈজ্ঞানিক জার্নাল ‘রেজন্যান্স’-এ ড. বসুর ওপর একটি জীবনী প্রকাশ করে। এইভাবে দেশ ও বিদেশের শিক্ষামহল ড. বসুর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ড. বসুর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
‘ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স’ ১৯৮৬ সালে তাঁর ৬৫তম জন্মবার্ষিকীতে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি ‘ফেস্টস্কিফ্ট’ তৈরি করেছিল। ‘ইনশা’ অধ্যাপক সাধন বসু স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর গবেষণার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি বার্ষিক পুরস্কার ‘অধ্যাপক সাধন বসু মেমোরিয়াল আওয়ার্ড’ দিয়ে থাকে। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ২০১৩ সালে ভারতের প্রথম শ্রেণির বৈজ্ঞানিক জার্নাল ‘রেজন্যান্স’-এ ড. বসুর ওপর একটি জীবনী প্রকাশ করে। এইভাবে দেশ ও বিদেশের শিক্ষামহল ড. বসুর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ড. বসুর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
* ড. উৎপল অধিকারী, সহ-শিক্ষক, আঝাপুর হাই স্কুল, আঝাপুর, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান।