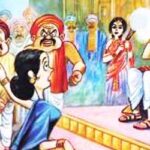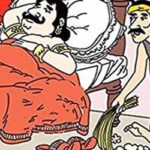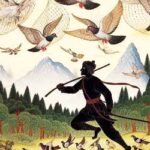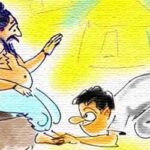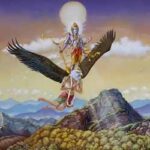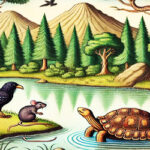ছবি: প্রতীকী। সংগৃহীত।
মিত্রভেদ
বোধিসত্ত্ব তখন ভাবলেন, পরে রওনা হওয়াই বরং ভালো। কারণ সেই তরুণ বণিকটি যখন তার পাঁচশো বলদের গাড়ি নিয়ে যাবে তখন সেই মালবাহী গাড়িগুলোর চাপে প্রথমত: অসমান পথ সমান হবে, আর দ্বিতীয়ত: তাদের গাড়ির বলদগুলো সব পাকা ঘাস খেয়ে নেওয়ার পর সেইসব ঘাসের গোড়া থেকে আবার যে কচি নরম ঘাস বেরোবে, বোধিসত্ত্বের বলদগুলো সে সব খেতে পারবে; মানে যাত্রাপথে গবাদি পশুদের জন্য একেবারে পুষ্টিগুণযুক্ত তাজা খাবার পাওয়া যাবে। এতে বলদদের শরীর-স্বাস্থ্যও অটুট থাকবে; আর শুধু গবাদি পশুই বা কেন? তাদের নিজেদের জন্যেও নতুন আর টাটকা ফলমূল মিলবে কিছুদিন পরে ওই রাস্তায় গেলেই। উপরন্তু পথে যে সব জায়গায় জলের অভাব, সেখানে এদের দলটি আগে যাওয়ায় কারণে নিজেদের জন্য তারা যে সমস্ত কূপ খুঁড়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে, পরে যখন সার্থবাহদের দল নিয়ে বোধিসত্ত্ব স্বয়ং যাবেন সে পথে তাঁরা তখন সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন স্বচ্ছন্দে। উপরন্তু নতুন জায়গায় পণ্যের দাম নির্ধারণের জন্য লোকের সঙ্গে দরদস্তুরও করতে হবে না বিশেষ। কারণ আগের বণিকটি যে দ্রব্যের যে দাম স্থির করে যাবে। বোধিসত্ত্বদের দল গিয়েও সেই দামেই জিনিস বিক্রি করতে পারবে। আর সবচেয়ে বড় কথাটা হল, সেই বণিকের দলটি আগে যাওয়ার কারণে, আগে থেকেই মার্কেটিং করে পণ্যদ্রব্যের চাহিদাটা বাজারে তৈরি করে রাখবে, ফলে বোধিসত্ত্বের দলের সার্থবাহদের ক্রয়-বিক্রয় নির্ঝঞ্ঝাটে হতে পারবে।
‘অপণ্ণক-জাতক’-এর এই গল্পটা পঞ্চতন্ত্র প্রসঙ্গে এই পর্যন্ত জানাটাই যথেষ্ট। কারণ, ‘পঞ্চতন্ত্র’ নিয়ে কথা বলতে বসে জাতকের গল্প নিয়ে বেশি কথা বললে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা আছে। সেই সঙ্গে আবার অন্য প্রসঙ্গে বেশি ঢুকে গেলে খেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। তাই জাতকের প্রসঙ্গটা এখানেই থামিয়ে দেওয়াটা শ্রেয়। উত্সাহী পাঠক-পাঠিকাদের বলবো যে গল্পের বাকি অংশটুকুর জন্য আপনারা ঈশাণচন্দ্র ঘোষের ‘জাতক’ কাহিনির প্রথম খণ্ডটি দেখতে নিতে পারেন; ‘অপণ্ণক-জাতক’-এর পুরো গল্পটা আপনি সেখানেই পেয়ে যাবেন। মোট ছয় খণ্ডে প্রকাশিত পালিভাষায় রচিত মূল ‘জাতকাত্থবণ্ণনা (সং – জাতকার্থবর্ণনা)’ গ্রন্থের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য বাংলা সংস্করণ এইটিই। তাই ভবিষ্যতেও ‘পঞ্চতন্ত্র’ প্রসঙ্গে কোনও জাতকের কাহিনির সূত্র টানতে গেলে ঈশাণচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ করা ‘জাতকাত্থবণ্ণনা’ গ্রন্থেরই সহায়তা নিতে হবে আমাদের। এই গল্পটিকে এখানে টেনে আনবার উদ্দেশ্য একটাই। আসলে সার্থবাহদের দল যখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে পণ্য দিয়ে যেতেন, তখন তাঁদের যে কতোদিক বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হতো, সেইটা বোঝাবার জন্যেই এই গল্পটির কথা মনে হয়েছিল।
প্রাচীন কালে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ ধরে বণিকরা যখন দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন, তখন সেই পথের দুর্গমতা অনুসারেই সে পথকে নির্দিষ্ট কতগুলি ‘কান্তার’-এ ভাগ করতেন তাঁরা। এমনকি তাঁদের যাত্রাপথে ঠিক কোন কোন ‘কান্তার’ অতিক্রম করতে হবে, সেই অনুসারে আগে থেকেই লোকবল এবং প্রতীকারের ব্যবস্থা নিয়েই রওনা হতেন তাঁরা দূর দেশের বাণিজ্যে। বৌদ্ধজাতকগুলো খুঁজলে আপনি পাঁচ রকম কান্তারের খবর পাবেন।

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৫: অল্প ক্ষতি স্বীকার করে হলেও ভবিষ্যতে বড় লাভের কথা চিন্তা করা দরকার

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১১: কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং কয়েকটি প্রশ্ন
আপনারা ল্যুই ক্যারোলের ‘অ্যালিস ইন ওয়ান্ডাল্যান্ড’-এর খবর জানেন। সেখানে অ্যালিস মেয়েটি যেমন বাস্তবের জগৎ থেকে রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করে এখানেও তাই। বর্ধমান বণিকের সঞ্জীবক নামের সেই বৃষটি যমুনাতীরের কচি কচি ঘাস খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হয়ে মহাদেবের ষাঁড়ের মতো বলশালী ও বৃহদাকৃতি হয়ে বনে বনে ঘুরতে থাকে আর আবিষ্কার করে মনুষ্য জগতের মতন জঙ্গলে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও আছে এক সমান্তরাল সমাজ। সেখানেও আছে বনের রাজা, মন্ত্রী সবকিছুই মনুষ্য জগতের মতনই। রাজনীতি-কূটনীতির খেলা সেখানেও সমানতালেই চলে। সঞ্জীবকের গল্পের আড়ালে রাজপুত্রদের সঙ্গে আমাদের নিয়েও পঞ্চতন্ত্রকার প্রবেশ করলেন সেই কল্পনায় মোড়া পশুরাজের রাজ্যে।

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১৫: আর্য কোথায়?
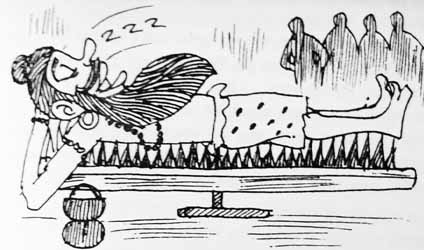
এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-২০: শোওয়ার বালিশ বিছানা কেমন হবে? শক্ত না নরম?
অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি বনে বিসর্জিতঃ কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে বিনশ্যতি।। (মিত্রভেদ ২০)
যে বস্তুকে রক্ষা করবার কেউ নেই, সেই অরক্ষিত বস্তুও যদি দৈব সহায়তা থাকে, মানে কপালে থাকে, তবে দেখবেন ঠিক সুরক্ষিত থাকে; আর কপালে না থাকলে সুরক্ষিত বস্তুও নষ্ট হয়ে যায়। উহারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দৈব সহায় হলে বনে ছেড়ে যাওয়া অনাথ শিশুও দিব্যি বেঁচে বর্তে থাকে, আবার কপালে না থাকলে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঘরে মধ্যে সুরক্ষিত রাখলেও তা বিনষ্ট হতে পারে। তাই জীবনের কথা কেউ বলতে পারে না যে কার কপালে কী আছে।
আমাদের শুধু জীবনের পতনোভ্যূত্থানের বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হয় বৃহৎ জীবনের দিকে। এই শ্লোকটা কোথাও হয়তো সেই বস্তুবাদী রাজপুত্রদের কাছে এই বার্তাকেই পৌঁছে দিতে চায় যে জীবনের দৈবদুর্বিপাককে যাতে তারা সহজে নিতে পারে। কারণ পুরুষকার থাকলেও দৈবকে আমরা কোন সময়েই উপেক্ষা করতে পারি না আর সবটা হয়তো আমাদের হাতেও থাকে না। তাই আনন্দ কিংবা শোক—সবেতেই যেন আমরা মোহহীন হয়ে অবস্থান করতে পারি। আনন্দে বা দুঃখে নিজের কর্ম থেকে যেন বঞ্চিত না হই—এইটাই সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের মূল কথা আর জীবনের উন্নতির সূত্রও হয়তো এইটাই।

চলো যাই ঘুরে আসি: চুপি চুপি ঘুরে আসি

দশভুজা: দু’শো বছর আগে হলে তিনি ইঞ্জিনিয়ারের বদলে সতী হতেন
কিন্তু সমস্যা হল, রাজার তো আর ভয় পেলে চলে না কিংবা রাজা যে ভয় পেয়েছে সেটাও আশেপাশের লোকজনকে বুঝতে দেওয়া যায় না। তাই জল না খেয়ে তখন নিজেকে ভয়হীন দেখিয়ে চতুর্মণ্ডলে অবস্থান করল। এই ‘চতুর্মণ্ডলাবস্থান’ অর্থশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। অর্থশাস্ত্র বলে, রাজা নিজের আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করে সবসময় এইরকম চতুর্মণ্ডলে অবস্থান করবেন। আজকের পরিভাষায় ব্যাপারটা অনেকটা ‘জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা’ –এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কোনও নেতা বা ভিআইপি-দের সর্বোচ্চ সুরক্ষার জন্য ভারতে এই ‘জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা’ দেওয়া হয়, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যায় আগ্নেয় অস্ত্রধারী পুরুষ, বুলেট প্রুফ গাড়ি কিংবা ‘সার্ভিলেন্স সিস্টেম’-এর ব্যবস্থা থাকে। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই ‘চতুর্মণ্ডলাবস্থান’ ব্যাপারটা আরেকটু বিস্তৃত।
একটু চিন্তা করে দেখবেন, এই চতুর্মণ্ডলের মধ্যে আজকের দিনেও রাজারা কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তেই বসে থাকেন, বাইরের বিপদের আঁচটুকুও তাঁর কাছে সহজে আসতে পারে না। পিঙ্গলক বনের প্রাণী, কোনও গৃহপালিত প্রাণীর সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয়ও হয়নি তাঁর। তাই সঞ্জীবকের এরকম গম্ভীর গর্জন দূর থেকে শুনে বিষয়টা বুঝতে না পেরে ভয়ে চতুর্মণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করলো সে।—চলবে