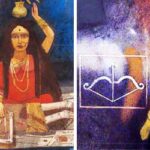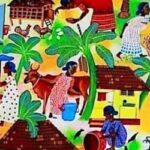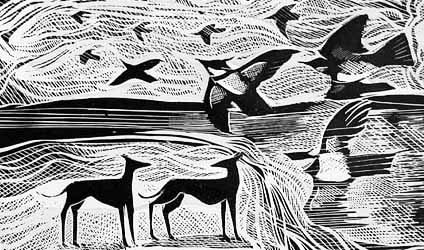
ছবি প্রতীকী। সংগৃহীত।
‘সম্মতি’ বিষয়টি আমাদের মধ্যে দু’ প্রকার অনুভুতি তৈরি করে। প্রথমেই আসে ছোট থেকে বড় বেলায় আসার প্রাক মুহূর্ত অবধি আমাদের কাছে গুরুজনের সরাসরি কিংবা প্রশ্রয় মেশানো সম্মতি পাওয়ার গুরুত্ব। আমাদের মূল্যবোধের আধারে বাধ্য হয়ে থাকা আর বাধ্য থাকলে কী সুবধে পাওয়া যাবে খুব বড় জায়গা নিয়ে থাকে। দ্বিতীয় ভাগে আসে সরকারি হিসেবে আঠারো বছর হওয়ার পর আমরা ‘সম্মতি’র বিষয়টিকে কীভাবে দেখছি। আঠার বছররের পর যৌন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করার সময় থেকে সম্মতির বিষয়টির আমি বলব লিঙ্গ বিভাজন হয়ে যায়। এই বিভাজন অসম এক বিভাজন, আর নারীদের ক্ষেত্রে বা যারা নারী পুরুষ এই দুই বিভাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চান না তাদের যৌন আচরণের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করানোর সম্মতি যেন সমাজ দিয়ে রেখেছে পুরুষদের। ‘সম্মতি’ বিষয়টি বিসমকাম সমাজে একতরফা একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আগের পর্বের লেখাতে আমি বলেছি, সম্মতি বিষয়টি নিয়ে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গর্ভধারণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে করা যাবে না বলে। সমাজ চিন্তিত বংশের বাতি থাকল না কি থাকল না সেই বিষয় নিয়ে। সমাজ অল্প বয়েসে সন্তানের জন্মদিতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পড়ে যাওয়া নারীদের নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। সমাজের এই ভাবনার অবস্থান এখনও কিছুই বদলায়নি বলে জানিয়েছেন আমার চেনা মানুষেরা।
তাঁদের আক্ষেপ, আজও যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে নারীদের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না পুরুষেরা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তাঁরা প্রয়োজন বোধ করছে না? এই বোধের জাগরণ না হওয়ার কারণ কী হতে পারে? আমরা ‘মি টু’ আন্দোলন হতে দেখেছে। মহিলারা সারা পৃথিবীব্যাপী কীভাবে নিজের বাড়িতে অতিনিকট জনের সম্মতিহীন বল পূর্বক যৌন লালসার শিকার হয়েছেন। নিজেদের কাজের জায়গায়, অতি আপনজন স্বামীর মাধ্যমেও বল পূর্বক যৌন লালসার শিকার হয়েছেন। আমি আগের লেখাতে বলেছিলাম কীভাবে নারীরা এই ধরনের অত্যাচারকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়।
আগের পর্বের লেখাতে আমি বলেছি, সম্মতি বিষয়টি নিয়ে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গর্ভধারণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে করা যাবে না বলে। সমাজ চিন্তিত বংশের বাতি থাকল না কি থাকল না সেই বিষয় নিয়ে। সমাজ অল্প বয়েসে সন্তানের জন্মদিতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পড়ে যাওয়া নারীদের নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। সমাজের এই ভাবনার অবস্থান এখনও কিছুই বদলায়নি বলে জানিয়েছেন আমার চেনা মানুষেরা।
তাঁদের আক্ষেপ, আজও যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে নারীদের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না পুরুষেরা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তাঁরা প্রয়োজন বোধ করছে না? এই বোধের জাগরণ না হওয়ার কারণ কী হতে পারে? আমরা ‘মি টু’ আন্দোলন হতে দেখেছে। মহিলারা সারা পৃথিবীব্যাপী কীভাবে নিজের বাড়িতে অতিনিকট জনের সম্মতিহীন বল পূর্বক যৌন লালসার শিকার হয়েছেন। নিজেদের কাজের জায়গায়, অতি আপনজন স্বামীর মাধ্যমেও বল পূর্বক যৌন লালসার শিকার হয়েছেন। আমি আগের লেখাতে বলেছিলাম কীভাবে নারীরা এই ধরনের অত্যাচারকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়।
প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা এই ধরনের শারীরিক এবং তার থেকে উদ্ভূত মানসিক যন্ত্রণাকে কীভাবে স্বাভাবিক ভাবছে? কোন ফর্মুলা মেনে তাঁরা নিজেদের জন্য থাকা সাংবিধানিক এবং সেই সঙ্গের আইনি অধিকারকে পাশে সরিয়ে রেখে দিচ্ছেন, আর সম্মতি বিষয়টিকে গুরুত্ত্ব দিয়ে ভাবতে পারছেন না? এখানে অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করে বলবেন, ধারা ৪৯৮-কে কীভাবে নারীরাই হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করে কত পুরুষের উপর অত্যাচার করেছে তার হিসেব আমি রাখিনি। রাখিনি এই কারণে কতজন নারী এই ধরনের রক্ষাকবচের কথা জানেন আর তার ব্যবহার করেন? যদি এই সব আইনি বিষয় সব শ্রেণির নারীরাই জানতেন তাহলে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক খুঁড়ে বউয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হত না। আবার রাশিকা আগার্বালদের মতো অতিশিক্ষিত মেয়েদের মারা যেতে হত না নিজের শ্বশুর বাড়িতেই।
এই মৃত্যুগুলির সঙ্গে জুড়ে থাকে ভারতীয় সমাজের সেই অধ্যায়গুলি যেখানে প্রচলিত সমাজের নারীদের প্রতি ধারণা ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় উদ্ধারকারী এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী মনোভাব ভারতীয় নারীর শরীর এবং মন নিয়ে আইনি সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু এই সংগ্রামের পরিণাম আমাদের এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতির দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে যেখানে ‘সম্মতির’ মতো বিষয়গুলি খুব যত্নের সঙ্গে অবগত থেকে বলার মতো বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নীতি নৈতিকতার বেড়াজাল দিয়ে নারীদের এমন ভাবে ঘিরে রাখা হয়েছিল যে নারীদের অবগত হওয়া থেকে সবসময় আড়াল করে রাখা হয়েছে।
এই মৃত্যুগুলির সঙ্গে জুড়ে থাকে ভারতীয় সমাজের সেই অধ্যায়গুলি যেখানে প্রচলিত সমাজের নারীদের প্রতি ধারণা ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় উদ্ধারকারী এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী মনোভাব ভারতীয় নারীর শরীর এবং মন নিয়ে আইনি সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু এই সংগ্রামের পরিণাম আমাদের এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতির দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে যেখানে ‘সম্মতির’ মতো বিষয়গুলি খুব যত্নের সঙ্গে অবগত থেকে বলার মতো বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নীতি নৈতিকতার বেড়াজাল দিয়ে নারীদের এমন ভাবে ঘিরে রাখা হয়েছিল যে নারীদের অবগত হওয়া থেকে সবসময় আড়াল করে রাখা হয়েছে।
আরও পড়ুন:

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-২৭: সমস্যা যখন ‘সম্মতি’ নেওয়া বা দেওয়ার
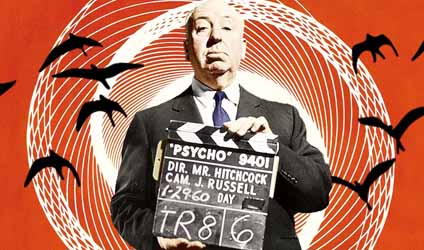
লাইট সাউন্ড ক্যামেরা অ্যাকশন, পর্ব-৬: হিচককের সাইকো—ম্যারিয়নের স্নান ও নর্মা-র মৃতদেহ

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৪২: আশা-ভরসার ‘শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক’
তাই ভারতীয় নারীদের এখনও সবসময় অদৃশ্য ঘোমটা পরে থাকতে হয়। ফুলমণির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ‘সম্মতি’র ধারনার একটি ইউরোপীয় ধাঁচের ধারণার প্রবেশ ঘটেছিল ভারতে। এই তথাকথিত বিদেশিদের দেওয়া আইনের লক্ষ্য ছিল নারীদের জীবনরক্ষা করা। কিন্তু ভারতীয় চেতনায় শুধু একজন ফুলমণির মৃত্যু খুব একটা গুরুত্ব পায় না। কারণ একটা মৃত্যু দিয়ে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ গর্ভধারণ প্রথা, যার মধ্যে দিয়ে জন্মান পুত্র সন্তান পূর্ব পুরুষের আত্মার মুক্তি ঘটাবে, ভীষণ রকম ভাবে ব্যহত হবে। ‘সম্মতি’ দেওয়ার বয়েস বেড়ে যাওয়া মানে নারীর গর্ভ তথা নারী দূষিত হয়ে যাবে। এর ফলে নারীর স্বামী-সহ বাকি আত্মীয়দের উপর তার খারাপ প্রভাব পড়বে। পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ক্রমেই হিন্দু সমাজ ধ্বংস হবে। এই ভাবে ধ্বংস হোক সমাজ তা কেউ মেনে নিতে চাইবে না। যে নারী অল্প বয়েসে মা হতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছেন সেও তখন বৃহত্তর স্বার্থে রাজি হয়ে যাচ্ছেন ‘সম্মতি’ দিয়ে দিতে।
একদিকে স্বাধীনতা আন্দলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এবং ভারতীয় সমাজের হারিয়ে যাওয়া গৌরব উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলছে। সেই পরিস্থিতিতে নারীদের আত্মত্যাগের বিষয় যেমন সতী প্রথা প্রভৃতি যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছিল তাতে সাধারণ নারী থেকে উচ্চ বর্ণের নারী গভীর ভাবে আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন যে, তাঁদের আত্মত্যাগ অনেক মহৎ। এই ভাবনা থেকে আজও আমরা সরে আসতে পারিনি। তাই নারীদের প্রতি যৌন অত্যাচারের খবর যখন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায় তখন আমরা শুনেছি, ‘এরকম ঘটনা হতেই পারে’, রাত্রিবেলা ওই জায়গায় যাওয়ার দরকার কী ছিল’, ‘ওই রকম পোশাক পরেছিল মানেই সে সম্মতি দিয়েই রেখেছিল’ ইত্যাদি।
একদিকে স্বাধীনতা আন্দলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এবং ভারতীয় সমাজের হারিয়ে যাওয়া গৌরব উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলছে। সেই পরিস্থিতিতে নারীদের আত্মত্যাগের বিষয় যেমন সতী প্রথা প্রভৃতি যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছিল তাতে সাধারণ নারী থেকে উচ্চ বর্ণের নারী গভীর ভাবে আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন যে, তাঁদের আত্মত্যাগ অনেক মহৎ। এই ভাবনা থেকে আজও আমরা সরে আসতে পারিনি। তাই নারীদের প্রতি যৌন অত্যাচারের খবর যখন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায় তখন আমরা শুনেছি, ‘এরকম ঘটনা হতেই পারে’, রাত্রিবেলা ওই জায়গায় যাওয়ার দরকার কী ছিল’, ‘ওই রকম পোশাক পরেছিল মানেই সে সম্মতি দিয়েই রেখেছিল’ ইত্যাদি।
আরও পড়ুন:

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-২: মেয়েটি যেন গৃহলক্ষ্মী

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-২৮: সাইনাস নাকি কখনওই সারে না?

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৪: সুন্দরবনের লবণ-বৃত্তান্ত
২০১২ সালে নির্ভয়া কেস যখন আমাদের সামনে আসে তখন সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে। এই ঘটনা ভারতীয় চেতনাতে অন্যরকম প্রভাব ফেলেছিল। একটি মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা কোনও একটি সাধারণ ঘটনা নয়। দেশের মানুষ এই অত্যাচারের তীব্রতা অনুভব করতে পারেন। তখন ফুলমণির কষ্টের কথা ধামাচাপা পড়ে গেলেও এ বারে ‘সম্মতির’ বিষয়টিকে নতুন করে গুরুত্ব দেওয়া হল। দেশের জনগণের সমবেত আন্দোলনের ফলে ‘সম্মতি’ সংক্রান্ত একটি সংশোধিত আইন প্রণয়ন করা হয়।
এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে যে, মানুষের নিজের মধ্যে চেতনা জাগরণ না হলে পরিবর্তন আনা যায় না। এই নতুন সংশোধিত আইনি সংজ্ঞাতে বলা হয় ‘সম্মতি’ সবসময় দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বেচ্ছাকৃত হয়, কোন শব্দ কিংবা ইঙ্গিত বা মৌখিক বা অমৌখিক ভাবে যৌনক্রিয়াতে অংশ গ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করা। আপাত দৃষ্টিতে সম্মতির এই সংজ্ঞা আমাদের মধ্যে ভরসা বাড়ায়। কিন্তু মানুষের চেতনার মধ্যে নির্ভয়ার মতো ঘটনার প্রভাব খেই হারিয়ে ফেলে যখন সম্মতির মতো বিষয়টিকে ভাবা হয় সরল রেখার মতো।
এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে যে, মানুষের নিজের মধ্যে চেতনা জাগরণ না হলে পরিবর্তন আনা যায় না। এই নতুন সংশোধিত আইনি সংজ্ঞাতে বলা হয় ‘সম্মতি’ সবসময় দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বেচ্ছাকৃত হয়, কোন শব্দ কিংবা ইঙ্গিত বা মৌখিক বা অমৌখিক ভাবে যৌনক্রিয়াতে অংশ গ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করা। আপাত দৃষ্টিতে সম্মতির এই সংজ্ঞা আমাদের মধ্যে ভরসা বাড়ায়। কিন্তু মানুষের চেতনার মধ্যে নির্ভয়ার মতো ঘটনার প্রভাব খেই হারিয়ে ফেলে যখন সম্মতির মতো বিষয়টিকে ভাবা হয় সরল রেখার মতো।
আরও পড়ুন:

হুঁকোমুখোর চিত্রকলা, পর্ব-৫: আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কী?

ইতিহাস কথা কও, কোচবিহারের রাজকাহিনি, পর্ব-১: রাজবাড়ির ইতিকথা—ইতিহাসের অন্তরে ইতিহাস

পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-১৯: পঞ্চমের সুরে লতার গাওয়া ‘মেরে নয়না সাওন ভাদো’ গান শুনে শুনেই প্রস্তুতি শুরু করেন কিশোর
২০১৭ সালে একটি ঘটনা ঘটে। ফারুকি নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন বিদেশে গবেষণারত ভারতীয় ধর্ষণের অভিযোগ আনেন। এই ঘটনাতে গবেষক মেয়েটির শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিকেও আদালত খুব গুরুত্ব সহকারে দেখে। কারণ ‘সম্মতির’ বিষয়টিকে এবার ফুলমণির মতো নাবালিকার দৃষ্টি কোণ থেকে দেখা হয়নি। দেখা হয়েছে একজন শিক্ষিত মেয়ে এই ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ তোলার আগেও যখন মেলামেশা করেছে, অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়েছে, নানা ধরনের কথা বার্তা বলেছে, তখন তার সম্মতি না দেওয়ার বা কখনও না থাকার বিষয়টি কীভাবে সমাজ দেখবে?
সমাজ নারীদের হঠাৎ মতো পরিবর্তন করাকে কখনও স্বাভাবিক বিষয় বলে মানতে চায় না। সমাজ মনে করে যেমন প্রকৃতি হঠাৎ পরিবর্তিত হয়, তেমন নারীরাও রহস্যময়ী হয়ে থাকে, আর নিজেদের মতামত পরিবর্তন করে নেয়। এই হঠাৎ পরিবর্তন পুরুষের কাছে অস্বস্তি তৈরি করে, শাসন করতে অসুবিধে হয়। তাই নারীদের মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই কেসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থ করা হল। কারণ ধর্ষণ করার সময় সেই মেয়েটি শারীরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।
কেন তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি সেই মুহূর্তে তার উত্তরে তিনি তাঁর বক্তব্যতে জানিয়েছিল, নিজেকে শারীরিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। সেই সঙ্গে নিজের উপরে এই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত চাপ, ওই ব্যক্তির শরীরের চাপ এতটাই তার উপরে পড়েছিল যে সে হাত-পা না ছুঁড়ে নিশ্চল থেকে যায়। এই কথা শুনে আদালত জানায়, শিক্ষিত মহিলাদের খুব পরিষ্কার করে তাঁদের অনিচ্ছা জানাতে হবে। আদালত জানায়, এ ক্ষেত্রে যেহেতু আগে থেকেই শারীরিক সংযোগ ছিল সেখানে সামান্য প্রতিরোধ, দুর্বল ভাবে ‘না’ ‘বলাকে সম্মতি নেই’ এটা বোঝা খুব শক্ত।
সমাজ নারীদের হঠাৎ মতো পরিবর্তন করাকে কখনও স্বাভাবিক বিষয় বলে মানতে চায় না। সমাজ মনে করে যেমন প্রকৃতি হঠাৎ পরিবর্তিত হয়, তেমন নারীরাও রহস্যময়ী হয়ে থাকে, আর নিজেদের মতামত পরিবর্তন করে নেয়। এই হঠাৎ পরিবর্তন পুরুষের কাছে অস্বস্তি তৈরি করে, শাসন করতে অসুবিধে হয়। তাই নারীদের মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই কেসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থ করা হল। কারণ ধর্ষণ করার সময় সেই মেয়েটি শারীরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।
কেন তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি সেই মুহূর্তে তার উত্তরে তিনি তাঁর বক্তব্যতে জানিয়েছিল, নিজেকে শারীরিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। সেই সঙ্গে নিজের উপরে এই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত চাপ, ওই ব্যক্তির শরীরের চাপ এতটাই তার উপরে পড়েছিল যে সে হাত-পা না ছুঁড়ে নিশ্চল থেকে যায়। এই কথা শুনে আদালত জানায়, শিক্ষিত মহিলাদের খুব পরিষ্কার করে তাঁদের অনিচ্ছা জানাতে হবে। আদালত জানায়, এ ক্ষেত্রে যেহেতু আগে থেকেই শারীরিক সংযোগ ছিল সেখানে সামান্য প্রতিরোধ, দুর্বল ভাবে ‘না’ ‘বলাকে সম্মতি নেই’ এটা বোঝা খুব শক্ত।

ছবি প্রতীকী। সংগৃহীত।
২০১৮ সালে আবার আমরা পৃথিবীব্যাপী ‘মি টু’ আন্দোলন হতে দেখা গেল। সেই আন্দলনের মূল বিষয় ছিল কীভাবে নারীরা তাঁদের ইতিবাচক জোরাল সম্মতি প্রকাশ করবে, না সম্মতি দেবে না। এ বারে সম্মতির ধারণার মধ্যে আবার দুটি প্রেক্ষাপট জুড়ে গেল। এক দিকে বলা হল ‘না মানে না’, আবার অন্য দিকে ‘হ্যাঁ মানে হ্যাঁ’। আমরা যেন খুব তীব্র, তীক্ষ্ণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোনওভাবেই বোঝাতে পারছি না সম্মতির মতো বিষয়টির প্রতিফলন কতটা সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল হওয়া দরকার।
নারী পুরুষের মধ্যে থাকা ক্ষমতার বিন্যাস এই সম্মতির ধারণাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ যখন বলে বিয়ে করেছি, তাই যৌনক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করার মধ্যে সম্মতির বিষয় মাথা গলাব কেন? মাথা গলাতে হবে, কারণ বিয়ে করা মানেই সেটা সামাজিক ঘটনা এবং বিয়ে কোনও আন্তঃব্যক্তি বিষয় নয়। তাই বিয়ের নামে যৌন আচরণ অন্য একজনের উপর দমনমূলক হতে পারে এই বোধ ভারতীয় সমাজে তৈরি হয়নি।
কিন্তু এই সামাজিক বিষয়ের মধ্যে নারী পুরুষের মধ্যেকার ক্ষমতার জাল এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছে যে, সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ধারণা জুড়ে গিয়ে এক বিশাল ক্ষমতার সংযুক্ত জাল নির্মাণ হয়েছে। এই বিস্তারিত জাল আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে। আমরা ক্রমেই এই জালের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে এক রকমের সাজ সেজে বসে আছি। এই জালের একটা অংশ হল সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জাল এবং এই জালের কাজ হল নজরদারি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি সমাজের নিচু তলা থেকে একদম ওপরের তলা অবধি অবধি এমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যে, মানুষ মনে করবে এই জালের মধ্যে থেকেই তাঁরা সমাজের মূল্যবোধকে বজায় রাখতে পারবে। এই জাল তাঁদের মধ্যে নানা ধরনের সীমানা তৈরি করে দেয়। পরস্পর বিরোধিতার সীমানা। ফলে মানুষ চাইবে এই সীমানার মধ্যে থাকলেই তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক দর্শনের বিরোধিতা করার অবকাশ পাবে না।
মানুষের কাছে এই সীমানাগুলি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করতে থাকে। কখনও দমনমূলক আবার কখনও মুক্তির স্বাদ দেওয়া। কিন্তু ভয় থেকে যায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার। তাই বিশেষ পরিস্থিতি মানুষকে বোঝাবে যে, তাদের পিতৃতান্ত্রিক আচরণগুলোই ভালো আচরণ এবং এই ভালো আচরণগুলি তাদের সমাজে বেঁচে থাকার রসদ। এই জাল তাদের কাছে অব্যর্থ যুক্তির সমান। এই যুক্তির মধ্যেই বিজ্ঞানের সত্যতা খোঁজা হবে।
* প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
ঋণ স্বীকার:
● Sarkar, Tanika. “A Prehistory of Rights: The Age of Consent Debate in Colonial Bengal.” Feminist Studies 26, no. 3 (2000): 601–22.
https://doi.org/10.2307/3178642
নারী পুরুষের মধ্যে থাকা ক্ষমতার বিন্যাস এই সম্মতির ধারণাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ যখন বলে বিয়ে করেছি, তাই যৌনক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করার মধ্যে সম্মতির বিষয় মাথা গলাব কেন? মাথা গলাতে হবে, কারণ বিয়ে করা মানেই সেটা সামাজিক ঘটনা এবং বিয়ে কোনও আন্তঃব্যক্তি বিষয় নয়। তাই বিয়ের নামে যৌন আচরণ অন্য একজনের উপর দমনমূলক হতে পারে এই বোধ ভারতীয় সমাজে তৈরি হয়নি।
কিন্তু এই সামাজিক বিষয়ের মধ্যে নারী পুরুষের মধ্যেকার ক্ষমতার জাল এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছে যে, সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ধারণা জুড়ে গিয়ে এক বিশাল ক্ষমতার সংযুক্ত জাল নির্মাণ হয়েছে। এই বিস্তারিত জাল আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে। আমরা ক্রমেই এই জালের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে এক রকমের সাজ সেজে বসে আছি। এই জালের একটা অংশ হল সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জাল এবং এই জালের কাজ হল নজরদারি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি সমাজের নিচু তলা থেকে একদম ওপরের তলা অবধি অবধি এমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যে, মানুষ মনে করবে এই জালের মধ্যে থেকেই তাঁরা সমাজের মূল্যবোধকে বজায় রাখতে পারবে। এই জাল তাঁদের মধ্যে নানা ধরনের সীমানা তৈরি করে দেয়। পরস্পর বিরোধিতার সীমানা। ফলে মানুষ চাইবে এই সীমানার মধ্যে থাকলেই তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক দর্শনের বিরোধিতা করার অবকাশ পাবে না।
মানুষের কাছে এই সীমানাগুলি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করতে থাকে। কখনও দমনমূলক আবার কখনও মুক্তির স্বাদ দেওয়া। কিন্তু ভয় থেকে যায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার। তাই বিশেষ পরিস্থিতি মানুষকে বোঝাবে যে, তাদের পিতৃতান্ত্রিক আচরণগুলোই ভালো আচরণ এবং এই ভালো আচরণগুলি তাদের সমাজে বেঁচে থাকার রসদ। এই জাল তাদের কাছে অব্যর্থ যুক্তির সমান। এই যুক্তির মধ্যেই বিজ্ঞানের সত্যতা খোঁজা হবে।
* প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
ঋণ স্বীকার:
https://doi.org/10.2307/3178642
* বৈষম্যের বিরোধ-জবানি (Gender Discourse): নিবেদিতা বায়েন (Nibedita Bayen), অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, পি আর ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ।