
সেই রাতটা আমার আজও মনে আছে। অনেকদিন আগের ঘটনা। সালটা ছিল ২০০৩। ডিসেম্বরের ১২ তারিখ। রাত প্রায় দশটা। চেম্বারে রোগী দেখা শেষ গোছগাছ করছি। চেম্বার বন্ধ করব। এমন সময় হঠাৎ লাঠি টুকটুক করতে করতে আমার ৮৫ বছর বয়স্ক বাবার চেম্বারে প্রবেশ। বাবাদের একটা বয়স্ক আড্ডার গ্রুপ বসতো আমার বাড়ি কাম চেম্বারের কাছেই। প্রতিদিন রাতে ঘণ্টা দুয়েক ধরে তাঁরা আড্ডা দিতেন, তারপর যে যার বাড়ি ফিরে যেতেন। এবং এই আড্ডাটা ছিল তাঁদের কাছে একটা বাঁচার অক্সিজেন। চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে বাবা গলা তুলে বললেন, ‘অখনো চেম্বার বন্ধ করস নাই। রাত হইল। ঠান্ডা পড়সে। চেম্বার বন্ধ কইরা উপরে আয়।’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, এই তো এখনই বন্ধ করব। তুমি সাবধানে উপরে যাও। মা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খাবার বেড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।’ আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে বাবা লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে চেম্বারের পাশের গেট খুলে আমাদের মূল বাড়ির দিকে এগোলেন। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল লাঠি ঠোকার আওয়াজ। মিনিট দশকের মধ্যেই আমিও চেম্বার আটকে ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় সবে উঠছি, এমন সময় আমার স্ত্রীর আর্ত চিৎকার ভেসে এলো, শিগগির উপরে এসো, বাবা যেন কেমন করছে!
আমি পড়িমড়ি করে দৌড়ে দোতলায় গিয়ে সোজা রান্নাঘরে ঢুকলাম। ঢুকে এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমার অন্যতম প্রিয় মানুষ আমার বাবা চেয়ারে বসা অবস্থায় মুখ গুঁজে পড়ে আছেন খাবারের থালাতে। মা-কাকিমা এবং বাড়ির অন্যান্যদের সমবেত ফুঁপিয়ে কান্না আমাকে আরও ধ্বস্ত করে দিল। মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম ভয়ংকর কিছু ঘটে গিয়েছে, বাবার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে বাবাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আমার কাছের মানুষ, দু’জন ডাক্তার দাদা মলয় ভট্টাচার্য এবং অমিতাভ রায়কে ফোন করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে দুজনেই ছুটে এলেন এবং দেখে বললেন এক্ষুনি হসপিটালাইস করতে হবে। এমন পরিস্থিতির জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, কেউই থাকেন না। তবু বাস্তবকে মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে বাবাকে মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করলাম। বাবা তখন গভীর কোমা স্টেজে। আমার স্নেহভাজন ডাঃ তরুণ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে শুরু হল চিকিৎসা। তবে ও প্রথমে দেখেই জানিয়ে দিল, অবস্থা খুবই খারাপ, তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। পরের দিনই বাবাকে দেওয়া হল ভেন্টিলেশনে। আজন্ম বাবার ছত্রছায়াতেই বড় হয়েছি, ডাক্তারি পড়েছি, পাশ করেছি, প্র্যাকটিসও করছি। মাথার উপর একটা ছাদ সব সময় ছিল।
পরপর কয়েক রাত নার্সিংহোমেই কাটিয়ে ছিলাম আমি। আরএমও-র রেস্টরুমে আমাকে রাতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতে আমার একেবারেই ঘুম হল না। ঘণ্টাখানেক বাদে বাদে লিফটে করে একতলা থেকে চার তলায় গিয়ে আইসিসিইউ-তে ঢুকে বাবার বেডের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে আসতাম। এ ভাবেই দিন রাত কাটতে লাগলো। প্রত্যেকদিনই মনে হতো আজ বাবা নিশ্চয়ই চোখ মেলে তাকাবেন। যে বিরাট হেমারেজিক ক্লটটা ব্রেনে আটকে আছে, সেটা নিশ্চয়ই সরে যাবে। নানা কথা মনে পড়তো বাবাকে নিয়ে। খুব ছোটবেলায় তো বাবাকে বিশেষ দেখিনি। যখন বাবা বনগাঁ পেট্রাপোল বর্ডারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন, তখন আমরা ছোটরা সব ঘুমিয়ে থাকতাম। আবার বাবা যখন রাত এগারোটায় ফিরতেন, তখনও আমরা ঘুমিয়ে থাকতাম। সপ্তাহে শুধু রবিবার বাবার সঙ্গ পেতাম। অনেক কষ্ট করে বাবা আমাকে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন। যদিও আমি ন্যাশনাল স্কলার হয়ে ছিলাম হায়ার সেকেন্ডারির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে, কিছু টাকাও বৃত্তিও পেতাম, কিন্তু তাতে আর কতটুকু হত! বাবা রোজগার করতেন খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু ১৪-১৫ জনের বিশাল পরিবার লালন-পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেতেন।
আমি পড়িমড়ি করে দৌড়ে দোতলায় গিয়ে সোজা রান্নাঘরে ঢুকলাম। ঢুকে এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমার অন্যতম প্রিয় মানুষ আমার বাবা চেয়ারে বসা অবস্থায় মুখ গুঁজে পড়ে আছেন খাবারের থালাতে। মা-কাকিমা এবং বাড়ির অন্যান্যদের সমবেত ফুঁপিয়ে কান্না আমাকে আরও ধ্বস্ত করে দিল। মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম ভয়ংকর কিছু ঘটে গিয়েছে, বাবার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে বাবাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আমার কাছের মানুষ, দু’জন ডাক্তার দাদা মলয় ভট্টাচার্য এবং অমিতাভ রায়কে ফোন করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে দুজনেই ছুটে এলেন এবং দেখে বললেন এক্ষুনি হসপিটালাইস করতে হবে। এমন পরিস্থিতির জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, কেউই থাকেন না। তবু বাস্তবকে মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে বাবাকে মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করলাম। বাবা তখন গভীর কোমা স্টেজে। আমার স্নেহভাজন ডাঃ তরুণ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে শুরু হল চিকিৎসা। তবে ও প্রথমে দেখেই জানিয়ে দিল, অবস্থা খুবই খারাপ, তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। পরের দিনই বাবাকে দেওয়া হল ভেন্টিলেশনে। আজন্ম বাবার ছত্রছায়াতেই বড় হয়েছি, ডাক্তারি পড়েছি, পাশ করেছি, প্র্যাকটিসও করছি। মাথার উপর একটা ছাদ সব সময় ছিল।
পরপর কয়েক রাত নার্সিংহোমেই কাটিয়ে ছিলাম আমি। আরএমও-র রেস্টরুমে আমাকে রাতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতে আমার একেবারেই ঘুম হল না। ঘণ্টাখানেক বাদে বাদে লিফটে করে একতলা থেকে চার তলায় গিয়ে আইসিসিইউ-তে ঢুকে বাবার বেডের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে আসতাম। এ ভাবেই দিন রাত কাটতে লাগলো। প্রত্যেকদিনই মনে হতো আজ বাবা নিশ্চয়ই চোখ মেলে তাকাবেন। যে বিরাট হেমারেজিক ক্লটটা ব্রেনে আটকে আছে, সেটা নিশ্চয়ই সরে যাবে। নানা কথা মনে পড়তো বাবাকে নিয়ে। খুব ছোটবেলায় তো বাবাকে বিশেষ দেখিনি। যখন বাবা বনগাঁ পেট্রাপোল বর্ডারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন, তখন আমরা ছোটরা সব ঘুমিয়ে থাকতাম। আবার বাবা যখন রাত এগারোটায় ফিরতেন, তখনও আমরা ঘুমিয়ে থাকতাম। সপ্তাহে শুধু রবিবার বাবার সঙ্গ পেতাম। অনেক কষ্ট করে বাবা আমাকে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন। যদিও আমি ন্যাশনাল স্কলার হয়ে ছিলাম হায়ার সেকেন্ডারির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে, কিছু টাকাও বৃত্তিও পেতাম, কিন্তু তাতে আর কতটুকু হত! বাবা রোজগার করতেন খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু ১৪-১৫ জনের বিশাল পরিবার লালন-পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেতেন।

শুধু ডাক্তারি পড়া নয়, বেকার অবস্থায় আমি বিয়ে করেছিলাম। বরং বলা ভালো বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেই বিয়ের খরচও বাবা দিয়েছিলেন। এমনকি আমার হনিমুনের খরচও। আমি ১৯৮৩ থেকে ৮৭ ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে কাজ করেছি। প্রতিবছর পয়লা এপ্রিল থেকে আমাদের রিনিউয়াল হতো। হঠাৎ ১৯৮৭-র ৩১ মার্চ দু’দিনের নোটিশে আমাদের তিনজন ডাক্তারকে পার্মানেন্টলি বসিয়ে দেওয়া হয়, আমি ছিলাম যার অন্যতম। ঠিক দেড় মাস বাদে ১৪ মে ছিল আমার বিয়ে। বাবাকে সব জানিয়ে বললাম, বিয়ে পিছিয়ে দিতে। তখন তো আমি পুরো বেকার, ভাবলাম বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস জমিয়ে নিই, তারপর বিয়ে করব। আমার জীবন রসিক বাবা এই প্রস্তাব শুনে বললেন, ‘জন্ম-মৃত্যু-বিয়া, তিন বিধাতা নিয়া। বিয়া পেছন যাইবো না, আমি ধার দিমু। বিয়া কর।’ হানিমুন করতে আমি কাঠমান্ডু গিয়েছিলাম মানে বিদেশে। প্রথম জীবনে প্লেন চড়া। পেপারে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, থ্রি নাইট ফোর ডেজ ৩৫০০ টাকার প্যাকেজ। অবশ্য আজ থেকে সেটা ৩৫ বছর আগে। এমন সুযোগ ছাড়া যায়! আমার কাছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ছিল শ-চারেক টাকা। মাকে বললাম সব। মা বলল বাবাকে। বাবার যথারীতি সহাস্য উত্তর, ‘দ্যাখ, আমার জীবনে হনিমুন হয় নাই, তোর দিদি জামাইবাবুরও হয় নাই, তুই হনিমুনে যা। আমি এখন যা লাগে দিমু, তুই আমারে শোধ কইরা দিস।’
প্র্যাকটিস শুরু করে চার মাস টাকা জমিয়ে আমি বাবার এই দেনাটাই প্রথমে শোধ করেছিলাম। তারপর তো জীবন বইতে শুরু করলো নিজের মতোই। প্র্যাকটিস জমছে না। অর্থের অভাব। এদিকে এক মেয়ের বাবা হয়ে গিয়েছি। বাবাই বেবি ফুড সাপ্লাই দিত। আমার বউ ধৃতিকণাও তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। ভেঙে পড়ার মানুষ আমি কোনওদিনই ছিলাম না, এখনও নেই। নেগেটিভিটি ব্যাপারটাই আমার জীবনে নেই। তবু প্র্যাকটিস পর্বের প্রথম দু’তিনটে বছর খুব কষ্টে কেটেছিল। বাবা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ‘লাইগ্যা থাক। এমন দিন আইবো, যখন দেখবি, রোগী আর টাকা দুই-ই তোর পিছনে ছুটবো।’ আমার বাবা ছিলেন কর্মযোগী মানুষ। অল্প শিক্ষিত, কিন্তু জীবনের লড়াই থেকে কোনওদিন এক পা পিছিয়ে আসেননি। বাবার পরিশীলিত ইংরাজি উচ্চারণ এবং সুন্দর হাতের লেখা নিয়ে আমার ভীষণ অহংকার হতো। মনে হতো, আমি কেন অমন পারি না! কিন্তু বাবার থেকে যেটা আমি পেয়েছিলাম সেটা হল, অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা। করোনা ঝড়ের আগে পর্যন্ত একই সঙ্গে আমি তিনটি প্রফেশন চালিয়েছি। ডাক্তারি, অভিনয় এবং লেখালেখি। আমি যখন প্রথম প্র্যাকটিস শুরু করি, তখন রাতবিরেতে ডাক পড়তো অর্থাৎ নাইট কল। আমার বাবা এবং আমার ফুলকাকা, দুজনেই জেগে বসে থাকতেন যতক্ষণ না আমি কল থেকে ফিরি। অনেক সময় ফুল কাকা আমার সঙ্গে পেশেন্টের বাড়ি পর্যন্ত যেতেন, আবার ফিরতেন।
বাবাকে নিয়ে এমন এলোমেলো অনেক কথাই মনে পড়তো তখন, কারও সঙ্গে শেয়ার করতাম না। কথাগুলো নিজের বুকেই রাখতাম, আর প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম, বাবা যেন একবার চোখ মেলে তাকান। দেখতে দেখতে ১৮ দিন হয়ে গেল। বাবা চেতনাহীন হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা বাবাকে নিয়ম করে দেখতে যেতাম। অনেকক্ষণ বেডের পাশে বসে থাকতাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতাম, বাবা বাবা বলে, যদি বাবা চোখ মেলে তাকান! কিন্তু না, বাবা এর মধ্যে একদিনও চোখ খোলেনি, নড়াচড়াও করেননি। ১৯-তম দিনে অন্য দিনের মতোই সকাল ১১টা নাগাদ আমি আর ভাই বাবাকে দেখতে গেলাম। একই অবস্থা। একটু থাকার পর ভাইকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে আমি ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে ডাক্তারি করতে বেরিয়ে গেলাম গাড়ি নিয়ে। মিশনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। এমন সময় ভাইয়ের ফোন। ও ফোনে জানালো, বাবা চোখ পিটপিট করছে, একটা হাতের আঙুলও নাকি একটু নড়ছে! শুনিই গাড়ি ঘোরালাম। নার্সিংহোমে পৌঁছে দ্রুত এসে দাঁড়ালাম বাবার বেডের পাশে। বাবা বাবা করে ডাকলাম এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম বাবা ধীরে ধীরে দুটো চোখই কিছুটা খুললেন। আমি বাবার একটা হাত ধরলাম। দেখলাম, সেটার আঙুল গুলো একটু একটু নড়ছে। আনন্দে-আবেশে চোখে জল এসে গেল আমাদের সবারই। বাবা তাহলে কোমা থেকে, ভেন্টিলেশন থেকে ফিরে আসছে! তাহলে তো বাবাকে নিশ্চয়ই আমরা এবার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো! মোবাইল থেকে ফোন করলাম ডাক্তার তরুণকে। একটু বাদে ও চলে এলো। বাবাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, ‘অমিতাভ দা, মিরাকেল ঘটছে। মনে হয় মেসোমশাইকে দু-চার দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরিয়ে দিতে পারব।’ কৃতজ্ঞতায় তরুণের হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে থ্যাংকস জানালাম বারবার।
প্র্যাকটিস শুরু করে চার মাস টাকা জমিয়ে আমি বাবার এই দেনাটাই প্রথমে শোধ করেছিলাম। তারপর তো জীবন বইতে শুরু করলো নিজের মতোই। প্র্যাকটিস জমছে না। অর্থের অভাব। এদিকে এক মেয়ের বাবা হয়ে গিয়েছি। বাবাই বেবি ফুড সাপ্লাই দিত। আমার বউ ধৃতিকণাও তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। ভেঙে পড়ার মানুষ আমি কোনওদিনই ছিলাম না, এখনও নেই। নেগেটিভিটি ব্যাপারটাই আমার জীবনে নেই। তবু প্র্যাকটিস পর্বের প্রথম দু’তিনটে বছর খুব কষ্টে কেটেছিল। বাবা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ‘লাইগ্যা থাক। এমন দিন আইবো, যখন দেখবি, রোগী আর টাকা দুই-ই তোর পিছনে ছুটবো।’ আমার বাবা ছিলেন কর্মযোগী মানুষ। অল্প শিক্ষিত, কিন্তু জীবনের লড়াই থেকে কোনওদিন এক পা পিছিয়ে আসেননি। বাবার পরিশীলিত ইংরাজি উচ্চারণ এবং সুন্দর হাতের লেখা নিয়ে আমার ভীষণ অহংকার হতো। মনে হতো, আমি কেন অমন পারি না! কিন্তু বাবার থেকে যেটা আমি পেয়েছিলাম সেটা হল, অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা। করোনা ঝড়ের আগে পর্যন্ত একই সঙ্গে আমি তিনটি প্রফেশন চালিয়েছি। ডাক্তারি, অভিনয় এবং লেখালেখি। আমি যখন প্রথম প্র্যাকটিস শুরু করি, তখন রাতবিরেতে ডাক পড়তো অর্থাৎ নাইট কল। আমার বাবা এবং আমার ফুলকাকা, দুজনেই জেগে বসে থাকতেন যতক্ষণ না আমি কল থেকে ফিরি। অনেক সময় ফুল কাকা আমার সঙ্গে পেশেন্টের বাড়ি পর্যন্ত যেতেন, আবার ফিরতেন।
বাবাকে নিয়ে এমন এলোমেলো অনেক কথাই মনে পড়তো তখন, কারও সঙ্গে শেয়ার করতাম না। কথাগুলো নিজের বুকেই রাখতাম, আর প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম, বাবা যেন একবার চোখ মেলে তাকান। দেখতে দেখতে ১৮ দিন হয়ে গেল। বাবা চেতনাহীন হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা বাবাকে নিয়ম করে দেখতে যেতাম। অনেকক্ষণ বেডের পাশে বসে থাকতাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতাম, বাবা বাবা বলে, যদি বাবা চোখ মেলে তাকান! কিন্তু না, বাবা এর মধ্যে একদিনও চোখ খোলেনি, নড়াচড়াও করেননি। ১৯-তম দিনে অন্য দিনের মতোই সকাল ১১টা নাগাদ আমি আর ভাই বাবাকে দেখতে গেলাম। একই অবস্থা। একটু থাকার পর ভাইকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে আমি ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে ডাক্তারি করতে বেরিয়ে গেলাম গাড়ি নিয়ে। মিশনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। এমন সময় ভাইয়ের ফোন। ও ফোনে জানালো, বাবা চোখ পিটপিট করছে, একটা হাতের আঙুলও নাকি একটু নড়ছে! শুনিই গাড়ি ঘোরালাম। নার্সিংহোমে পৌঁছে দ্রুত এসে দাঁড়ালাম বাবার বেডের পাশে। বাবা বাবা করে ডাকলাম এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম বাবা ধীরে ধীরে দুটো চোখই কিছুটা খুললেন। আমি বাবার একটা হাত ধরলাম। দেখলাম, সেটার আঙুল গুলো একটু একটু নড়ছে। আনন্দে-আবেশে চোখে জল এসে গেল আমাদের সবারই। বাবা তাহলে কোমা থেকে, ভেন্টিলেশন থেকে ফিরে আসছে! তাহলে তো বাবাকে নিশ্চয়ই আমরা এবার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো! মোবাইল থেকে ফোন করলাম ডাক্তার তরুণকে। একটু বাদে ও চলে এলো। বাবাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, ‘অমিতাভ দা, মিরাকেল ঘটছে। মনে হয় মেসোমশাইকে দু-চার দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরিয়ে দিতে পারব।’ কৃতজ্ঞতায় তরুণের হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে থ্যাংকস জানালাম বারবার।
ক’দিন বাদে বাবাকে সত্যিই বাড়ি নিয়ে এলাম। তবে এটা বুঝলাম, এই বাবা আর সেই আগের বাবা নেই। সম্পূর্ণ বিছানায় শয্যাশায়ী, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, যাকে বলে একবারে ভেজিটেটিভ কন্ডিশন। নিয়মিত ফিজিওথেরাপি চলতে লাগলো। মাস দুয়েক বাদে অনেকটা উন্নতি দেখা দিল। বাবাকে উঠে বসাতে পারলাম। এরপর ধরে ধরে হাঁটানোও শুরু করলাম। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আবার রি-অ্যাটাক, আবার সেরিব্রাল। আবার ভর্তি করা হলো মিডল্যান্ডে। কিছুদিন যমে মানুষে টানাটানির পর গলায় ফুটো করে (ট্রাকিওসটমি) অক্সিজেন-স্যালাইন সাপোর্ট দিয়ে বাবাকে আবার বাড়ি নিয়ে এলাম। এরপর বাবা আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি। বাড়িতেই বাবার ঘরটিকে মিনি নার্সিংহোম বানানো হল। ২৪ ঘণ্টা অক্সিজেন ও অ্যাটেনডেন্ট, সাকার মেশিন, রাইলস টিউব, ক্যাথিটার… সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হল। মাঝে মাঝে তীব্র শ্বাসকষ্ট হলে স্যালাইন চালিয়ে ইন্ট্রাভেনাস স্টেরয়েড দিতাম আমি নিজে হাতেই। অনেক সময় শিরা পাওয়া যেত না। বাবার এই প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় মধ্যেও আমি ঘরে ঢুকলে বাবা ঠিক টের পেতেন। দেহের কোনও অংশই নাড়াতে পারতেন না। কিন্তু চোখ ঘুরিয়ে আমি কোন দিকে যাচ্ছি না যাচ্ছি, ঠিক খেয়াল করতেন। যখন কাজ ছেড়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম, বাবার চোখে মুখে কেমন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠতো। এটা কেবল বাবা আর আমিই বুঝতে পারতাম, আর কেউ নয়।
শেষদিকে বাবাকে স্যালাইন চালানো খুব মুশকিল হয়ে উঠেছিল, কারণ বাবার কোনও শিরা পাওয়া যেত না। দিনদিন চেহারাটা যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল, তাছাড়া বেডসোরগুলোও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। প্রায় রাতেই অবস্থা খারাপ হলে রাতে যিনি ডিউটিতে থাকতেন, সেই দিদি এসে আমার ঘরের দরজায় নক করতেন। আমি সজাগ থাকতাম। প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে বাবার ঘরে যেতাম। এমন এক রাতে কিছুতেই বাবার ভেন পাচ্ছি না, হাতে-পায়ে নানা জায়গায় চেষ্টা করলাম। ফ্লুইড চালাতে পারছি না। অথচ বাবার তীব্র শ্বাসকষ্ট, অক্সিজেন চালু থাকা সত্ত্বেও বুকের খাঁচাটা হাঁপরের মতো ওঠা নামা করছে। হতাশ হয়ে সেদিন বলেই ফেললাম, আমি আর পারছি না বাবা।
এবার তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারো। প্রায় আড়াই বছর ধরে তুমিও লড়ছো, আমিও লড়ছি। আমি ভীষণ ক্লান্ত, ধ্বস্ত। অ্যাটেনডেন্ট দিদিকে বললাম, অক্সিজেনই চলুক, আর একটা ইনজেকশন ইন্ট্রামাসকুলার দিচ্ছি। ঘর ছেড়ে বেরোতে যাচ্ছি, দেখলাম বাবা আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। যেন বলতে চাইছে, আমাকে ছেড়ে যাস না, আর একবার চেষ্টা করে দেখ। কি মনে হল, সত্যিই আর একবার চেষ্টা করলাম এবং একটা খুব সূক্ষ্ম শিরা পায়ের গোড়ালির ওখানে, পেয়েও গেলাম। খুব সন্তর্পনে সেখানেই চ্যানেল করে স্যালাইন চালানো শুরু করলাম এবং ইন্ট্রাভেনাস স্টেরয়েড ও ডেরিফাইলিন দিয়ে দিলাম। ম্যাজিকের মতো কাজ হল। মিনিট চার-পাঁচের মধ্যেই বাবার শ্বাসকষ্ট অনেক কমে গেল। বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।
শেষদিকে বাবাকে স্যালাইন চালানো খুব মুশকিল হয়ে উঠেছিল, কারণ বাবার কোনও শিরা পাওয়া যেত না। দিনদিন চেহারাটা যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল, তাছাড়া বেডসোরগুলোও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। প্রায় রাতেই অবস্থা খারাপ হলে রাতে যিনি ডিউটিতে থাকতেন, সেই দিদি এসে আমার ঘরের দরজায় নক করতেন। আমি সজাগ থাকতাম। প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে বাবার ঘরে যেতাম। এমন এক রাতে কিছুতেই বাবার ভেন পাচ্ছি না, হাতে-পায়ে নানা জায়গায় চেষ্টা করলাম। ফ্লুইড চালাতে পারছি না। অথচ বাবার তীব্র শ্বাসকষ্ট, অক্সিজেন চালু থাকা সত্ত্বেও বুকের খাঁচাটা হাঁপরের মতো ওঠা নামা করছে। হতাশ হয়ে সেদিন বলেই ফেললাম, আমি আর পারছি না বাবা।
এবার তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারো। প্রায় আড়াই বছর ধরে তুমিও লড়ছো, আমিও লড়ছি। আমি ভীষণ ক্লান্ত, ধ্বস্ত। অ্যাটেনডেন্ট দিদিকে বললাম, অক্সিজেনই চলুক, আর একটা ইনজেকশন ইন্ট্রামাসকুলার দিচ্ছি। ঘর ছেড়ে বেরোতে যাচ্ছি, দেখলাম বাবা আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। যেন বলতে চাইছে, আমাকে ছেড়ে যাস না, আর একবার চেষ্টা করে দেখ। কি মনে হল, সত্যিই আর একবার চেষ্টা করলাম এবং একটা খুব সূক্ষ্ম শিরা পায়ের গোড়ালির ওখানে, পেয়েও গেলাম। খুব সন্তর্পনে সেখানেই চ্যানেল করে স্যালাইন চালানো শুরু করলাম এবং ইন্ট্রাভেনাস স্টেরয়েড ও ডেরিফাইলিন দিয়ে দিলাম। ম্যাজিকের মতো কাজ হল। মিনিট চার-পাঁচের মধ্যেই বাবার শ্বাসকষ্ট অনেক কমে গেল। বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।
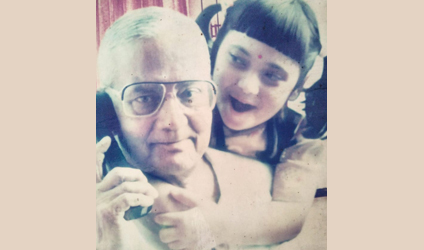
বাবাকে নিয়ে আমার এই দীর্ঘ লড়াইয়ের পর্বে আমি অনেককেই পাশে পেয়েছি। টেলিফোনে প্রায় একদিন বাদে বাদেই আমার স্নেহভাজন অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় বাবার খোঁজখবর নিত এবং সেটা নিয়ম করে জানাত তার বাবাকে অর্থাৎ সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে। সঞ্জীবদা নিজেও একাধিক বার ফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। নানা পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে আমি যাতে ভেঙে না পরি, যাতে ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু বাবার মৃত্যু পর্যন্ত করতে পারি। এদিকে এত কষ্ট সহ্য করেও বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা জন নানা কথা বলতে শুরু করলেন। আমার অতিরিক্ত ডাক্তারির জন্যই বাবার মৃত্যু হচ্ছে না, এমন কথাও শুনতে হল। অথচ ডাক্তার হিসেবে আমি আমার ন্যূনতম কর্তব্যটুকুই করেছি। চোখের সামনে আমার প্রিয়তম মানুষটি শ্বাসকষ্টে কষ্ট পাচ্ছেন কিংবা তার ইউরিন হচ্ছে না, কিংবা বেডসোর বেড়ে যাচ্ছে… আমার পক্ষে কি তখন সম্ভব ডাক্তার হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা!

অবশেষে বাবার মুক্তির দিন এলো। রাত বারোটা নাগাদ আমার ডাক্তার বন্ধু রজতকে দিয়ে বাবাকে চেকআপ করিয়ে ঘরে ফিরলাম। ও গাড়িতে ওঠার আগে বলল, এক্ষুনি তেমন কিছু ঘটবে না, আরও সপ্তাহখানেক তো বটেই। অথচ তার ঘণ্টাখানেক বাদেই আমার দরজায় টোকা। রাতের দিদি এসে বললেন, বাবার কোনও সাড়াশব্দ নেই। ছুটে গিয়ে দেখলাম লড়াই শেষ করে বাবা নিশ্চিন্তে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন। দিনটা ছিল ১৭ মে ২০০৫। বাবার শেষ সময়টা আমরা কাছের মানুষটা কেউই তার পাশে থাকতে পারলাম না। বাবার ইচ্ছে ছিল কাশিপুর মহাশ্মশান যেখানে ঠাকুরের শেষকৃত্য হয়েছিল, সেখানেই যেন বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন সকালে বাবাকে নিয়ে আমরা শেষযাত্রায় ওখানেই গেলাম।
শ্মশানে পৌঁছানোর একটু বাদেই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এলেন সপরিবারে। সঙ্গে মানুষ সমান একটি লাল গোলাপের রিং। যেটি নিজে হাতে আমার বাবার মৃতদেহের উপরে রেখে প্রণাম জানালেন। আমি বললাম দাদা, ‘আপনার তো এখন লেখার প্রচণ্ড চাপ, তাছাড়া শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। আপনি কেন আসতে গেলেন!’ স্মিত হেসে সঞ্জীবদা বললেন, ‘এসেছিলাম এই মানুষটিকে প্রণাম জানাতে। কেন জানেন! এই মানুষটিই তো আপনার মতো একজন কৃতি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।’ এমন কথা শুনে চোখে জল এসে গেল আমার। সত্যিই কি আমি কৃতি সন্তান! বাবার প্রতি যে কোনও সন্তানের যা করা উচিত, আমি তো শুধু সেটুকুই করেছি, এর বেশি কিছু নয়। অনেক আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম, মা-বাবার মৃত্যুর পরে আমি কোনও ধরাচুড়া পড়বো না, অশৌচ পালন করব না, শ্রাদ্ধ-শান্তিও করবো না। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরা অনুরোধ করলেন, মা যখন বেঁচে আছেন, অন্তত একদিন নিয়মকানুন মানতে। শুনলাম মারও সেটাই ইচ্ছে। রাজি হলাম। শ্মশান থেকে ফিরে সেই দিন কাছা-কোছা পরলাম। কিন্তু মনটা বড্ড খচখচ করছিল। পরের দিন সকালেই ফোন করলাম আমার গুরু সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে। আমার দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থাটা উনি খুব ভালো উপলব্ধি করলেন। আমাকে বললেন, ‘আপনি তো জীবিত অবস্থায় আমৃত্যু বাবার জন্য অনেক কিছুই করেছেন। এখন আর কিছু করার দরকার নেই। যেটা মন চাইবে না, সেটা কখনও করবেন না। শুধু একটা কাজ প্রতিদিন সকালবেলা করবেন। স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে হাতজোড় করে বাবার উদ্দেশ্যে বলবেন, হে পিতা তুমি আমাকে পৃথিবীতে এনেছিলে বলেই আমি এই পৃথিবীর রং-রস-রূপ-গন্ধ, সবকিছু অনুভব করতে পারছি। আমি একটা সুন্দর জীবন পেয়েছি শুধু তোমারই জন্য, একটা সুন্দর সংসার পেয়েছি। আনন্দ দুঃখ সবকিছুই অনুভব করতে পারছি। এর সবকিছুর জন্য দায়ী তুমি। কারণ তুমিই আমাকে পৃথিবীতে এনেছিলে। তাই তোমাকে আমার অন্তর থেকে প্রণাম জানাই।’
শ্মশানে পৌঁছানোর একটু বাদেই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এলেন সপরিবারে। সঙ্গে মানুষ সমান একটি লাল গোলাপের রিং। যেটি নিজে হাতে আমার বাবার মৃতদেহের উপরে রেখে প্রণাম জানালেন। আমি বললাম দাদা, ‘আপনার তো এখন লেখার প্রচণ্ড চাপ, তাছাড়া শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। আপনি কেন আসতে গেলেন!’ স্মিত হেসে সঞ্জীবদা বললেন, ‘এসেছিলাম এই মানুষটিকে প্রণাম জানাতে। কেন জানেন! এই মানুষটিই তো আপনার মতো একজন কৃতি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।’ এমন কথা শুনে চোখে জল এসে গেল আমার। সত্যিই কি আমি কৃতি সন্তান! বাবার প্রতি যে কোনও সন্তানের যা করা উচিত, আমি তো শুধু সেটুকুই করেছি, এর বেশি কিছু নয়। অনেক আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম, মা-বাবার মৃত্যুর পরে আমি কোনও ধরাচুড়া পড়বো না, অশৌচ পালন করব না, শ্রাদ্ধ-শান্তিও করবো না। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরা অনুরোধ করলেন, মা যখন বেঁচে আছেন, অন্তত একদিন নিয়মকানুন মানতে। শুনলাম মারও সেটাই ইচ্ছে। রাজি হলাম। শ্মশান থেকে ফিরে সেই দিন কাছা-কোছা পরলাম। কিন্তু মনটা বড্ড খচখচ করছিল। পরের দিন সকালেই ফোন করলাম আমার গুরু সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে। আমার দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থাটা উনি খুব ভালো উপলব্ধি করলেন। আমাকে বললেন, ‘আপনি তো জীবিত অবস্থায় আমৃত্যু বাবার জন্য অনেক কিছুই করেছেন। এখন আর কিছু করার দরকার নেই। যেটা মন চাইবে না, সেটা কখনও করবেন না। শুধু একটা কাজ প্রতিদিন সকালবেলা করবেন। স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে হাতজোড় করে বাবার উদ্দেশ্যে বলবেন, হে পিতা তুমি আমাকে পৃথিবীতে এনেছিলে বলেই আমি এই পৃথিবীর রং-রস-রূপ-গন্ধ, সবকিছু অনুভব করতে পারছি। আমি একটা সুন্দর জীবন পেয়েছি শুধু তোমারই জন্য, একটা সুন্দর সংসার পেয়েছি। আনন্দ দুঃখ সবকিছুই অনুভব করতে পারছি। এর সবকিছুর জন্য দায়ী তুমি। কারণ তুমিই আমাকে পৃথিবীতে এনেছিলে। তাই তোমাকে আমার অন্তর থেকে প্রণাম জানাই।’

সঞ্জীবদা এর কিছুটা সংস্কৃতে আমাকে বলেছিলেন, তারপরে বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এত চমৎকার ভাবে স্পষ্ট উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন যে শুনতে শুনতেই আমার দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছিল জলের ধারা। আমি তাঁর কথা মেনে প্রতিদিন এই আচারটি পালন করতাম। আমরা বাবার কোনও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিনি, করে ছিলাম শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান, যেখানে প্রিয়জনেরা বাবাকে নিয়ে নানা কথা বলেছিল, গান শুনিয়ে ছিল, ছড়া পাঠ করেছিল। একদম শেষে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী চিত্রলেখা চৌধুরির সঙ্গে আমরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলাম, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে…। বাবা লোকজনকে খুব খাওয়াতে ভালোবাসতেন। আমরাও অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত সবাইকে ভুরিভোজন করিয়েছিলাম, যেন বাবাই সবাইকে ডেকে খাওয়াচ্ছেন।
সংসারে বাবাদের নিয়ে কোন কালেই সেভাবে চর্চা হয় না। সন্তান পালনে মায়েরাই কৃতিত্বের ভাগীদার হন সব সময়। আমার বাবা ছিলেন কর্মযোগী এক লো-প্রোফাইল জীবন রসিক মানুষ। বাবা চলে গিয়েছেন ১৭ বছর হয়ে গেল। মাও চলে গিয়েছেন। এঁদের অস্তিত্ব আমি প্রতিদিন প্রতি কাজেই অনুভব করি। এঁরা ছায়ার মতো আমাকে জড়িয়ে থাকেন, ভালো কাজে প্রাণিত করেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত করেন। আর আমার গুরু, আমার আরেক পিতা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের আশীর্বাদের হাত সব সময় আমার মাথার উপর আছে বলেই আজ আমি একটু আধটু লেখালেখি করতে শিখেছি। জীবনটাকে অন্যভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছি। আমার দুই পিতাকেই জানালাম সশ্রদ্ধ প্রণাম।
সংসারে বাবাদের নিয়ে কোন কালেই সেভাবে চর্চা হয় না। সন্তান পালনে মায়েরাই কৃতিত্বের ভাগীদার হন সব সময়। আমার বাবা ছিলেন কর্মযোগী এক লো-প্রোফাইল জীবন রসিক মানুষ। বাবা চলে গিয়েছেন ১৭ বছর হয়ে গেল। মাও চলে গিয়েছেন। এঁদের অস্তিত্ব আমি প্রতিদিন প্রতি কাজেই অনুভব করি। এঁরা ছায়ার মতো আমাকে জড়িয়ে থাকেন, ভালো কাজে প্রাণিত করেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত করেন। আর আমার গুরু, আমার আরেক পিতা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের আশীর্বাদের হাত সব সময় আমার মাথার উপর আছে বলেই আজ আমি একটু আধটু লেখালেখি করতে শিখেছি। জীবনটাকে অন্যভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছি। আমার দুই পিতাকেই জানালাম সশ্রদ্ধ প্রণাম।



















