
অলঙ্করণ: লেখক।
টেনিদা চোখ পাকিয়ে বলল, শাট্ আপ ক্যাবলা…
ক্যাবলার দোষ ঠিক কোথায় তা কেউ জানে? মেফিস্টোফিলিস মানে যে শয়তান, তার নামে জয়ধ্বনি দেওয়া কেমন শয়তানি?
আসলে। আসলে যে কী তার ঠিক নেই। তবুও আসলে, ক্যাবলার কোনও দোষ নেই। ক্যাবলাদের-ও। তাদেরও একটা ভালো নাম থাকে। কী যেন নাম ছিল ক্যাবলার? তাতে কী বা আসে যায়, কেউ কেউ নিজেই নিজের নাম দেয় পেলব রায়, আর কেউ কেউ নির্বিশেষে হয়ে ওঠে ক্যাবলা। ক্যাবলা মানে কী? সে কথা না হয় তোলা থাক। আমরা যে যেমনটা বুঝি তাই দিয়েই আপাতত চলুক। ক্যাবলা জানে, নাগপুর বা কানপুর বা চাঁদপুর ঠিক কোথায়। রাঁচি আর করাচির ব্যবধান কতটুকু তার জানা আছে। জানে বলেই, আর অন্যে সেটা মানে না বলেই সে ‘ক্যাবলা’…
নচিকেতার পিতা হয়তো এমনটাই বলতে চেয়েছিলেন। এমন হাড় জিরজিরে জীর্ণ গাভী দান করে পুণ্য হয়? তাহলে আমাকে কার কাছে দেবেন বলে স্থির করেছেন হে পিতঃ?
এমন জিজ্ঞাসা করতে নেই যে। যে করে সে ক্যাবলা হয়। অথবা আত্মজ্ঞানী।
এই যে সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে দুমদাম পাহাড়ে যাচ্ছে জঙ্গলে যাচ্ছে হিমালয় থেকে সাহারায় কুংফুর প্যাঁচ কিংবা বুদ্ধির রেসে চমক দিচ্ছে, তাকে ভিলেনরা ‘বাচ্ছাছেলে’ ভাবতে ছাড়ছে কী? আর একের পর এক স্বপ্ন এঁকে চলা মুকুল তো বলেই দিল ‘আমি তো বড় হইনি’… তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে সমীকরণ?
তার আগে, ক্যাবলারা ছোট না বড় সেটাই তো জানা দরকার। এরা ছোট হলেও বড়, আর বড় হলেও ছোট। এরা বড় হোক, ‘দাদা’রা সেটা চায় কই?
বনভোজনে একে একে দেউটি নিভছে, আর পিকনিকের মরণযাত্রার ঘোষণা করছে ক্যাবলা, ইন্সটলমেন্টে। যেন ফটিক জল মেপে চলেছে, বলছে, ”এক বাও মেলে না। দো বাও মেলে—এ-এ না।”
আসুন, এই হযবরল-র জগতে আপনাকে স্বাগত জানাই।
ক্যাবলার দোষ ঠিক কোথায় তা কেউ জানে? মেফিস্টোফিলিস মানে যে শয়তান, তার নামে জয়ধ্বনি দেওয়া কেমন শয়তানি?
আসলে। আসলে যে কী তার ঠিক নেই। তবুও আসলে, ক্যাবলার কোনও দোষ নেই। ক্যাবলাদের-ও। তাদেরও একটা ভালো নাম থাকে। কী যেন নাম ছিল ক্যাবলার? তাতে কী বা আসে যায়, কেউ কেউ নিজেই নিজের নাম দেয় পেলব রায়, আর কেউ কেউ নির্বিশেষে হয়ে ওঠে ক্যাবলা। ক্যাবলা মানে কী? সে কথা না হয় তোলা থাক। আমরা যে যেমনটা বুঝি তাই দিয়েই আপাতত চলুক। ক্যাবলা জানে, নাগপুর বা কানপুর বা চাঁদপুর ঠিক কোথায়। রাঁচি আর করাচির ব্যবধান কতটুকু তার জানা আছে। জানে বলেই, আর অন্যে সেটা মানে না বলেই সে ‘ক্যাবলা’…
নচিকেতার পিতা হয়তো এমনটাই বলতে চেয়েছিলেন। এমন হাড় জিরজিরে জীর্ণ গাভী দান করে পুণ্য হয়? তাহলে আমাকে কার কাছে দেবেন বলে স্থির করেছেন হে পিতঃ?
এমন জিজ্ঞাসা করতে নেই যে। যে করে সে ক্যাবলা হয়। অথবা আত্মজ্ঞানী।
এই যে সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে দুমদাম পাহাড়ে যাচ্ছে জঙ্গলে যাচ্ছে হিমালয় থেকে সাহারায় কুংফুর প্যাঁচ কিংবা বুদ্ধির রেসে চমক দিচ্ছে, তাকে ভিলেনরা ‘বাচ্ছাছেলে’ ভাবতে ছাড়ছে কী? আর একের পর এক স্বপ্ন এঁকে চলা মুকুল তো বলেই দিল ‘আমি তো বড় হইনি’… তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে সমীকরণ?
তার আগে, ক্যাবলারা ছোট না বড় সেটাই তো জানা দরকার। এরা ছোট হলেও বড়, আর বড় হলেও ছোট। এরা বড় হোক, ‘দাদা’রা সেটা চায় কই?
বনভোজনে একে একে দেউটি নিভছে, আর পিকনিকের মরণযাত্রার ঘোষণা করছে ক্যাবলা, ইন্সটলমেন্টে। যেন ফটিক জল মেপে চলেছে, বলছে, ”এক বাও মেলে না। দো বাও মেলে—এ-এ না।”
আসুন, এই হযবরল-র জগতে আপনাকে স্বাগত জানাই।
“আমাদের সিটি কলেজ খুব ভালো। খালি ছুটি দেয়। আজও চড়কষষ্ঠী না কোদালে অমাবস্যা- কিসের একটা বন্ধ ছিল। আমি সোজা চলে এলুম চাটুজ্যেদের রোয়াকে। দেখি, টেনিদা হাত-পা নেড়ে কী সব যেন বোঝাচ্ছে ক্যাবলা আর হাবুল সেনকে।”
এই হল সেই জগৎ যেখানে রাজা-উজির মরে কথায় কথায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, ক্রিকেটে উইকেট পড়লেও মূর্তিমান ‘উইকেড’ হয়ে ব্যাট চালানো যায়। পড়ে যাওয়া উইকেট পুনঃস্থাপিত করে ঝিঁঝিঁ খেলা চলে। নিজের গোলে গোল দিয়ে কেউ নায়ক বনে যায় তো কেউ হনলুলুর মাকুদার জন্য জীবনপাত করে দেয় দেশের পক্ষ থেকে। হিসাবের খাতার পাতা ল্যাম্পপোস্টের তারে গিয়ে বেঁধে থাকে, শিঙিমাছের পাখনা কেটে কেটে একটা মাছেই তিনমাস দিব্যি মাছের ঝোল খাওয়া যায়। কেউ হাঁড়ি-কড়ার দুঃখে উন্মাদ হয় তো কেউ পিলে চমকানো প্রভাতসঙ্গীত শুনেও বখশিস করে চলে যায়।
হাসি পায়? হযবরল-র দুনিয়ায় ন্যাড়া, হিজিবিজবিজ, উদোবুধোর দুনিয়াদারি, প্যাঁচার বিচার, শেয়ালের ওকালতি, কাকের হিসেব আর ভেবলে থাকা ‘আমি’-র হাতে একটা পেনসিল-ই থেকে যায়। সেটা দিয়েই বাঁদরের পিঠেভাগের ছবি আঁকি, আসুন।
অসঙ্গত ‘পশ্চাত্পক্বতার’ জগতে এমন ক্যাবলামি হাজার হাজার ড. হাজরা আর ছাব্বিশ ইঞ্চির ‘ফ্রি সাইজের’ দুনিয়ায় মানায় নাকি?
“তোমার মাপে হয়নি সবাই/ তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়/ কেউ বা মরে তোমার চাপে”
তোমার জন্য বীরভোগ্যা বসুন্ধরা থাকুক। এদের জন্য থাকুক আকাশ, ছেলেবেলার বৃষ্টি আর একটু পালিয়ে বাঁচার তেপান্তরের মাঠ।
আসুন, একটু অপুর সংসারে উঁকি দিই।
“এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত— অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়… পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া…”
এই হল সেই জগৎ যেখানে রাজা-উজির মরে কথায় কথায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, ক্রিকেটে উইকেট পড়লেও মূর্তিমান ‘উইকেড’ হয়ে ব্যাট চালানো যায়। পড়ে যাওয়া উইকেট পুনঃস্থাপিত করে ঝিঁঝিঁ খেলা চলে। নিজের গোলে গোল দিয়ে কেউ নায়ক বনে যায় তো কেউ হনলুলুর মাকুদার জন্য জীবনপাত করে দেয় দেশের পক্ষ থেকে। হিসাবের খাতার পাতা ল্যাম্পপোস্টের তারে গিয়ে বেঁধে থাকে, শিঙিমাছের পাখনা কেটে কেটে একটা মাছেই তিনমাস দিব্যি মাছের ঝোল খাওয়া যায়। কেউ হাঁড়ি-কড়ার দুঃখে উন্মাদ হয় তো কেউ পিলে চমকানো প্রভাতসঙ্গীত শুনেও বখশিস করে চলে যায়।
হাসি পায়? হযবরল-র দুনিয়ায় ন্যাড়া, হিজিবিজবিজ, উদোবুধোর দুনিয়াদারি, প্যাঁচার বিচার, শেয়ালের ওকালতি, কাকের হিসেব আর ভেবলে থাকা ‘আমি’-র হাতে একটা পেনসিল-ই থেকে যায়। সেটা দিয়েই বাঁদরের পিঠেভাগের ছবি আঁকি, আসুন।
অসঙ্গত ‘পশ্চাত্পক্বতার’ জগতে এমন ক্যাবলামি হাজার হাজার ড. হাজরা আর ছাব্বিশ ইঞ্চির ‘ফ্রি সাইজের’ দুনিয়ায় মানায় নাকি?
“তোমার মাপে হয়নি সবাই/ তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়/ কেউ বা মরে তোমার চাপে”
তোমার জন্য বীরভোগ্যা বসুন্ধরা থাকুক। এদের জন্য থাকুক আকাশ, ছেলেবেলার বৃষ্টি আর একটু পালিয়ে বাঁচার তেপান্তরের মাঠ।
আসুন, একটু অপুর সংসারে উঁকি দিই।
“এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত— অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়… পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া…”
আরও পড়ুন:
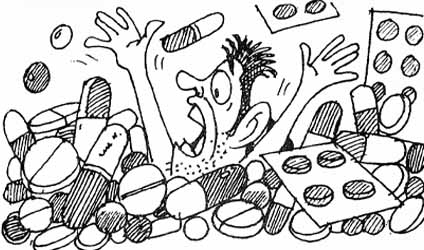
এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-২২: স্টেরয়েড বড় ভয়ঙ্কর ওষুধ?

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১৭: দু’ মাস আগের এক সন্ধ্যা

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১৩: কুরুপাণ্ডবদের দুই পিতামহের একজন — ভীষ্ম এবং তাঁর মা গঙ্গা
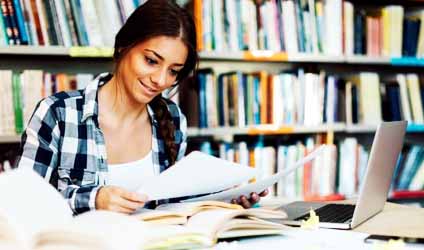
ইংলিশ টিংলিশ: শিখে নাও in- prefix দিয়ে তৈরি নতুন কিছু শব্দ
টেনিদার রক যদি হয় “সব পেয়েছির দেশ” তবে অপুর পাঠশালা একটা কল্পলোকের আঁতুড়ঘর। এই যে একটা অনন্ত ব্যাকুলতা জীবনের বাঁকে বাঁকে, পুকুর ঘাট থেকে বাঁশবাগান, আমবাগান, নানা মাঠ পার হয়ে শহর নগর ছাড়িয়ে অনন্তে মেশে সেটা তো নেহাৎ একটা ক্যাবলামি ছাড়া কী বা হতে পারে, যেখানে জলসা নেই, সেজবাতি নেই, মৌতাত নেই, নিজেকে একটু নিজের মতো গুছিয়ে নেওয়ার বাসনাও নেই, সাধ্য নেই… সেটা ছাব্বিশ ইঞ্চির বাঁধা গতে ক্যাবলামি।
এই যে অহং-এর প্রচ্ছন্ন গতায়াত, বাচ্ছামি, পাকামি, বাঁদরামি, দুষ্টুমি, নষ্টামি, ইতরামি, পাগলামি এবং ক্যাবলামি-সহ যাবতীয় ভাব, কর্ম বা অনুকরণবাচক এমন এক শব্দকাঠামোর অন্তরে যে আমিত্বের অধিবাস, কোথায় যেন তা নিজেকে নিজের সামনে সকল মহাবিচ্যুতি নিয়ে মুহূর্তে দাঁড় করিয়ে দেয়।
অথচ বলা তো হয়েছিল, নিজেকে জানো, আত্মদীপ হও, আত্মগত অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনার অনুধ্যান করো, অভ্রংলেহী গগনচুম্বী মানবতা ও ঔদার্যের মহাসঙ্গীতের সিম্ফনি আর রুদ্রবীণার ঝঙ্কার প্রাণে বাতাস লাগাক, সেগুলি কেবলই আলংকারিক বাগাড়ম্বর ছিল তবে। কৌটিল্য এর চেয়ে অকপটে বলতে চেয়েছিলেন, রাজার জন্য বেদপাঠ কেবল নিন্দাবাদের ভয়ে প্রযোজ্য একটা নিছক অশ্বডিম্ব কেবল, ত্রৈবর্ণিকের অবশ্যকর্তব্য অকর্মরূপে রাজার জন্য তা অনুসরণীয় বটে, তবে ”বুঝ লোক যে জানো সন্ধান।”
এই ‘আমি’ কি তবে এতোই অপাংক্তেয় এক বিষয়, যেখানে নিজেকে চেনার থেকে সকলে তোমাকে যেভাবে দেখতে চায় তা হয়ে ওঠার এক বিপুল আত্মপ্রবঞ্চনার নির্বুদ্ধিতা? নাকি এই ‘আমি’র একত্ব বা অদ্বিতীয় কল্পলোক থেকে সেই ‘তোমরা’, ‘তারা’, সকলেই ওই ‘আমি’গুলো থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিতে বলে তাদের মাপে, তাদের খাপে, তাদের দুনিয়ার যুক্তিতে, দেখনদারিতে, ভাবে, ভাবনায়, কদর্যতায়, বিনোদনে আর যূথবদ্ধ শ্রেণিচরিত্রে অথবা এক নতুন ছাঁচে গড়া ‘অহম্’ এর এককেন্দ্রিক নির্বিকল্প নিরালোক নির্জনতায়…
এই যে অহং-এর প্রচ্ছন্ন গতায়াত, বাচ্ছামি, পাকামি, বাঁদরামি, দুষ্টুমি, নষ্টামি, ইতরামি, পাগলামি এবং ক্যাবলামি-সহ যাবতীয় ভাব, কর্ম বা অনুকরণবাচক এমন এক শব্দকাঠামোর অন্তরে যে আমিত্বের অধিবাস, কোথায় যেন তা নিজেকে নিজের সামনে সকল মহাবিচ্যুতি নিয়ে মুহূর্তে দাঁড় করিয়ে দেয়।
অথচ বলা তো হয়েছিল, নিজেকে জানো, আত্মদীপ হও, আত্মগত অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনার অনুধ্যান করো, অভ্রংলেহী গগনচুম্বী মানবতা ও ঔদার্যের মহাসঙ্গীতের সিম্ফনি আর রুদ্রবীণার ঝঙ্কার প্রাণে বাতাস লাগাক, সেগুলি কেবলই আলংকারিক বাগাড়ম্বর ছিল তবে। কৌটিল্য এর চেয়ে অকপটে বলতে চেয়েছিলেন, রাজার জন্য বেদপাঠ কেবল নিন্দাবাদের ভয়ে প্রযোজ্য একটা নিছক অশ্বডিম্ব কেবল, ত্রৈবর্ণিকের অবশ্যকর্তব্য অকর্মরূপে রাজার জন্য তা অনুসরণীয় বটে, তবে ”বুঝ লোক যে জানো সন্ধান।”
এই ‘আমি’ কি তবে এতোই অপাংক্তেয় এক বিষয়, যেখানে নিজেকে চেনার থেকে সকলে তোমাকে যেভাবে দেখতে চায় তা হয়ে ওঠার এক বিপুল আত্মপ্রবঞ্চনার নির্বুদ্ধিতা? নাকি এই ‘আমি’র একত্ব বা অদ্বিতীয় কল্পলোক থেকে সেই ‘তোমরা’, ‘তারা’, সকলেই ওই ‘আমি’গুলো থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিতে বলে তাদের মাপে, তাদের খাপে, তাদের দুনিয়ার যুক্তিতে, দেখনদারিতে, ভাবে, ভাবনায়, কদর্যতায়, বিনোদনে আর যূথবদ্ধ শ্রেণিচরিত্রে অথবা এক নতুন ছাঁচে গড়া ‘অহম্’ এর এককেন্দ্রিক নির্বিকল্প নিরালোক নির্জনতায়…
আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১৬: আবার নুনিয়া

পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-১৩: ‘ওই দেখ, রাহুল দেব বর্মণের বাবা হেঁটে যাচ্ছেন’
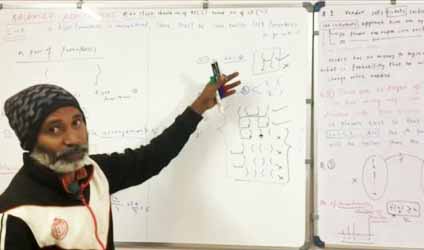
অজানার সন্ধানে: অঙ্কই ধ্যানজ্ঞান, মোটা বেতনের চাকরি নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেন আইআইটি-র শ্রবণ
এই ‘আমি’র মালিকদের ক্যাবলামি ইত্যাদির বিপরীতেই তো শোনা গিয়েছিল যাজ্ঞবল্ক্যের স্বর, “স্তব্ধ হও গার্গী”, কিন্তু মৈত্রেয়ীরা তো বলেই যাচ্ছে “যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্”
তাহলে ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচটাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে!
“ঘুইট্যাপাড়া আর কোথায় হইব? গোবরডাঙার কাছেই। গোবর দিয়াই তো ঘুইট্যা হয়।
ইয়াহ! টেনিদা এত জোরে হাবুলের পিঠ চাপড়ে দিলে যে হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। নাকটাকে জিভেগজার মতো উঁচু করে টেনিদা বললে, প্রায় ধরেছিস। তবে ঠিক গোবরডাঙার কাছে নয়, ওখান থেকে দশ মাইল হেঁটে, দুই মাইল দৌড়ে…”
এমন দৌড়ে কেন যেতে হয় ক্যাবলা তার অভ্যাসবশে জানতে চেয়েছিল, নাগপুর-কানপুর-চাঁদিপুরে আকস্মিক ভ্রমণের আশঙ্কা সত্ত্বেও, এমনকী এসবের উত্তর পাওয়া যায় না, এটা জেনেও হয়তো বা! টেনিদার সটান জবাবে সেই ছাব্বিশ ইঞ্চির উঁকিঝুঁকি…
“দৌড়তে হয় কেন?”
—ক্যাবলা জানতে চাইল।
—হয়, তাই নিয়ম। অত কৈফিয়ত চাসনি বলে দিচ্ছি। ওখানে সবাই দৌড়য়। হল?”
ক্যাবলামি এটাই। পড়াশোনা করে যে গাড়িচাপা পড়ে সে। অথবা নন্দলাল হয়ে রাস্তা বাঁচিয়ে চলে। জানার কোনও শেষ নাই বলেই জানার চেষ্টা বৃথা তাই। তাই বিদ্যালাভে লোকসান, নাই অর্থ, নাই মান। তা বলে কুয়োর ব্যাঙ হলে চলবে না। সমুদ্দুরের গপ্পো শোনাতে তো হবেই।
“ক্যাবলা বললে, হল। আর পথের বিবরণ দরকার নেই, গল্পটা বল।
গল্প!—টেনিদা মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, এমন একটা জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা, আর তুই বলছিস গল্প! শিগগির উইথড্র কর–নইলে এক চড়ে তোর নাক…
আমি বললুম, নাগপুরে উড়ে যাবে।
ক্যাবলা বললে, বুঝেছি। আচ্ছা আমি উইথড্র করলুম। কিন্তু টেনিদা ইংরেজিতে উচ্চারণ উইথড্র নয়।
তাহলে ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচটাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে!
“ঘুইট্যাপাড়া আর কোথায় হইব? গোবরডাঙার কাছেই। গোবর দিয়াই তো ঘুইট্যা হয়।
ইয়াহ! টেনিদা এত জোরে হাবুলের পিঠ চাপড়ে দিলে যে হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। নাকটাকে জিভেগজার মতো উঁচু করে টেনিদা বললে, প্রায় ধরেছিস। তবে ঠিক গোবরডাঙার কাছে নয়, ওখান থেকে দশ মাইল হেঁটে, দুই মাইল দৌড়ে…”
এমন দৌড়ে কেন যেতে হয় ক্যাবলা তার অভ্যাসবশে জানতে চেয়েছিল, নাগপুর-কানপুর-চাঁদিপুরে আকস্মিক ভ্রমণের আশঙ্কা সত্ত্বেও, এমনকী এসবের উত্তর পাওয়া যায় না, এটা জেনেও হয়তো বা! টেনিদার সটান জবাবে সেই ছাব্বিশ ইঞ্চির উঁকিঝুঁকি…
“দৌড়তে হয় কেন?”
—ক্যাবলা জানতে চাইল।
—হয়, তাই নিয়ম। অত কৈফিয়ত চাসনি বলে দিচ্ছি। ওখানে সবাই দৌড়য়। হল?”
ক্যাবলামি এটাই। পড়াশোনা করে যে গাড়িচাপা পড়ে সে। অথবা নন্দলাল হয়ে রাস্তা বাঁচিয়ে চলে। জানার কোনও শেষ নাই বলেই জানার চেষ্টা বৃথা তাই। তাই বিদ্যালাভে লোকসান, নাই অর্থ, নাই মান। তা বলে কুয়োর ব্যাঙ হলে চলবে না। সমুদ্দুরের গপ্পো শোনাতে তো হবেই।
“ক্যাবলা বললে, হল। আর পথের বিবরণ দরকার নেই, গল্পটা বল।
গল্প!—টেনিদা মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, এমন একটা জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা, আর তুই বলছিস গল্প! শিগগির উইথড্র কর–নইলে এক চড়ে তোর নাক…
আমি বললুম, নাগপুরে উড়ে যাবে।
ক্যাবলা বললে, বুঝেছি। আচ্ছা আমি উইথড্র করলুম। কিন্তু টেনিদা ইংরেজিতে উচ্চারণ উইথড্র নয়।
আরও পড়ুন:

দশভুজা: পিকনিক দল থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু: তাঁর লেন্সের বিস্তৃতি ছিল বিস্ময়কর

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৩৬: যুগে যুগে যা ‘সবার উপরে’

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫: মেরুর দিকে পৃথিবী কিছুটা চাপা, তাই এখানে দুটি কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যেও সূর্যালোকের পার্থক্য অনেকটা
আবার পণ্ডিতী! টেনিদা গর্জন করল: টেক কেয়ার ক্যাবলা, ফের যদি বিচ্ছিরি একটা কুরুবকের মতো বকবক করবি তো এক্ষুনি একটা পুঁদিচ্চেরি হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি তোকে। যা শিগগির আট আনার ঝাল-মুড়ি কিনে আন— তোর ফাইন!”
ক্যাবলাদের ছোটবেলা থেকে বড়বেলা সবটাই ক্যাবলামিতে ঠাসা। ক্বচিৎ কদাচিৎ যদি তাদের উত্তরণ ঘটে, তখন, বলা বাহুল্য তারা আর ক্যাবলা থাকে না। বেশ পোক্ত ধরণের সামাজিক জীবে পরিণত হয় তারা। তারা সেয়ানা, দাদা, নেতা, এমনকী তোতাপাখি-ও হতে পারে, কিন্তু ক্যাবলা তারা আর থাকতে পারে না।
ক্যাবলারা আসলে বড় হয় না। বয়সের পাকে ঘুরে ঘুরে ওই তেরো বছরেই এ এসে ঠেকে উদো বা বুধোর মতো। ক্যাবলাদের তাই সারাজীবনটাই ছোটবেলা।
অথচ, কৈবল্য পরিহাসের বিষয় নয়। “কৈবল্য /বিশেষ্য পদ/ ব্রহ্মত্ব বা মোক্ষলাভ; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্তি; পরমাত্মার অসঙ্গ অবস্থা; কেবলের ভাব।”
কৈবল্য প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, “কৈবল্য হল অষ্টাঙ্গ যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এর অর্থ হল ‘একাকীত্ব’, বিচ্ছিন্নতা, কেবল থেকে উৎপত্তি, একা, বিচ্ছিন্ন”। এটি হল প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিচ্ছিন্নতা, এবং পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি, অর্থাৎ মোক্ষ।” (উইকিপিডিয়া)
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, কৈবল্য হল অসঙ্গ, পুরুষার্থশূন্য সত্ত্বাদিগুণের প্রলয়রূপ বা প্রকৃতিরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি, স্বরূপে অবস্থিত চিতিশক্তি, ঐকান্তিকভাবে ও আত্যন্তিকভাবে দুঃখত্রয়ের তিরোধানরূপ মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ, ঐক্য, স্বরূপাবস্থান।
অতয়েব? ক্যাবলারা অদ্বিতীয় ও একা।
তারা, নিয়মে-অনিয়মে, সম্পদে-বিপদে এমনকী রাজদ্বারে-শ্মশানেও অসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন থাকে।—চলবে
ঋণ:
● নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ)
● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বোঝাপড়া)
● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পথের পাঁচালী)
ক্যাবলাদের ছোটবেলা থেকে বড়বেলা সবটাই ক্যাবলামিতে ঠাসা। ক্বচিৎ কদাচিৎ যদি তাদের উত্তরণ ঘটে, তখন, বলা বাহুল্য তারা আর ক্যাবলা থাকে না। বেশ পোক্ত ধরণের সামাজিক জীবে পরিণত হয় তারা। তারা সেয়ানা, দাদা, নেতা, এমনকী তোতাপাখি-ও হতে পারে, কিন্তু ক্যাবলা তারা আর থাকতে পারে না।
ক্যাবলারা আসলে বড় হয় না। বয়সের পাকে ঘুরে ঘুরে ওই তেরো বছরেই এ এসে ঠেকে উদো বা বুধোর মতো। ক্যাবলাদের তাই সারাজীবনটাই ছোটবেলা।
অথচ, কৈবল্য পরিহাসের বিষয় নয়। “কৈবল্য /বিশেষ্য পদ/ ব্রহ্মত্ব বা মোক্ষলাভ; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্তি; পরমাত্মার অসঙ্গ অবস্থা; কেবলের ভাব।”
কৈবল্য প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, “কৈবল্য হল অষ্টাঙ্গ যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এর অর্থ হল ‘একাকীত্ব’, বিচ্ছিন্নতা, কেবল থেকে উৎপত্তি, একা, বিচ্ছিন্ন”। এটি হল প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিচ্ছিন্নতা, এবং পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি, অর্থাৎ মোক্ষ।” (উইকিপিডিয়া)
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, কৈবল্য হল অসঙ্গ, পুরুষার্থশূন্য সত্ত্বাদিগুণের প্রলয়রূপ বা প্রকৃতিরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি, স্বরূপে অবস্থিত চিতিশক্তি, ঐকান্তিকভাবে ও আত্যন্তিকভাবে দুঃখত্রয়ের তিরোধানরূপ মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ, ঐক্য, স্বরূপাবস্থান।
অতয়েব? ক্যাবলারা অদ্বিতীয় ও একা।
তারা, নিয়মে-অনিয়মে, সম্পদে-বিপদে এমনকী রাজদ্বারে-শ্মশানেও অসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন থাকে।—চলবে
ঋণ:
● নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ)
● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বোঝাপড়া)
● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পথের পাঁচালী)
* ক্যাবলাদের ছোটবেলা (kyablader-chotobela): লেখক: ড. অভিষেক ঘোষ (Abhishek Ghosh) সহকারী অধ্যাপক, বাগনান কলেজ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ থেকে স্নাতকস্তরে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। স্নাতকোত্তরের পর ইউজিসি নেট জুনিয়র এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে সাড়ে তিন বছর পূর্ণসময়ের গবেষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। সাম্বপুরাণের সূর্য-সৌরধর্ম নিয়ে গবেষণা করে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। আগ্রহের বিষয় ভারতবিদ্যা, পুরাণসাহিত্য, সৌরধর্ম, অভিলেখ, লিপিবিদ্যা, প্রাচ্যদর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, চিত্রকলা, বাংলার ধ্রুপদী ও আধুনিক সাহিত্যসম্ভার। মৌলিক রসসিক্ত লেখালেখি মূলত: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন জার্নাল ও সম্পাদিত গ্রন্থে। সাম্প্রতিক অতীতে ডিজিটাল আর্ট প্রদর্শিত হয়েছে আর্ট গ্যালারিতে, বিদেশেও নির্বাচিত হয়েছেন অনলাইন চিত্রপ্রদর্শনীতে। ফেসবুক পেজ, ইন্সটাগ্রামের মাধ্যমে নিয়মিত দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন নিজের চিত্রকলা। এখানে একসঙ্গে হাতে তুলে নিয়েছেন কলম ও তুলি। লিখছেন রম্যরচনা, অলংকরণ করছেন একইসঙ্গে।



















